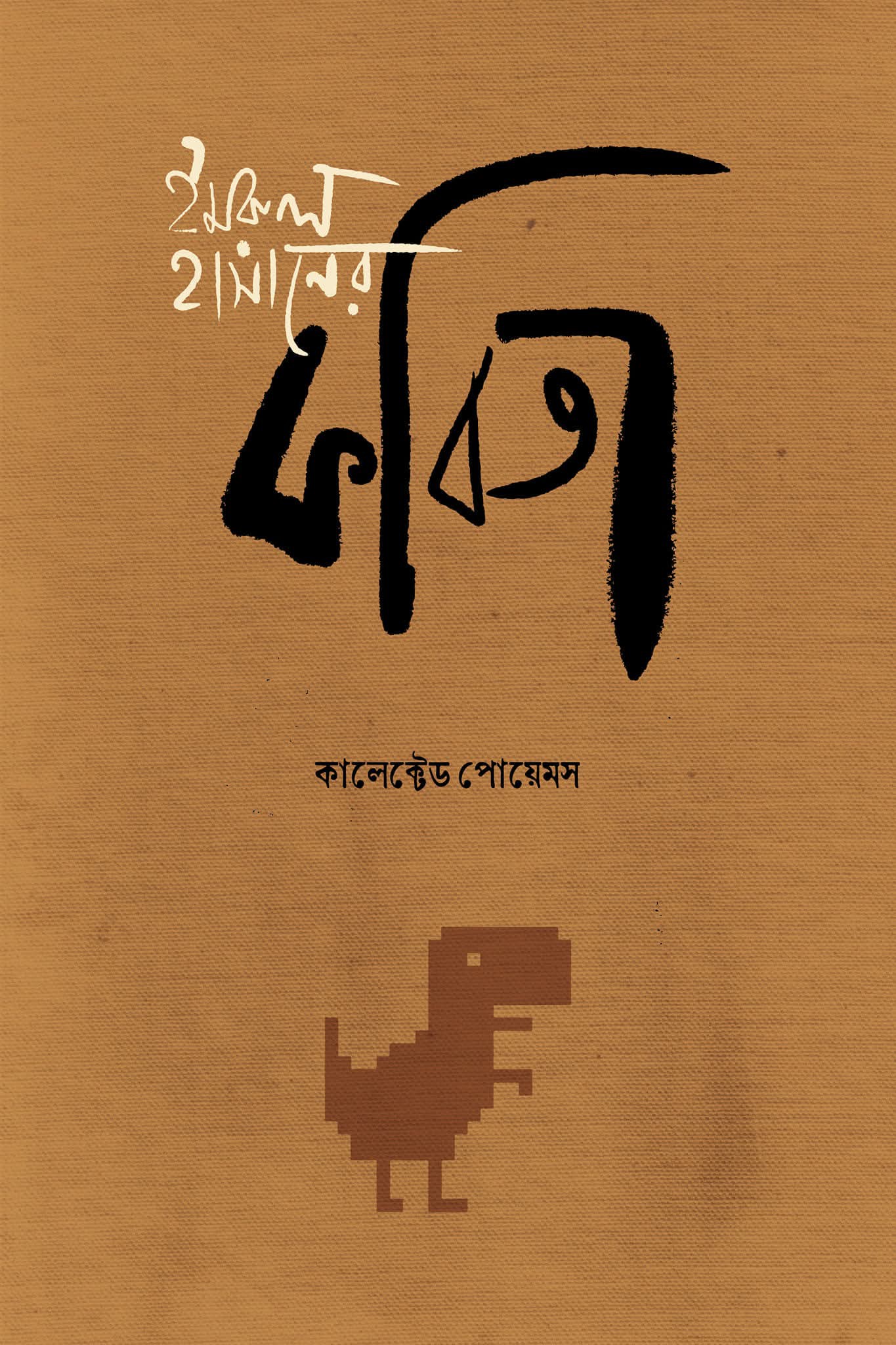সোনাকান্দি হতে মাঝের হাট দূর নয়। কিন্তু বর্ষায় নৌকা ছাড়া গতি নেই। তখন এ-পথটা অতিক্রম করতে গোটা একদিন লেগে যায়। এ-নদী সে-নদী; এ-খাল সে-নালা। স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ পানির আর মাছের, কচুরিপানার আর ধানের; নৌকায় ভরাট গন্ধ ভেজা কাঠের, ডহরের পানির আর খাম্বুরি তামাকের। আকাশের বর্ষাশেষের শ্রান্ত মেঘ নিস্তেজভাবে ঘোরে। হাওয়া নেই। পালশূন্য শ্লথগতি পানসি-ঘাসী-গয়না ও ডিঙির আর তেজের গরম নেই। এত পানি আর দিগন্তপ্রসারী খোলামেলা প্রসারতার মধ্যেও দমবন্ধ-করা ভাব। হঠাৎ কখনো-সখনো একটু হাওয়া যদি আসে চুড়ির মতো মিহিন ঢেউ তুলে পানিতে, বড় ভালো লাগে। দেহ শীতল হয়।
নৌকা আর নদী আর প্রসারতা আর মেঘ কেউ দেখে না। পথটা বাড়ির: এ-বাড়ির পথ বদলায় না। এ-বাড়ির পথ জীবন। কেবল কখনো শ্লথগতি, হাওয়া নেই বলে পাল ওড়ে না; আবার কখনো ঢেউ-ভাঙানো তেজময় গতি, পাল ফুলে থাকে হাওয়া আছে বলে। কখনো ঘুম পায়। কখনো খড়ের বিছানায় শুয়ে ছইয়ের ভেতরে দুলতে-থাকা থলে হুঁকার পানে তাকিয়েই থাকতে হয়। মাঝি ভাবে না, মাঝির ছেলেটা ভাবে না। যে-মেঘ নিস্তেজ সে-মেঘ দেখে না; যে-পানিতে সে-নিস্তেজ মেঘের ছায়া সে-পানি দেখে না। কখনো-সখনো নড়ে বসে কেবল খাম্বুরি তামাক খায় আর তার কড়া গন্ধ ভেসে আসে ছইয়ের ভেতর।
এ-পথ বাড়ির।
আফতাব ভাবে, চার বছর। চার বছর পরে বাড়ি যাচ্ছে। কলাপাতা-ঘেরা আম-জাম-গাছের ধারে, খাল-বিল নালা-ডোবার পাশে শতসহস্র ঘনবসতির মধ্যে বসবাস-করা লোকদের জন্য চার বছর পরে বাড়ি যাওয়াটা বড় কথা। সে-কথা পুঁথির কাহিনীর মতো দেশময় ছড়িয়ে পড়বার মতো অসাধারণ, নাড়ি ছেঁড়ার মতো গায়র-মামুলি।
– আফতাব মিঞা দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না। আফতাব মিঞা চাইর বচ্ছর দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না। শহরে থাকে। হেই বড় শহরে। আফতাব মিঞা গাড়ি-ঘোড়ায় চলে। আফতাব মিঞা সিদ্ধভাত খায়, বরফের মাছ খায়। আফতাব মিঞা রঙে আছে।
খেদু মিঞা দাঁতের মাজন বিক্রি করে ঢং করে বক্তৃতা দিয়ে, হাত সাফাইয়ের ম্যাজিক দেখিয়ে। খেদু মিঞা সে-শহরের খবর রাখে। আফতাব মিঞা হেই শহরে থাকে। চার বচ্ছর আফতাব মিঞা দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না।
– শহরে থাইকা আফতাব মিঞা বাড়িৎ কেবল টেকা পাঠায়। বাড়িৎ আছে নুনা মিঞা, তার বুড়া বাপ। বুড়া জমিজমা দ্যাখে আর বাতের ব্যথায় কঁকায়। চোখে ছানি পড়ছে; কিন্তুক বুড়া মানে না সে-কথা, স্বীকার করে না সে-কথা। মায়ের কবর পুকুরের পাড়ে গাবগাছটার তলে।
– আফতাব মিঞা শহরে থাকে; কিন্তু নুনা মিঞা দ্যাশে থাকে। পোস্টকার্ডে চিঠি ল্যাখে ছেলের কাছে আর ছেলের গল্প করে। আর নুনা মিঞা আফসোস করে। ছেলেডা আসে-আসে বলে, কিন্তু আসে না।
– আফতাব মিঞা কিন্তু কাবেল ছেলে। চাকরি করে আর বই বাঁধানোর দোকান চালায়। তাই আফতাব মিঞা দ্যাশে আসে না। আফতাব মিঞার সময় নাই, ছুটি নাই। আফতাব মিঞা চাকরিও করে ব্যবসাও করে।
দেশের বাড়িতে আর আছে বুবু। মানুষের জীবনে কী হয় বোঝা যায় না। বুবুর বিয়ে হল, বুবু নাইওর এল, বুবু শ্বশুরবাড়ি গেল। বুবুর ঘোমটা খুলল, বুবু সংসার গড়ল আরেক মানুষের ঘরে, বুবুর ছেলে-মেয়ে হল। বুবু মাছ ছাড়াল পুকুরে, আমগাছে আম গুনল। সন্ধ্যার পরেও বুবু কুপি হাতে খড়ম পরে গোয়ালে গরু দেখল, মুরগির খোঁয়াড়ে ঝাপ আছে কি না দেখল। তারপর বুবুর দাড়িওয়ালা স্বামীটা মারা গেল।
– জোতজমি আছিল। সেয়ানা লোকডা। ধড়াস্ কইরা মারা গ্যাল। মস্ত বড় মদ্দ মানুষ, হেই জোয়ান। কাতলার মতো মুখ হা কইরা ধড়াস করি মারা গ্যাল চক্ষের সামনে।
বুবু আর মাছ ছাড়ায় না, আমগাছে আম গোনে না।
-নুনা মিঞার মাইয়া সাদা শাড়ি পরে হিন্দুগো মতো। চোখে ছানিপড়া বুড়া বাপের সংসারডা দ্যাখে। নুনা মিঞার মাইয়ার নাকফুলের গর্তে বাঁশের ছিলার ঢিপি। নুনা মিঞার মাইয়ার চলনে-বলনে আর জান নাই। ছয়ডা পোলা-মাইয়া রাইখা তার স্বামীডা ধড়াস কইরা মারা গ্যাল চক্ষের সামনে।
ছইয়ের তলে কলকি দোলে হুঁকা দোলে আর টোপা দোলে।
আফতাব ভাবে, অনেকদিন সে বুবুকে দেখে নি। বরাবর বুবু তাকে দেখে কাঁদে। ভাবে, চার বছর পরে তাকে দেখে বুবু এবারো কাঁদবে কি? Continue reading →