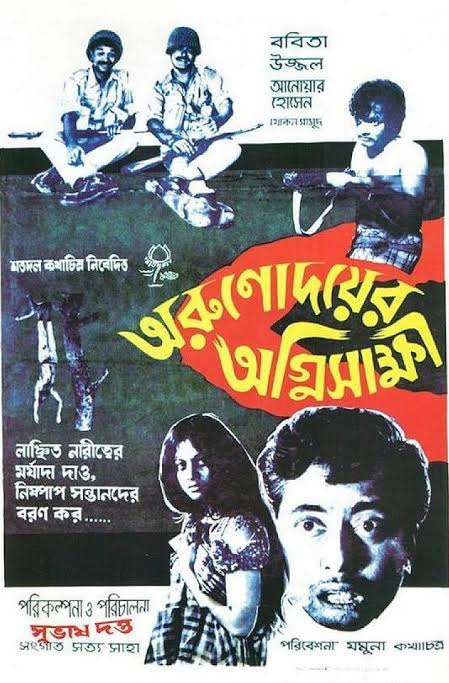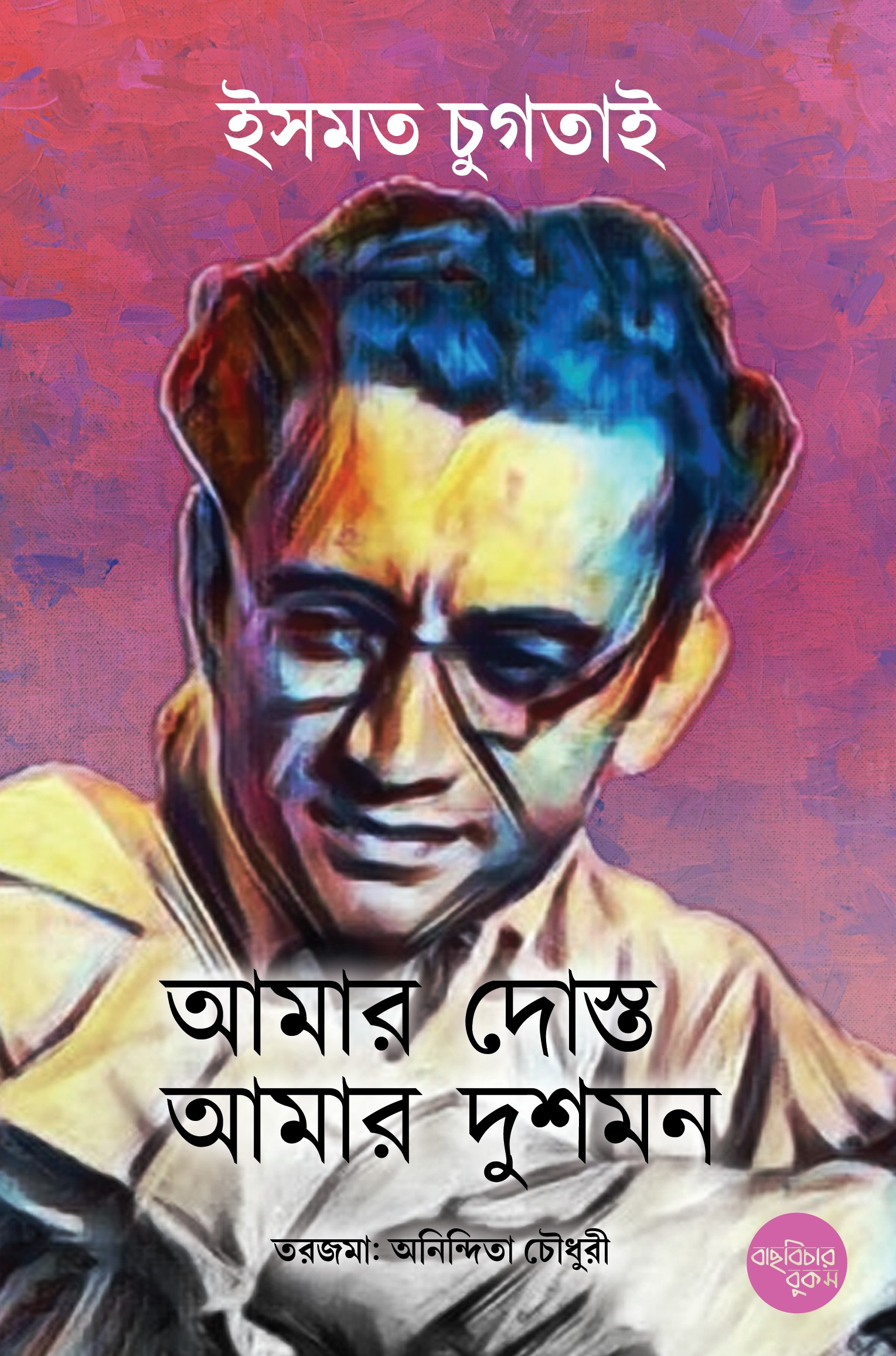ইন্ডিয়ান রাষ্ট্রবাদী প্রকল্প: একটা উদাহরণ Featured
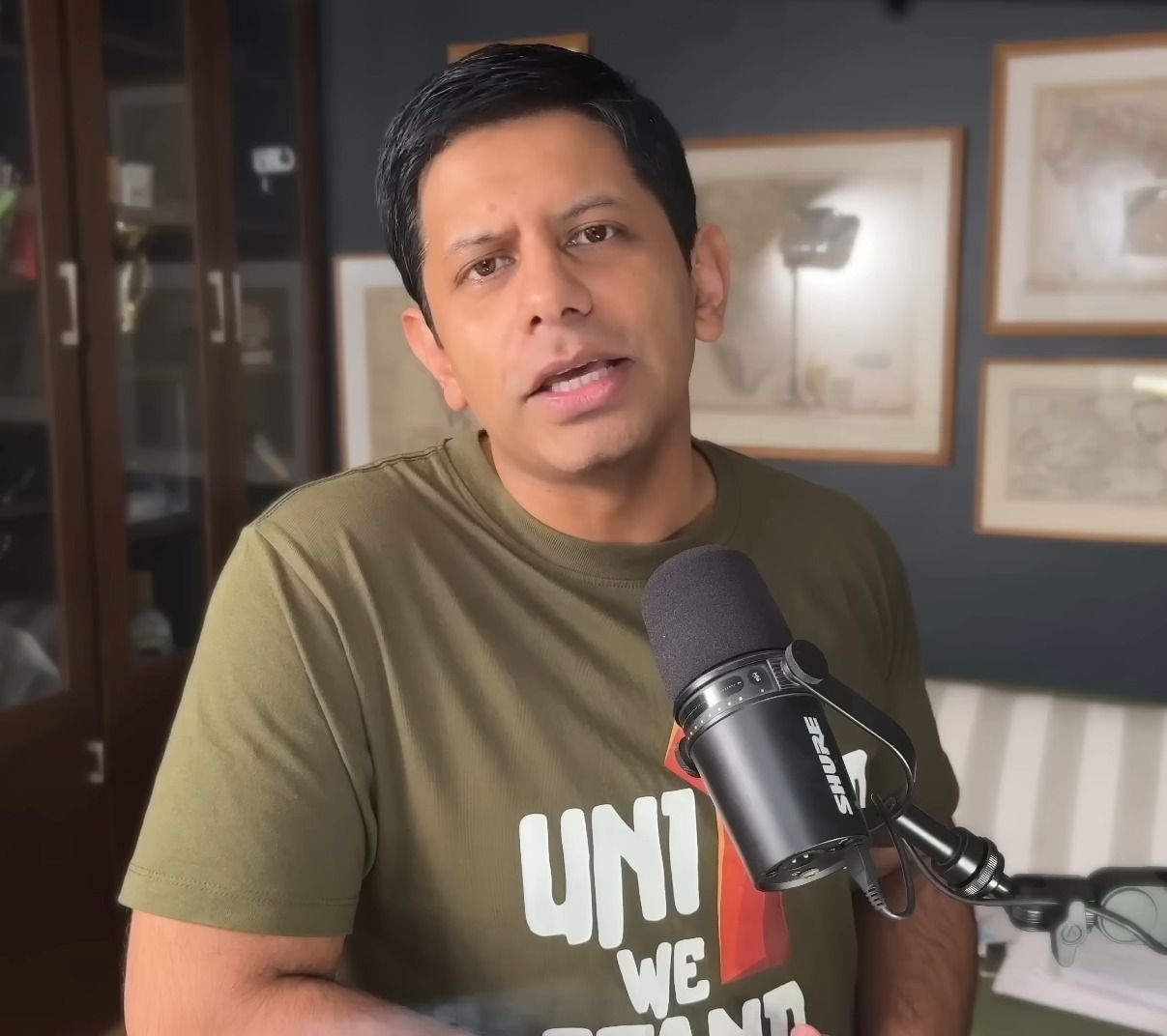
‘ইন্ডিয়ান রাষ্ট্রবাদী প্রকল্প’ জিনিসটা কী? তার আগের প্রশ্ন রাষ্ট্রবাদী প্রকল্প জিনিসটা কী? রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো এনটিটি না। একটা রাষ্ট্রের এক্সিস্টেন্স শুধু সেই রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে না। তাকে একটা শত্রু রাষ্ট্র নির্মাণ (মনোজগতে) করতে হয়৷ আম্রিকার যেমন একটা সোভিয়েত ইউনিয়ন বা একটা চীন লাগে, ভারতের একটা পাকিস্তান লাগে৷ এ ব্যতীত একটা ইউনিফায়েড রাষ্ট্র হিসেবে ফাংশান করা কঠিন।
অন্যসকল রাষ্ট্রের মতো শত্রু নির্মাণ করার পাশাপাশি ইন্ডিয়া আরেকটা কাজ করে: অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন লালন করে৷ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ইন্ডিয়াকে ‘ভারতবর্ষ’ বলে। মানে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। পুরো উপমহাদেশকে দখল করতে চায়। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তো বটেই, ভবিষ্যতে কোনোদিন রাজনৈতিকভাবে সমস্ত ভূখণ্ডকে একীভূত করার বাসনাও খুবই স্পষ্ট৷ হায়দ্রাবাদকে যেভাবে গিলে নিয়েছিল; নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশকেও তেমন গ্রাস করতে চায়৷ পাকিস্তানকেও চায় কিন্তু পারমাণবিক বোমা আছে জন্যে বলতে পারে না। অথচ ভারতবর্ষ বলে একক কোনো এনটিটি ছিল না বৃটিশরা আসার আগে।
এককথায়, শত্রুরাষ্ট্র নির্মাণ এবং তাকে গ্রাস করা— এই দুই মিলে তৈরি হয়: ইন্ডিয়ান রাষ্ট্রবাদী প্রকল্প।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, বিজেপির কথা না বলে কেন রাষ্ট্রের দিকে ইঙ্গিত করলাম। কারণ, বিষয়টা শুধু বিজেপির না৷ হায়দ্রাবাদ দখল করার সময় বিজেপি ক্ষমতায় ছিল না। অতো বেশি আগেও যাবার দরকার নেই, হাসিনার রেজিমের কথাই ভাবি। ২০০৯ সালে মসনদে বসার পরে প্রথমেই হাসিনা বিডিআর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করলো। ঘটনার সময় ভারতীয় প্যারাট্রুপাররা রেডি হয়ে ছিল, সংকেত পেলে বাংলাদেশে প্রবেশ করে হস্তক্ষেপের জন্য। তখন কিন্তু কংগ্রেস ক্ষমতায়। তারপর হাসিনা-মনমোহন একই বছরে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে যেটাকে বদরুদ্দীন উমর ‘বাঙলাদেশের নিরাপত্তা বিপন্নকারী’ বলে অভিহিত করেন। Continue reading