а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓа¶Ча¶Ња¶≤а¶Њ
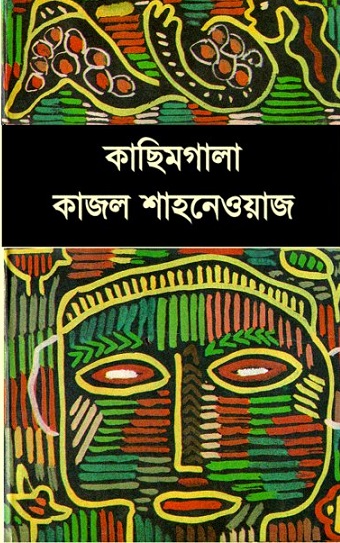
а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶ЬаІА аІІаІѓаІЃаІѓ ඪථаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶Па¶З а¶ЫаІЛа¶Яа¶Ча¶≤аІН඙а¶Яа¶Њ а¶ХаІЛаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗа¶ЮаІНа¶ЪаІБа¶∞аІА ඙ඌа¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ ථඌ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶З ඁගඕаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єа¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶За¶∞а¶Ха¶ЃаІЗа¶∞ ඁගඕ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗвАУ а¶Ча¶≤аІН඙/а¶Хඐගටඌа¶∞ а¶ђа¶За¶Яа¶Њ а¶ЦаІБа¶ђа¶З вАШа¶≠а¶Ња¶≤аІЛвАЩ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ බаІЛа¶ХඌථаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯаІЗа¶Яа¶ња¶≠ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපа¶ХබаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶Єа¶Ња¶Ђа¶≤аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶ЕථаІЗа¶Х බаІБа¶ЈаІН඙ඌ඙аІНа¶ѓ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞аІЗа¶У вАШа¶≠а¶Ња¶≤аІЛвАЩ а¶ђа¶≤а¶Ња¶Яа¶Њ а¶Па¶ЦථаІЛ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ, а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓа¶Ча¶Ња¶≤а¶Њ а¶Ча¶≤аІН඙а¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶ЧаІБаІЯа¶Ња¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ша¶Яа¶Ња¶ЗаІЯа¶Њ ඁගඕа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗа¶З а¶Яа¶Ња¶∞аІНථ а¶Ха¶∞ඌථаІЛ а¶ЧаІЗа¶≤аІЛа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථ ඁගඕаІЗа¶∞а¶З а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБ ථඌа¶З, а¶Ца¶Ња¶≤а¶њ а¶Еа¶∞аІНඕඐබа¶≤ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђа•§ а¶Па¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ පаІЗа¶Ј ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶∞а¶Ха¶ЃаІЗа¶∞ ඁගඕаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඌඐථඌа¶∞ බගа¶ХаІЗа¶З а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶єаІЯටаІЛа•§ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓа¶Ча¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ ඁගඕ а¶ЙථаІНа¶ЃаІЛа¶ЪථаІЗ а¶Па¶ђа¶В ඙аІБථа¶Гථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£аІЗ а¶Ж඙ථඌа¶ХаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶Чටඁ!
___________________________________________________________
а¶Па¶Хබගථ පаІБථග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Еටගа¶ЪаІЗථඌ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ ථඌа¶Ха¶њ ටගථප а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ба¶ЪаІЗа•§ а¶Па¶Хඕඌ а¶Ьඌථඌа¶∞ ඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶≠аІБа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ-බඌа¶УаІЯа¶ЊаІЯ а¶∞аІБа¶Ъа¶њ ථаІЗа¶З, а¶Єа¶Ња¶∞ඌබගථ පаІБа¶ІаІБ а¶≠а¶Ња¶ђа¶њ – а¶Ха¶њ а¶ѓаІЗ а¶≠а¶Ња¶ђа¶њ ටඌ ථගа¶ЬаІЗа¶З а¶Ьඌථග ථඌ, පаІБа¶ІаІБ а¶Ьඌථග, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶≠ඌඐටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, а¶Жа¶∞аІЛ, а¶Жа¶∞аІЛ а¶ђаІЗපаІА а¶Ха¶∞аІЗа•§
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Й а¶Єа¶ђа¶Єа¶ЃаІЯа¶З а¶ђа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථඌа¶Ха¶њ а¶Ша¶∞а¶ХаІБථаІЛа•§ а¶Хඕඌа¶Яа¶Њ පаІБථаІЗ а¶Па¶Ха¶Ња¶З а¶Цඌථගа¶Ха¶Яа¶Њ а¶єа¶Ња¶Єа¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶Єа¶њ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Еа¶Ѓа¶ЊаІЯа¶ња¶Х а¶ЫаІЛа¶Яа¶ђаІЗа¶≤а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶За•§ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶єа¶Ња¶ЄаІНа¶ѓа¶ЃаІЯаІЗа¶∞а¶Њ а¶ђа¶ЙаІЯаІЗа¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ а¶≠а¶ХаІНට а¶єаІЯа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ђа¶Й а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Еටපට а¶ЬඌථаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶∞ඌටаІЗ ඙ඌපаІЗ පаІБаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗа¶З ථඌа¶Ха¶њ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ බаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІЗа•§ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶∞ඌටаІЗ යආඌаІО යආඌаІО а¶ЧаІБа¶Ща¶њаІЯаІЗ а¶ХаІЗа¶БබаІЗ а¶ЙආаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗථаІЛ а¶ХаІБ඙ගаІЯаІЗ а¶ХаІБ඙ගаІЯаІЗ а¶ЃаІЗа¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶ЫаІЗа•§ බаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІЗ, а¶ХаІБа¶Ъа¶њ а¶ХаІБа¶Ъа¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶ЪаІБථ ඁගපගаІЯаІЗ а¶ђа¶ЄаІНටඌඐථаІНබаІА а¶Ха¶∞аІЗ ඙ඌථගටаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗ බගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ බаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІЗ а¶≤а¶ЮаІНа¶Ъ а¶°аІБඐගටаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ ඙аІЬа¶Ыа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶њ, ඙а¶∞аІЗа¶∞ බගථ а¶ЂаІБа¶≤аІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗ а¶Жа¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶ЧථඌඐබаІНа¶І а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බаІЗа¶єа•§ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶Іа¶∞а¶Ђа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЙආаІЗ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞аІЗ, вАШа¶≤а¶ЮаІНа¶ЪаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤аІЗ а¶ЧаІЛ?вАЩ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗථаІЛ а¶Уа¶∞ а¶≠ගටа¶∞а¶Яа¶Њ а¶Йа¶Ба¶Ха¶њ а¶ЃаІЗа¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶Ыа¶њ а¶Пඁථ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Уа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ පаІБа¶ІаІБ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Йа¶ХаІЗ බаІЗа¶Ца¶њ, බаІБа¶ЪаІЛа¶Ц а¶ЃаІЗа¶≤аІЗ බаІЗа¶Ца¶њ, а¶Уа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ඙а¶∞а¶Њ а¶ђаІНа¶≤а¶Ња¶Йа¶ЬаІЗа¶∞ යඌටඌයаІАථ а¶ђа¶Ња¶єаІБа¶ЃаІВа¶≤ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶ХаІНа¶≤ඌථаІНට а¶ђа¶Њ а¶ЃаІНа¶≤ඌථ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ පаІБа¶ІаІБ ඙аІНа¶∞පаІНථа¶З а¶Ха¶∞аІЗ, а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶ЦаІЗа¶Ња¶Ба¶ЬаІЗ а¶®а¶Ња•§[pullquote][AWD_comments][/pullquote]
ථඌථඌа¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඁගපаІЗа¶Ыа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶ња•§ а¶Па¶Хබගථ а¶Па¶Х а¶ЕථаІНа¶І а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙ගආаІЗ යඌට а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤, вАШа¶ђаІЬ а¶≠аІБа¶≤ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶Па¶≤а¶ња¶∞аІЗ ඙ඌа¶Ча¶≤а•§вАЩ а¶Ьඌථග а¶Па¶Єа¶ђ ඁථ а¶≠аІЛа¶≤ඌථаІЛ а¶Хඕඌ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ХаІЗ-а¶З а¶ђа¶Њ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓа•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Ха¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶Ца¶њ, ටඌа¶∞ а¶∞а¶ХаІНටගඁ а¶Ъа¶ХаІНа¶ЈаІБ а¶ХаІЛа¶Яа¶∞аІЗ а¶∞а¶Є а¶ЧаІЬа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, ටඐаІБ а¶ХаІЗඁථ а¶ХаІЛа¶Ѓа¶≤ а¶У а¶Жа¶∞аІНබаІНа¶∞ а¶≤а¶Ња¶Ча¶ЫаІЗа•§ а¶єаІЯටаІЛ а¶Па¶Х а¶Єа¶ЃаІЯ а¶°а¶Ња¶Хඌටග а¶Ха¶∞ටаІЛ, а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞а¶Њ а¶ЪаІЛа¶Ц ටаІБа¶≤аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ а¶ђа¶ња¶∞а¶ХаІНට а¶єаІЯаІЗа•§
вАШа¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙аІАа¶∞ а¶ХаІЗ а¶Ьඌථඪ? ඙ඌටа¶∞а¶Ња¶За¶≤аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха¶ЧаІБа¶≤а¶Ња•§вАЩ
вАШа¶ПටаІЛ а¶≤аІЛа¶Х ඙аІАа¶∞?вАЩ
вАШа¶ПටаІЛ а¶Ха¶З а¶∞аІЗ, а¶≤аІЛа¶Х ටаІЛ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶За•§вАЩ
вАШ…!вАЩ
вАШа¶Єа¶ђ а¶≤аІЛа¶Х а¶Ха¶њ а¶Жа¶∞ а¶≤аІЛа¶Х? බаІЗа¶Ц а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛа¶ЃаІЬаІЗ а¶Хටа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ЪаІЛа¶Йа¶Ца•§вАЩ
вАШа¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ?вАЩ
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ђа¶З а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња•§ ථඌථඌ а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐ а¶Хඕඌ ටඌа¶ХаІЗ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЕථаІНа¶І а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶Њ බඁа¶З а¶ђаІЗප а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђ а¶Ха¶∞а¶Ња•§ а¶ЄаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ, вАШа¶ЦаІБа¶ђ а¶Ца¶Ња¶∞ඌ඙ а¶Жа¶∞ а¶ЧඌථаІНබඌ а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІЯа¶Яа¶Њ, බаІЗа¶За¶Ца¶Њ පаІБа¶Зථඌ а¶Ъа¶≤а¶Ња¶Яа¶Ња¶З а¶ђаІБබаІН඲ගඁඌථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ьа•§ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З ඙аІАа¶∞ а¶єа¶За¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶ЊаІЯ, ඪඌඐ඲ඌථ а¶ЧаІЛ а¶Єа¶Ња¶ђа¶Іа¶Ња¶®а•§вАЩ
а¶Жа¶Ѓа¶њ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶њ, а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Яа¶Ња¶ђаІЗ ථඌ а¶Пඁථ а¶≤аІЛа¶Х а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶ЖපаІНа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓ а¶Єа¶ђ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа•§ а¶Ьа¶Ња¶Ђа¶≤а¶Ва¶П ඙ගаІЯа¶Ња¶Зථ ථබаІА ඙ඌаІЬ а¶єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ථаІМа¶Ха¶Њ а¶Яа¶≤а¶Ѓа¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Йආа¶≤аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶њ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶њ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤, вАШඁඌථаІБඣටаІЛ а¶Жа¶∞ ඙ඌටаІНඕа¶∞ а¶®а¶Ња•§ ථаІМа¶Ха¶Њ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ බаІБа¶≤а¶ђаІЛа¶За•§вАЩ
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Й а¶Па¶Єа¶ђ а¶ЫаІБа¶Яа¶ХаІЛ а¶Хඕඌа¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ а¶≠а¶ХаІНа¶§а•§ ටඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Па¶За¶Єа¶ђ а¶Еථඌඁඌ а¶≤аІЛа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Йа¶ХаІНටගа¶∞а•§ а¶ЄаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶ЫаІЗ, ථටаІБථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ පаІБථа¶≤аІЗа¶З ඃඌටаІЗ ටඌа¶ХаІЗ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞ටගඁඌඪаІЗ ඙ඌа¶Ба¶Ъа¶Яа¶њ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶ЙаІЯаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа¶З а¶ђа¶ња¶ЪගටаІНа¶∞ а¶≤аІЛа¶ХබаІЗа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞аІЗ පа¶∞аІАа¶∞, а¶Ша¶Ња¶ЃаІЗ а¶Ша¶Ња¶Ѓ а¶≤а¶Ња¶Ча¶њаІЯаІЗ ඁගපටаІЗ а¶єаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞а•§
а¶Жа¶∞аІЛ а¶Хටа¶ЧаІБа¶≤аІЛ බඌаІЯගටаІНа¶ђ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ вАШа¶ЕвАЩ а¶Па¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГට а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£ පගа¶ЦටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗа•§ а¶Жа¶Ь ථඌ а¶єаІЯ а¶Ха¶Ња¶≤ а¶Па¶Хබගථ ටаІЛ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ а¶ђа¶Њ а¶ЃаІЗаІЯаІЗ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, ටа¶Цථ а¶Уа¶ХаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞а¶ђа¶∞аІНа¶£ පаІЗа¶ЦඌටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ ටаІЛ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗа¶За•§ ඙ගටඌ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Х බඌаІЯගටаІНа¶ђа¶ЯаІБа¶ХаІБ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶∞ а¶Ѓа¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ බගටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶З а¶®а¶Ња•§ а¶Ша¶∞аІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Ѓа¶Њ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ча¶ЊаІЭ а¶ђа¶ња¶ЪගටаІНа¶∞ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£а¶З а¶ЬඌථаІЗа¶®а¶Ња•§ а¶У а¶ѓа¶Цථ а¶ђаІЬ а¶єа¶ђаІЗ, а¶Уа¶ХаІЗ ඃඌටаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Еа¶ЪаІЗථඌ ඙аІГа¶ђа¶њаІАටаІЗ а¶ЕථаІБ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞ටаІЗ ථඌ а¶єаІЯ а¶ЄаІЗа¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Па¶Цථ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටаІБටග බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а•§
вАШа¶ЕвАЩ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђа¶ња¶ЪගටаІНа¶∞ а¶ђа¶єаІБа¶ђа¶∞аІНа¶£а¶ња¶≤ а¶ІаІНа¶ђа¶®а¶ња•§ පаІБа¶ІаІБ а¶ІаІНඐථග ථаІЯ, а¶Па¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ЬаІЬඌථаІЛ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ђа¶єаІБ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІНඃඌටаІНа¶Ѓ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юа¶§а¶Ња•§ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶∞ඌටаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ха¶Яа¶њ вАШа¶Еа¶Уа¶Е-вАЩ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ха¶ђа¶ња¶ЄаІНа¶ЃаІЯ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞аІЗ, а¶ЄаІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶Ха¶З බගථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶≠а¶Ња¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІНа¶Хඣටඌа¶ХаІЗ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ вАШа¶ЕвА٠බගаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ а¶ЃаІЗа¶Яа¶ЊаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶≠ඌඐටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶З а¶Па¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ѓаІБа¶ђа¶ХаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞аІНටථඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ вАШа¶ЖвАЩ, а¶ђа¶Ња¶≤а¶ХаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඐඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ вАШа¶ЗвАЩ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІВ඙аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶ґа¶ња¶§а•§
а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶З ටඌа¶∞ඌබаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞а¶ђа¶∞аІНа¶£ а¶Ха¶њ? а¶≠аІНа¶∞а¶Ѓа¶£а¶Ъа¶≤а¶ња¶ЈаІНа¶£аІБ ථа¶ХаІНඣටаІНа¶∞ а¶Ьа¶ЧаІО ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІЗ а¶Ха¶Цථ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ? а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ХаІЗ පаІЗа¶ЦඌථаІЛа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђа¶∞аІНа¶£ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶єаІБඁඌටаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІБа¶ЄаІНටа¶ХаІЗа¶∞ ඪථаІН඲ඌථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ХаІНа¶≤ඌථаІНට а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶∞ а¶ђаІМ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЛ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Ха¶∞а¶ња•§ ඙аІНа¶∞පаІНථа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶ЦаІБа¶Ба¶Ьа¶њ ථඌ ටඐаІБ ඙аІНа¶∞පаІНථа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶З а¶Ча¶§а¶ња•§ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞ ඙а¶ЫථаІНබ а¶Ха¶∞а¶њ ටඌ а¶ђа¶≤аІЗ ඁථаІЗа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞а¶Яа¶Њ ඃඌබаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶БටඪаІНа¶ѓа¶Ња¶БටаІЗ, а¶°аІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඁඌа¶∞а¶Њ, ටඌබаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථ ඪයඌථаІБа¶≠аІВටග ථඌа¶За•§ а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ බаІБа¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ша¶∞ ඃටаІЛа¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶Жа¶≤аІЛа¶ЃаІЯ а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ђаІМ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ ටඌ а¶∞а¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞аІБа¶ЃаІЗ බаІБа¶Ьථ а¶∞ඌටаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶Ча¶Ѓ, а¶ШаІБа¶Ѓ а¶ЗටаІНඃඌබග පඌа¶∞аІАа¶∞а¶ња¶Х ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЃаІЗа¶Яа¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶њ, а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞аІБа¶ЃаІЗ බаІБа¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЦаІЗа¶∞ а¶Ьගථගපа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња•§ а¶ХаІЛථ а¶Еටගඕග а¶Па¶≤аІЗ බа¶∞аІЛа¶Ьа¶Њ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶ђа¶≤а¶њ, вАШа¶≠а¶Ња¶З а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІЛ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНට, ඐඪටаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ыа¶њ а¶®а¶Ња•§вА٠඙ඌа¶∞ට඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶Ха¶Ња¶Йа¶ХаІЗ а¶Ша¶∞аІЗ а¶ПථаІЗ а¶ђа¶Єа¶Ња¶З а¶®а¶Ња•§ ථගටඌථаІНටа¶З а¶ХаІЗа¶Й ඃබග а¶ЖඪටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯ, а¶ђа¶ЙаІЯаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ђаІБබаІНа¶Іа¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞ඌථаІНථඌа¶Ша¶∞аІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За•§ а¶Уа¶ЦඌථаІЗ බаІБа¶Яа¶Њ а¶ЃаІЛаІЬа¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶Ѓа¶≤ගථ а¶У ඙аІБа¶∞ඌථаІЛ а¶ђаІЗටаІЗа¶∞, а¶ђа¶Єа¶≤аІЗ ඙ඌа¶Ыа¶ЊаІЯ а¶ђа¶Ња¶БපаІЗа¶∞ а¶Хඌආගа¶∞ а¶ЦаІЗа¶Ња¶Ба¶Ъа¶Њ а¶ЦаІЗටаІЗ а¶єаІЯа•§ බаІБа¶Па¶Х ඁගථගа¶Я а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞а¶њ, вАШа¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶Ъа¶ЊвАЩа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶ђаІЛвАЩ – а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЪаІБа¶≤а¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Ха¶Ња¶З, ටඌа¶Ха¶Ња¶З а¶ЄаІЗа¶≤а¶ЂаІЗа¶∞ а¶ХаІМа¶Яа¶Ња¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ බගа¶ХаІЗа•§ а¶Еටගඕග а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Ъа¶ња¶∞බගථаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ඐගබඌаІЯ ථаІЗаІЯа•§
බаІБථඁаІНа¶ђа¶∞ а¶∞аІБа¶Ѓа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ ඙а¶∞аІЗ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ – а¶Па¶Х ථඁаІНа¶ђа¶∞а¶Яа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌа¶З а¶ђа¶≤а¶ња•§ පаІБа¶ІаІБ а¶∞ඌටаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶њ а¶ђа¶≤аІЗ а¶П а¶∞аІБа¶Ѓа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶Ња¶∞ගබගа¶ХаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඐඌටග а¶≤а¶Ња¶ЧඌථаІЛа•§ а¶ђаІМ а¶ЈаІЬа¶ЛටаІБа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Уа¶ЄаІНටඌබ а¶≤аІЛа¶Ха•§ а¶ЫаІЛа¶Яа¶ђаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ ථඌа¶Ха¶њ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ђаІГබаІН඲ඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Уа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤аІЛ, ටඌа¶∞а¶Ња¶З а¶Уа¶ХаІЗ а¶ЛටаІБ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Х ථඌථඌ а¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗ а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶І а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ѓаІЗ а¶ЛටаІБа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶ЬаІЗථаІЗа¶ЫаІЗ, ටඌ ථගаІЯаІЗ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ьа¶Ха¶Ња¶≤ а¶Єа¶єа¶ЬаІЗа¶З а¶ђа¶≤аІЗ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤ටග а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඙ථаІЗа¶∞ බගථ а¶Хට а¶УаІЯа¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶њ а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶ђа¶Ња¶≤аІНа¶ђ а¶ЬаІНа¶ђа¶≤а¶ђаІЗ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶ХаІЛа¶£а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ ථඌථа¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶ЄаІЗа¶° а¶≤а¶Ња¶ЧඌථаІЛ а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶ђаІМ ථගа¶ЬаІЗа¶З а¶ХаІБаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶Ьගථගප ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Уа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ඐඌථගаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶Єа¶ЬаІНа¶Юа¶Њ а¶ђа¶≤аІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶ђаІБа¶Эа¶њ а¶®а¶Ња•§ ටඐаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЭаІЗа¶Ња¶Ба¶Х ඙аІБа¶∞ඌථаІЛ а¶Жа¶Ѓа¶≤аІЗа¶∞ ටаІЗа¶≤аІЗа¶∞ ඐඌටගටаІЗа•§ а¶ђа¶ња¶ђа¶Ња¶єа¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶Ја¶ња¶ХаІАа¶∞ а¶∞ඌටаІЗ а¶ЬаІНа¶ђа¶Ња¶≤ඌථаІЛа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІЗа¶ЯаІНа¶∞аІЛа¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Є а¶ЬаІЛа¶Ча¶ЊаІЬ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Па¶З а¶Єа¶ђ а¶ЬගථගපаІЗа¶∞ а¶Эа¶Ња¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ а¶єа¶≤аІЛ, а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Єа¶ЃаІЯа¶З а¶Па¶∞ බаІБа¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Еа¶Вප а¶Єа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗ ථගටаІЗ а¶єаІЯ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ යඌටаІЗа•§ ඃබගа¶У а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЯаІБа¶≤а¶ђа¶ХаІНа¶Є а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Эа¶Ња¶≤а¶Ња¶З а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶За¶≤аІЗа¶Ха¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Х ටඌටඌа¶≤, а¶Ђа¶Ња¶За¶≤, а¶єаІНඃඌථаІНа¶° а¶°аІНа¶∞а¶ња¶≤, а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Є, а¶ђа¶Ња¶Яа¶Ња¶≤, යඌටаІБаІЬаІА, а¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶Бබඌ, а¶ЄаІНа¶ХаІНа¶∞аІБ а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠а¶Ња¶∞, а¶Ѓа¶Ња¶≤аІНа¶Яа¶ња¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ња¶∞ – ටඐаІЗ а¶За¶≤аІЗа¶ХаІНа¶ЯаІНа¶∞ථගа¶Ха¶ЄаІЗа¶∞ ටаІЗඁථ а¶Єа¶Ц ථඌа¶За•§ а¶ѓаІЗඁථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІМаІЯаІЗа¶∞ ථඌа¶З а¶ђа¶Ња¶Чඌථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ца•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ЦаІБපаІА а¶ПටаІЗа•§ පගа¶≤аІН඙ඐග඙аІНа¶≤а¶ђаІЗа¶∞ ඙а¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ЗටаІЛ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІЬаІЛ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, ථඌ а¶єаІЯ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ЫаІЛа¶Я а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ; а¶ђа¶Ња¶Чඌථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶Яа¶Њ а¶ХаІЛථа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З ඙аІЬаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶Ња¶Чඌථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඁථаІЗ а¶єаІЯ а¶Па¶Х а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≤а¶Ња¶Єа•§
а¶ЛටаІБ ඐගපаІЗа¶Ја¶ЬаІНа¶Ю а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІМ පаІЛа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ша¶∞а¶Яа¶Њ а¶Пඁථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ха¶≤аІН඙ථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ аІІаІ®’ аІА аІІаІ™’ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶ХаІНа¶ЈаІЗ ඥаІБа¶Ха¶≤аІЗ а¶Жබගа¶ЕථаІНටයаІАථ ඁඌටаІНа¶∞ඌටаІНටаІЛа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЕථаІБа¶≠аІБටග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶ЮаІНа¶Ъа¶Ња¶∞ගට а¶єаІЯа•§ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶Еа¶∞аІНа¶ІаІЗа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГට а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІЗаІЬ а¶ЂаІБа¶Я а¶Йа¶Ба¶ЪаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ђа¶≤а¶Є а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗ, ඃඌටаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞аІН඙аІЗа¶Я ඙ඌටඌ а¶Жа¶∞ а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗа¶Яа¶Њ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථ බගа¶ХаІЗ а¶Єа¶∞ඌථаІЛ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ђаІМ ඙аІНа¶∞ටගඁඌඪаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶Еථගа¶∞аІНа¶Іа¶Ња¶∞ගට ටඌа¶∞а¶ња¶ЦаІЗ а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗа¶∞ а¶ЄаІНඕඌථ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶∞аІН඙аІЗа¶ЯаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶Па¶Х а¶За¶ЮаІНа¶Ъа¶њ а¶ЂаІЛа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ъඌබа¶∞а•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Й඙а¶∞ ඙ඌа¶Яа¶њ а¶ђа¶ња¶ЫඌථаІЛ а¶ѓа¶ЊаІЯ, ඁඌබаІБа¶∞а¶У а¶ЂаІЗа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЄаІЗ а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛа¶Х, а¶Уа¶∞ а¶ђаІЯа¶ЄаІЗа¶∞ ඪඁඌථ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Х ඙а¶Ба¶Ъගපа¶Яа¶Њ а¶ЫаІЛа¶Я, а¶ђаІЬ, а¶ЧаІЛа¶≤, а¶ЪаІНඃඌ඙аІНа¶Яа¶Њ, ටගථа¶ХаІЛа¶£а¶Њ ථඌථඌ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶≤ගප а¶ђа¶ња¶ЫඌථඌаІЯ а¶ЫаІЬඌථаІЛ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶ђаІМа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶≤ගපаІЗ ඥаІЗа¶ХаІЗ ටඌа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶ШаІБඁඌථаІЛа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶ђа¶Њ а¶Уа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ђа¶Ња¶≤ගපаІЗа¶∞ ඐගපаІНа¶ђа¶ѓаІБබаІНа¶І а¶≤а¶Ња¶Ча¶њаІЯаІЗ බගаІЯаІЗ ටаІБа¶ЃаІБа¶≤ а¶ђа¶Ња¶≤ගපඐаІГа¶ЈаІНа¶ЯගටаІЗ а¶ЃаІБа¶Ја¶≤а¶Іа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶≤ගපඐа¶∞аІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶≠аІЛа¶∞а¶∞ඌටаІЗ බаІЗа¶Ца¶њ а¶ђа¶Ња¶≤ගපа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶ХаІЗ а¶У а¶ХаІЛа¶≤аІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ШаІБа¶Ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶ЦаІБа¶Ха¶ња¶Яа¶ња¶∞ ඁටаІЛ ථаІЯ а¶ѓаІЗථаІЛ а¶ђа¶Њ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа¶Ха¶Ња¶∞ ථඌа¶∞аІАබаІЗа¶∞ පට඙аІБටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶Ха¶Ња¶ЩаІНа¶Ца¶Ња¶∞ а¶≠ගටа¶∞аІЗ а¶єа¶Ња¶ђаІБа¶°аІБа¶ђаІБ а¶Ца¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Уа•§ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ පඪаІНа¶ѓ-පаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓа¶≤а¶Њ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶ШаІБа¶Ѓа¶ШаІБа¶Ѓ а¶ЃаІЗа¶Ша•§
а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ බа¶∞аІЛа¶Ьа¶Њ බаІБа¶Яа¶њ а¶Єа¶Ња¶ЬඌථаІЛа¶∞ а¶Ха¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶£аІЗ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗ а¶ђа¶ЙаІЯаІЗа¶∞ ආаІЗа¶Ња¶Ба¶Яа•§ ඁථ а¶Ъа¶ЊаІЯ а¶Уа¶ЦඌථаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞ඌබගථ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶Ха¶∞а¶њ, а¶ЪаІБа¶ЃаІБ а¶Ца¶Ња¶З, а¶≠а¶ња¶Ьа¶њаІЯаІЗ ටаІБа¶≤а¶њ а¶ѓа¶Њ ථаІЗа¶З а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ђ а¶ЕථඪаІНටගටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶≠ඌඐථඌа¶ЧаІБа¶≤а¶ња•§ а¶ђа¶ЄаІНටаІБටа¶Г а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕа¶З а¶єа¶≤аІЛ а¶Хටа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ථගа¶∞аІНа¶ђа¶ЄаІНටаІБа¶Х а¶≠а¶Ња¶ђа¶ХаІЗ а¶ЫаІЗа¶Ња¶БаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶≤аІН඙ථගа¶Х а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≠ඌඐථඌа¶ХаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶ња¶Х а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ХаІГаІОа¶ХаІМපа¶≤а•§
පаІЛа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ша¶∞а¶ЯඌටаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶Ња¶Ба¶ЪаІЗа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Б඙ඌ а¶Ха¶ња¶Йа¶ђ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Яа¶Ња¶∞ а¶Па¶Хබගа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъ а¶Єа¶∞ඌථаІЛ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶ЪаІНа¶Ыටඌа¶∞ බගа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Е඙а¶∞а¶ња¶ЄаІАа¶Ѓ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ යආඌаІО а¶Жථඌ а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶Па¶З а¶Шථа¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ а¶≠ගටа¶∞аІЗ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ца¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЄаІНඕඌ඙ථаІЗа¶∞ а¶ЪගථаІНටඌ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Жа¶Іа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶≠ගටа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Ы ඙аІЛа¶ЈаІЗ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶ХаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶Ѓ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ъа¶Ња¶З ථඌ, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Жа¶∞аІЛ а¶ЃаІМа¶≤а¶ња¶Х а¶У а¶Па¶Ха¶Х а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За•§ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶ЖථаІНටа¶∞а¶ња¶Х а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Па¶З බඌඁаІА а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъа¶ШаІЗа¶∞а¶Ња¶ЯаІЛ඙аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За•§
а¶ђа¶Й а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁටаІЛа¶З аІѓа¶Яа¶Њ-аІЂа¶Яа¶Њ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Уа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථ ථඌඁ а¶Жа¶Ь а¶Еа¶ђаІНබග ආගа¶Х а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња¶®а¶ња•§ а¶Па¶Ха¶З ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ථඌඁаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІАа•§ вАШථඌඁвАЩ – а¶Па¶З а¶ђа¶ња¶ЄаІНа¶ЃаІЯа¶Ха¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶Њ ඃටаІЛ а¶ђаІЗපаІА а¶ІаІНඐථගථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ පаІНа¶∞а¶ђа¶£а¶™аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶єа¶ђаІЗ ටටа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЊаІЯа•§ ථටаІБථ ථඌඁ බගටаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤а¶ђа¶Ња¶Єа¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Уа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ආගа¶Х а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ХаІЛථ ථඌඁаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶њ ඪථаІНටаІБа¶ЈаІНа¶Я ථа¶За•§ а¶ђа¶ЙаІЯаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶ђ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶Ьඌථග ටඌටаІЗ а¶Єа¶єа¶ЬаІЗа¶З а¶Уа¶ХаІЗ а¶°а¶Ња¶ХටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ а¶Ж-ටගаІЯа¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ ථඌඁа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ вАШටвАЩ а¶ІаІНඐථග ඐගපаІЗа¶Ј а¶Еа¶≠а¶ња¶Шඌට යඌථа¶≤аІЗа¶У а¶ђа¶єаІБ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗ ටඌ а¶ЃаІНа¶≤а¶Ња¶®а•§ а¶Жа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЬගථගපаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ පගයа¶∞а¶£ ථඌа¶За•§
а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶∞ ථඌඁ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ђаІЛ а¶®а¶ња¶єа¶ња•§ а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶∞ ථඌඁ ථаІГа¶™а¶Ња•§ а¶ђа¶Њ а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶∞ ථඌඁ ඙ගа¶Б඙ගа¶Б, а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶∞ ථඌඁ а¶Ха¶ња¶ґа•§ а¶Па¶Єа¶ђ а¶≠ඌඐටаІЗ а¶≠ඌඐටаІЗ පගපаІБබаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Ьа¶≤а¶∞а¶ВаІЯаІЗ ථඌථඌа¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Ха¶ЃаІН඙аІЛа¶Ьගපථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞а¶ња¶Х а¶∞а¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶≠ගටа¶∞ ඥаІБа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඕඌа¶Ха¶ња•§
඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ а¶≠аІЗа¶ђаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ ටගа¶Жа¶∞ а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶∞аІЛа¶ЮаІНа¶Ьа¶ЃаІВа¶∞аІНටග а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶Ба¶ЪаІЗа¶∞ а¶Шථа¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞а¶ња•§ ඲ඌටаІБа¶Ча¶≤ඌථаІЛ а¶Ђа¶Ња¶∞аІНථаІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ а¶ђаІНа¶∞аІЛа¶ЮаІНа¶Ь а¶Ча¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶З а¶ЃаІЛа¶≤аІНа¶°а¶ња¶В а¶П ථаІЗа¶ЃаІЗ ඙аІЬа¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ша¶∞аІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЛ а¶ЃаІЛа¶Ѓа¶ђа¶Ња¶§а¶ња•§ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Ца¶Ња¶≤а¶њ а¶За¶ХаІЛථаІЛ а¶Ха¶≤а¶Ѓ а¶ЃаІЛа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤ඌටаІЗ а¶Ча¶≤а¶њаІЯаІЗ, а¶ђа¶Ња¶Ба¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶Ха¶≤а¶ЃаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ХаІГටග а¶Ша¶Яа¶њаІЯаІЗ ථඌථඌ а¶∞а¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶∞а¶≤ а¶∞аІЗа¶Ца¶Њ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ а¶Ђа¶∞аІНа¶Ѓ ටаІИа¶∞аІА а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ХаІЛථ а¶ХаІЛථа¶Яа¶Њ а¶єаІЯаІЗ බඌа¶БаІЬа¶Ња¶≤аІЛ а¶Єа¶Ва¶Ча¶Ѓа¶∞ට ටаІНа¶∞а¶ња¶≠а¶ЩаІНа¶Ч ථа¶Яа¶∞а¶Ња¶Ь, а¶ХаІЛථа¶Яа¶Њ а¶Йа¶∞аІНබаІНа¶Іа¶ЃаІБа¶ЦаІА ඙ඌа¶ХඌථаІЛ а¶Єа¶Ња¶™а•§ а¶ѓаІЗථ а¶ЄаІН඙аІЗа¶Єа¶ХаІЗ а¶Іа¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ටаІНа¶∞ගඁඌටаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶Ђа¶Ња¶Бබ ඐඌථඌа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ඃබගа¶У, ටගа¶Ж а¶єа¶≤аІЛ а¶®а¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ ටගа¶Ж ථаІЯ, а¶Жа¶Ьа¶Ха¶Ња¶≤ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶≠ගටа¶∞ а¶Р а¶ђа¶єаІБ ටа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ба¶ЪаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶З а¶Еථඐа¶∞ට а¶ШаІБа¶∞ටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ѓа¶Ња¶З, а¶ѓаІЗ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ ඕඌа¶Ха¶њ а¶ХඌථаІЗа¶∞ а¶≠ගටа¶∞ а¶ХаІБඁථаІНටаІНа¶∞а¶£а¶Њ බගටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ а¶Р а¶ЄаІАа¶Ѓа¶Ња¶єаІАථ а¶Еа¶∞аІНඕපаІВථаІНа¶ѓ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶Єа•§ а¶ЄаІЗ а¶ѓаІЗථ а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ а¶ђа¶≤аІЗ, вАШа¶≠а¶∞аІЛ, а¶≠а¶∞аІЛ, а¶≠а¶∞аІЛвАЩа•§
а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඕа¶≤а¶њ යඌටаІЗ а¶Па¶Хබගථ а¶Еа¶Ђа¶ња¶ЄаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶За•§ вАШටаІБа¶Ѓа¶њ පаІБа¶ІаІБ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶∞а¶Ња¶ЬаІА а¶єа¶УвАЩ а¶ђа¶≤аІЗ ටගа¶Жа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐ බаІЗа¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බаІБථඁаІНа¶ђа¶∞ а¶Ша¶∞а¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ බගටаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ ටගа¶Ж а¶∞а¶Ња¶ЬаІА а¶єаІЯ ථඌ а¶Ха¶ња¶ЫаІБටаІЗа¶За•§ а¶Еඕа¶Ъ а¶Ха¶њ а¶Па¶Ха¶ШаІЗа¶БаІЯаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶ЫаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Р а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶Ба¶Ъගපа¶Яа¶Њ а¶Ьගථගඪ ථගаІЯаІЗ а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ а¶≠ඌඐටаІЗа•§ аІ®аІЂ-аІ≠=аІІаІЃ; аІІаІЃ/аІ®=аІѓ; аІѓ-аІ©=аІђа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶Па¶ХඌථаІНට а¶Ж඙ථ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Р а¶Ша¶∞аІЗ ඁඌටаІНа¶∞ аІђа¶Яа¶Њ а¶Ьගථගඪ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶Ха¶ња¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ аІ≠а¶Яа¶Њ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£, බаІБа¶ЬථаІЗа¶∞, ටගа¶Жа¶∞ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ аІђа¶Яа¶Њ, ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ХаІА ටගථа¶Яа¶Њ а¶Па¶Х ථඁаІНа¶ђа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Єа¶ВපаІНа¶≤а¶ња¶ЈаІНа¶Яа•§ аІђа¶Яа¶Њ а¶Ьගථගඪ, а¶Еඕа¶Ъ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ха¶Ња¶ЩаІНа¶Ца¶Њ аІ≠а¶Ѓа¶ЯඌටаІЗа•§ а¶Жа¶∞ а¶Уа¶ЦඌථаІЗ ථටаІБථ а¶ХаІЛථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ѓа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶У ථඌа¶За•§
а¶Па¶Хබගථ а¶ЃаІЯඁථඪගа¶Ва¶є ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ъගආග ඙ඌа¶З, а¶ЄаІЗа¶З а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЦаІЗа¶Ња¶Ба¶Ь ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§
ටගа¶Ж а¶ХаІЗ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶Чට බаІЗаІЬ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶∞ඌට а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶Яа¶Ња¶За¶®а¶ња•§ බаІЗаІЬ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶Њ а¶∞ඌටа¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Па¶Х ථඁаІНа¶ђа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶Ђа¶≤а¶Є а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗ බඌ඙ඌබඌ඙ග а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ; а¶Р а¶∞ඌටа¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Ыа¶њ а¶ЃаІЗаІЯаІЗබаІЗа¶∞ а¶ѓаІМථа¶ЖටаІНа¶Ѓа¶Њ а¶Еа¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≤а¶Ња¶ЄаІАа•§ а¶ЃаІЗаІЯаІЗබаІЗа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶Єа¶єа¶Ь а¶ђа¶ЯаІЗ а¶ХගථаІНටаІБ ටගа¶Ж а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤ а¶ЃаІЗаІЯаІЗа•§ а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤ටඌ බගаІЯаІЗ а¶Уа¶ХаІЗ а¶ЬаІЯ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єаІЯа•§ ටගа¶Ж а¶Ха¶ЦථаІЛа¶З а¶ХаІНа¶≤ඌථаІНට а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶Уа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞ а¶ЄаІГа¶ЬථаІА ඙аІНа¶∞ටගа¶≠ඌබаІА඙аІНට, а¶ђаІАа¶∞а¶ђаІНа¶ѓа¶ЮаІНа¶Ьа¶Х а¶Жа¶∞ а¶Уа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞аІЗа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞аІЗа¶∞ а¶Еа¶Вපа¶ЯаІБа¶ХаІБа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЧаІНа¶ЃаІАටඌ а¶Еа¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ පа¶∞аІАа¶∞а¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЙබаІНа¶ѓа¶Ѓ බගаІЯаІЗ ඃබග а¶ЄаІН඙аІАа¶°а¶ђаІЛа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤а¶њ а¶Уа¶∞ а¶Ьа¶≤а¶Ња¶≠аІВඁගටаІЗ а¶У а¶ЦаІБපаІАටаІЗ ඙а¶Ба¶Ъගපа¶Яа¶Њ ටගа¶Ж а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗ, а¶ђаІЗа¶≤аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ ඁටаІЛ а¶ЧаІБаІЬаІЛ а¶єаІЯаІЗ а¶Эа¶∞аІЗ ඙аІЬаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ යඌටаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Жа¶∞а¶ђаІНа¶ѓ а¶∞а¶ЬථаІАа¶∞ පඌයа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Уа¶∞ යආඌаІО а¶ШаІБа¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Уආඌ а¶ЄаІНටථඃаІБа¶Ча¶≤аІЗа¶∞ а¶Ча¶≤аІН඙ ථගඐаІЗබථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ѓаІЗ а¶Ча¶≤аІН඙аІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶Хඌ඙ а¶≠а¶∞аІНටග а¶Йа¶ЈаІНа¶£ а¶Па¶ХаІНඪ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЄаІЛ а¶Ха¶Ђа¶ња•§ а¶У а¶ЦаІБපග а¶єаІЯаІЗ а¶ЙථаІНඁඌබගථаІА а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗ, а¶ѓаІЗථ а¶Ча¶≤а¶Ња¶Яග඙аІЗ ඪථаІНටඌථа¶ХаІЗ а¶ЃаІЗа¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶ЫаІЗ а¶Па¶Х а¶°а¶Ња¶За¶®а¶ња•§ а¶У а¶Уа¶∞ ටа¶≤඙аІЗа¶Яа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЄаІЗටаІБ, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЯаІЛа¶≤ а¶ЖබඌаІЯа¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶ЦаІБа¶ђ а¶ХаІЬа¶Њ – а¶ЕඐපаІНа¶ѓа¶З ටඌа¶ХаІЗ а¶Єа¶Ња¶ЃаІБබаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶ЪаІБа¶ЃаІБ බගටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, ටඐаІЗа¶З ටඌа¶∞ ටа¶≤බаІЗපаІЗа¶∞ а¶∞а¶Єа¶ња¶Х а¶ХаІЬа¶ња¶∞ а¶ЃаІБබаІНа¶∞ගට а¶≠а¶Ња¶Ба¶Ь а¶ЦаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЕථаІБඁටග а¶ЄаІЗ බаІЗа¶ђаІЗа•§
а¶ѓаІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЃаІЯඁථඪගය ඕаІЗа¶ХаІЗ ටඌа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶Ыа¶∞ ඙ඌа¶Ба¶ЪаІЗа¶Х а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Па¶Х а¶ђа¶ња¶ХаІЗа¶≤ පаІЗа¶Ј ථඌ а¶єа¶УаІЯа¶Њ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Ыග඙а¶Ыග඙аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථаІМа¶Ха¶ЊаІЯ ටаІЛа¶≤а¶Њ а¶ЪаІБа¶≤а¶ЊаІЯ а¶≠ඌට а¶Яа¶Ча¶ђа¶Ч а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤аІЛа•§ ථබаІАа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶ХаІБаІЯඌපඌа¶∞ ඁපඌа¶∞аІА а¶Яа¶Ња¶ЩаІНа¶ЧඌථаІЛа¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ъа¶≤а¶ЫаІЗа•§ ථаІМа¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Жа¶∞ а¶ПටаІЛа¶З а¶ЕථаІБа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ ඁථ а¶Ца¶Ња¶∞ඌ඙ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа•§
а¶Жа¶Ѓа¶њ ටа¶Цථ а¶ЫඌටаІНа¶∞а•§ ඙аІБа¶∞ඌථаІЛ а¶ђаІНа¶∞а¶єаІНඁ඙аІБටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Б඲ඌථаІЛ ඙ඌаІЬ а¶Іа¶∞аІЗ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ බа¶≤ а¶ђаІЗа¶Ба¶ІаІЗ а¶єаІЗа¶ЯаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ а¶∞ඌටаІЗ а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£а¶™а¶ХаІНа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶Жа¶ХඌපаІЗа¶∞ ඙а¶Яа¶≠аІВඁගටаІЗ ථа¶ХаІНඣටаІНа¶∞а¶ЧаІБа¶ЪаІНа¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≠аІЗа¶ђаІЗ а¶≠аІЗа¶ђаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ බаІЗයථа¶ХаІНඣටаІНа¶∞ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶Па¶З а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶Яа¶ЊаІЯ ඙аІЛа¶Ја¶Њ а¶ђаІНа¶∞а¶єаІНඁ඙аІБටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Њ ඐග඙аІНа¶∞බඌඪаІЗа¶∞ ඁටаІЛа•§ ආගа¶Х а¶ђаІБа¶Эа¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ ථබаІАа¶∞ а¶Р ඙ඌаІЬаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶∞ඌට ඙а¶∞аІНඃථаІНට බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ඙ඌථගа¶∞ а¶У඙а¶∞ බගаІЯаІЗ а¶Еථඐа¶∞ට а¶Хටа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Жа¶≤аІЛа¶∞ а¶ђа¶≤ ථඌа¶Ъඌථඌа¶Ъа¶њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶У а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ъа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а•§ а¶Ха¶ЦථаІЛа¶З බаІБа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЧаІБථа¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶Ња¶Б඲ඌථаІЛ а¶Ша¶Ња¶ЯаІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛ а¶єаІЯаІЗ ඙ඌ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ ඕඌа¶Ха¶ња•§ ඪඌඁථаІЗ ධඌථаІЗ а¶ђа¶Ња¶ЃаІЗ а¶Йа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤ а¶ђа¶ња¶ЪගටаІНа¶∞ а¶ђа¶∞аІНа¶£аІЗа¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶Ха¶Њ а¶Ца¶ЄаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶Жа¶Хඌප ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІМаІЬаІЗ ධඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶ЃаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ යආඌаІО ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ а¶єа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа•§ а¶Жа¶∞ а¶ХаІА ටаІАа¶ђаІНа¶∞ ඁථаІЛа¶єа¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶Ха¶Ња¶∞ ඙аІБаІЬаІЗ а¶Ѓа¶∞а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶Ха¶Ња¶Ыа¶њ а¶Йа¶≤аІНа¶Хඌ඙ඌටаІЗа¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶З ථඌථඌа¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Ша¶Яථඌ а¶Ша¶ЯටаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶њ – ඙аІЛаІЬа¶Њ а¶ЧථаІНа¶ІаІЗ ඐඌටඌඪ а¶≠а¶Ња¶∞аІА а¶єаІЯаІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ьа¶ња¶ђ බගаІЯаІЗ а¶ЄаІНඐඌබ ථගаІЯаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶њ а¶ЄаІИථаІНа¶Іа¶ђ а¶≤ඐථаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶≤а¶Ња¶Ча¶ЫаІЗ а¶ђа¶Ња¶§а¶Ња¶Єа•§ а¶ЃаІГට ථබаІАа¶∞ ඙ඌаІЬ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Хඌප а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ьа¶ђа¶∞බඪаІНට ඁථаІЗ а¶єаІЯа•§
ථබаІАа¶∞ а¶Ша¶Ња¶ЯаІЗ а¶Па¶Хබගථ а¶Єа¶ња¶Ча¶Ња¶∞аІЗа¶Я а¶Іа¶∞ඌටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶єаІЯа•§ а¶ЪаІБа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Яа¶Ча¶ђа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗ а¶≠ඌට а¶ЂаІБа¶Яа¶ЫаІЗ, ථаІМа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЫаІИа¶ђа¶ња¶єаІАථ а¶Еа¶Вපа¶ЯඌටаІЗ а¶ЫаІЬඌථаІЛ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЯаІЗа¶Яа¶Њ, а¶ђа¶∞аІНපඌ, а¶Ьа¶Ња¶≤, බаІЬа¶њ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶њаІОа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶Ха¶њ а¶Ьගථගඪ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ а¶≠ඌඐටаІЗа¶У ඙ඌа¶∞ගථග а¶Ха¶њ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Па¶ЧаІБа¶≤аІЛ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЬаІЗථаІЗ а¶ђа¶ња¶ЄаІНа¶ЃаІЯаІЗ а¶Ъа¶ЃаІОа¶Ха¶Ња¶∞ යටඐඌа¶Х! ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗа¶З ඁථаІЗ а¶єа¶≤аІЛ а¶Иඪ඙аІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З බаІБа¶∞аІНබඌථаІНට а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට а¶Й඙а¶Хඕඌа¶Яа¶њ: а¶Ха¶ЪаІНа¶Ы඙ а¶У а¶Ца¶∞а¶ЧаІЛа¶ЄаІЗа¶∞ බаІМаІЬа•§ а¶ХаІЗ а¶ЬගටаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЛ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ? ටඌ ථගаІЯаІЗ ඁඌඕඌ а¶Ша¶Ња¶Ѓа¶Ња¶За¶®а¶ња•§ а¶ХаІЗථ а¶Ша¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Зථග? а¶Ча¶≤аІН඙а¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶њ ටඌයа¶≤аІЗ ඪඁඌ඙аІНටගටаІЗ ථаІЯ? а¶Па¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Ѓа¶Ьа¶Ња¶Яа¶Њ а¶Ха¶њ а¶≤аІБа¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Па¶ХඌථаІНට а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Жබග඙аІНа¶∞аІЗа¶∞а¶£а¶Ња¶∞ а¶ЙථаІНа¶ЃаІЛа¶ЪථаІЗ? а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ІаІАа¶∞а¶ХаІЗ බаІНа¶∞аІБට, а¶ђа¶ња¶ЬаІЯаІАа¶ХаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶∞аІНඕ, а¶Єа¶єа¶Ь а¶ХаІЗ а¶Еа¶Єа¶єа¶Ь, а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х а¶ХаІЗ а¶Жа¶Ха¶ЄаІНа¶Ѓа¶ња¶Х а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ а¶≠ඌඐටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯ? а¶Жа¶Ь а¶Па¶З ථаІМа¶Ха¶ЊаІЯ а¶Ъа¶њаІО а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤аІЛ බаІЗа¶ЦаІЗ ටඌа¶З ඁථаІЗ а¶єа¶≤аІЛа•§
඙аІЗа¶ЯаІЗа¶∞ ටа¶≤а¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶∞а¶В а¶Шථයа¶≤аІБබ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶ђа¶ЬаІЗа¶єа¶≤аІБа¶¶а•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЬаІНඃඌථаІНට¬† а¶Ха¶Ња¶Ба¶Єа¶Ња¶∞ ඕඌа¶≤а¶Њ а¶ђа¶≤аІЗа¶У а¶≠а¶Ња¶ђа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Йа¶≤аІНа¶ЯаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤аІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶ња¶єа¶ђа¶≤ а¶єаІЯаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗ ඕඌа¶Ха¶ња•§ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ බаІЗа¶ЦаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶њ а¶ѓаІЗථ а¶Єа¶ђ ඁථаІЗ යටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶ЫаІЗа•§ ඁඌඕඌа¶∞ а¶≠ගටа¶∞а¶Яа¶Њ а¶ЧаІБа¶Ѓа¶ЧаІБа¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Йආа¶≤аІЛ, ඁථаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶≠ඌඐථඌ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЦаІБа¶ђ බаІВа¶∞аІЗ а¶Ха¶њ а¶ѓаІЗථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЕථаІБа¶≠ඌඐථඌ а¶Ъа¶ња¶Б а¶Ъа¶ња¶Б а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶°а¶Ња¶Ха¶ЫаІЗа•§ а¶За¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ а¶Ѓа¶Ча¶Ьа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶Йа¶≤аІНа¶ЯаІЗ බаІЗа¶З, а¶Ха¶њ ඁථаІЗ යටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶ЫаІЗ ටඌ а¶Ьඌථඌа¶Яа¶Њ а¶ЦаІБа¶ђа¶З බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶ѓаІЗථаІЛа•§
а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶Єа¶єа¶Ь а¶єа¶З, а¶ХගථаІНටаІБ а¶≠аІЗටа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЧаІНа¶∞ටඌ а¶∞аІЯаІЗа¶З а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЄаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗ ථඌ – ටඌа¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ – ටඐаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯ ඁථаІЗ а¶єа¶≤аІЛа•§ ඁථаІЗ а¶єа¶≤аІЛ а¶ЄаІЗ а¶≠а¶Ња¶ђа¶ЫаІЗ а¶Ха¶ња¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶≤а¶ђаІЗа•§ а¶ЪаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІБථаІЗ ටඌа¶∞ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶Яа¶Њ а¶ЄаІН඙ථаІНබඁаІЯ а¶Жа¶∞ ථගඐගаІЬа•§
вАШа¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶Жа¶ЧаІБථ а¶єа¶ђаІЗ?вАЩ
а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ථගа¶∞ඐටඌ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗа•§ а¶ЪаІБа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶Ња¶БපаІЗа¶∞ а¶ЯаІБа¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЪаІЬ а¶ЪаІЬ а¶Ха¶∞аІЗ ඙аІБаІЬа¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶З а¶Ъа¶њаІОа¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЦаІЛа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶ЪаІНа¶Ы඙аІЗа¶∞ ඁඌඕඌ а¶ђаІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶Па¶≤аІЛ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ча¶≤а¶Њ පаІБථаІЗа•§ ඙аІНа¶∞аІМаІЭ а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞а¶≤аІЛ, вАШа¶Єа¶ња¶Ча¶Ња¶∞аІЗа¶Я а¶Іа¶∞а¶Ња¶За¶ђаІНඃඌථ?вА٠඙ඌа¶Яа¶ЦаІЬа¶њ බගаІЯаІЗ а¶ЪаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІБථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ටаІБа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞а¶≤аІЛа•§
вАШа¶Ха¶њ а¶∞ඌථаІНа¶ІаІЗථ?вАЩ
вАШа¶Ъа¶Ња¶Йа¶≤ а¶ЂаІЛа¶Яа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶њвАЩ, а¶ђа¶≤аІЗ а¶Еа¶∞аІНа¶Іа¶ЈаІНа¶ЂаІБа¶Я а¶єа¶Ња¶З ටаІБа¶≤а¶≤аІЛа•§ а¶ЫаІИаІЯаІЗа¶∞ а¶≠ගටа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ටа¶∞аІБа¶£ а¶Ха¶њ а¶ѓаІЗථаІЛ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§
вАШа¶Ъа¶Ња¶Ъа¶Ња¶Ѓа¶њаІЯа¶Њ а¶ђа¶ЊаІЬаІА а¶Ха¶З?вАЩ
а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Еа¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶єаІЛа¶Х ටඌа¶ХаІЗ а¶Іа¶∞а¶ђаІЛа•§
а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ а¶єа¶≤аІЛ а¶Жа¶Ьа¶ђ а¶ЬаІАа¶ђа•§ ඙ඌථගа¶∞ а¶Ца¶Ња¶ЄаІАа•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ђаІЯа¶ЄаІНа¶Х ථаІБථаІБа¶∞ ඁටаІЛ ටඌа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Ба¶Ъа¶Ња¶ЫаІЛа¶≤а¶Њ а¶Йබඌඁ а¶Ча¶≤а¶Ња¶Яа¶њ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ђаІБа¶ХаІЗа¶∞ а¶≠ගටа¶∞ а¶≤аІБа¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, ටඌа¶З а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞а¶єа¶ЄаІНа¶ѓа¶ЃаІЯ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£аІАа•§ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථа¶∞а¶Њ а¶Ьа¶ђа¶Ња¶З а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ХаІМපа¶≤ а¶ЖаІЯටаІНа¶ђаІЗ а¶ЖථටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථග а¶ђа¶≤аІЗ а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Ва¶Є а¶Жа¶ЄаІНඐඌබථаІЗ а¶ђа¶ЮаІНа¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඁයඌපаІБථаІНа¶ѓа¶Ъа¶Ња¶∞аІАа¶∞ а¶Ъа¶ЃаІОа¶Ха¶Ња¶∞ ථගа¶∞ඌ඙බ ඙аІЛа¶Ја¶Ња¶ХаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶З а¶ђа¶Њ а¶Пඁථ බаІЗа¶єа¶ђа¶∞аІНа¶Ѓ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ? බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶≤а¶Ња¶ЬаІБа¶Х ඁථаІЗ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶ѓаІМථа¶ЬаІАඐථаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ ථගපаІНа¶ЪаІЯа¶З а¶ЦаІБа¶ђ а¶ЧаІЛа¶Ыа¶Ња¶≤аІЛа•§ а¶Ъа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶≤а¶ња¶∞ а¶ЙටаІНටඌ඙аІЗ а¶ѓаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЄаІЗ а¶°а¶ња¶Ѓ а¶ЂаІЛа¶Яа¶ЊаІЯ, а¶≠а¶Ња¶ђа¶≤аІЗ а¶ЕථаІБ඙аІНа¶∞ඌථගට යටаІЗ а¶єаІЯа•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶∞аІНඕථඌаІЯ а¶Йа¶ђаІБ а¶єа¶УаІЯа¶Њ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Ха¶ЪаІНа¶Ы඙аІЗа¶∞ а¶Жබගа¶ЧථаІНට а¶Еඐථටа¶≠а¶Ња¶ђ ඙ඌථග, а¶Жа¶Хඌප а¶У а¶≠аІВа¶Ѓа¶њ а¶∞аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Е඙ඌа¶∞аІНඕගඐ а¶Хඌඁථඌ а¶Ьа¶Ња¶Ча¶њаІЯаІЗ ටаІЛа¶≤аІЗа•§
඙аІНа¶∞аІМаІЭ а¶Ха¶ЪаІНа¶Ы඙ පගа¶Ха¶Ња¶∞аІА බаІАа¶∞аІНа¶Ш а¶ХඌයගථаІАа¶∞ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЧаІЛаІЬඌටаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЛ ටඌа¶∞ а¶Жබග а¶ђа¶ЊаІЬаІА а¶Ыа¶ња¶≤аІЛ а¶Хඌථඪඌа¶Яа•§ а¶Ъඌ඙ඌа¶Зථඐඌඐа¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗ ඙බаІНа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ЊаІЬ а¶Ѓа¶∞ඌ඙ඌа¶Ча¶≤а¶Ња¶∞ ඙ඌаІЬаІЗа•§ ටඌа¶У а¶ЕථаІЗа¶Хබගථ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ха¶•а¶Ња•§ вАШබаІБа¶Яа¶Њ බඌථඌа¶∞ а¶≤а¶Ња¶За¶Ча¶Њ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ බаІНඃඌප а¶Ыа¶Ња¶ЗаІЬа¶Њ а¶Па¶∞а¶ШаІЗ а¶ХඌථаІНටථа¶Ча¶∞ а¶Жа¶Єа¶Ња¶ЫаІНа¶ѓа¶ња•§вАЩ
බගථඌа¶Ь඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶∞а¶Ња¶Ха¶Ња¶ЮаІНа¶ЪථаІЗа¶∞ ඙ඌаІЬаІЗ а¶ХඌථаІНටථа¶Ча¶∞а•§ ථаІМа¶Ха¶Њ а¶≠а¶Ња¶Єа¶њаІЯаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ а¶Іа¶∞ටаІЗ а¶Іа¶∞ටаІЗ බаІЗප ඐගබаІЗප а¶Жа¶Єа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶єа¶∞а¶єа¶Ња¶ЃаІЗපඌа¶З а¶Ъа¶≤аІЗа•§ ඙ඌаІЯаІЗа¶∞ ථගа¶ЪаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶њ පа¶ХаІНට ථаІЯ а¶ђа¶≤аІЗа•§ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ පаІАටа¶Ха¶Ња¶≤ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ а¶Іа¶∞а¶ђаІЗ а¶Ѓа¶∞а¶Ња¶ђаІНа¶∞а¶єаІНඁ඙аІБටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶П а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶ЊаІЯ, ඙ඌථග පаІБа¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶ѓа¶Цථ а¶єа¶Ња¶єа¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ђа¶ња¶∞а¶ђаІЗ ඐඌටඌඪаІЗ, ටа¶Цථ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЂаІЗа¶∞а¶Ња•§
а¶≠а¶Ња¶ђ а¶Ьа¶Ѓа¶њаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶њ පගа¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶∞ ඪඌඕаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЬඌථටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ ඙ඌථගටаІЗ а¶Ха¶њ а¶Ха¶∞аІЗ? а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ а¶°а¶ња¶Ѓ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Ха¶ња¶≠а¶Ња¶ђаІЗ? а¶Жа¶∞ а¶ШаІБа¶Ѓа¶ЊаІЯ а¶ХаІЛඕඌаІЯ?
вАШа¶Ж඙ථඌа¶∞а¶Њ а¶ђаІБа¶Эගථ ඙ඌථගа¶Х а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ыа¶ЄаІНටඌ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗථ, ථඌ?вАЩ
а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶єаІЯ а¶∞ඌට а¶ШаІЛа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶УබаІЗа¶∞ ථаІИපඌයඌа¶∞ ඪඁඌ඙аІНа¶§а•§ а¶Ъඌබа¶∞ а¶ЃаІБаІЬа¶њ බගаІЯаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ШаІЗа¶∞ а¶Жа¶ХඌපаІЗа¶∞ ථගа¶ЪаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗа¶Ыа¶њ ථаІМа¶Ха¶Ња¶∞ ඙ඌа¶ЯඌටථаІЗа•§ а¶єа¶Ња¶∞а¶ња¶ХаІЗථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤а¶ња¶ЭаІБа¶≤а¶њ а¶Ѓа¶Ња¶Ца¶Њ а¶Жа¶≤аІЛටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЖපаІЗ඙ඌපаІЗ а¶Ъа¶њаІОа¶Ха¶∞а¶Њ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶ЬаІНа¶ђа¶≤а¶ЫаІЗ ථගඐа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶ХඌපаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Й඙а¶∞ බගаІЯаІЗ а¶ЬаІАථ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ ඁටаІЛ а¶Ча¶ЃаІНа¶≠аІАа¶∞ а¶ЄаІЗа¶Ња¶Б а¶ЄаІЗа¶Ња¶Б පඐаІНබ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶Хබа¶≤ බаІЗපඐබа¶≤аІА ඙ඌа¶Ца¶њ а¶ЙаІЬаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Жа¶ХඌපаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶Ха¶њ а¶ѓаІЗථ а¶≠а¶Ња¶ђа¶≤аІЛа•§ а¶Хඕඌ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ ඙ඌථගа¶∞ බаІЗඐටඌ, а¶Ъа¶∞аІЗа¶∞ ඙аІАа¶∞, а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶ЃаІЗа¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБ а¶Па¶За¶Єа¶ђ ථගаІЯаІЗа•§ ඙аІНа¶∞аІМаІЭа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Па¶Єа¶ђ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗа¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕගටග а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ¬† а¶Єа¶ЪаІЗටථ а¶Ха¶∞а¶ЊаІЯа•§
යආඌаІО а¶Ђа¶ња¶Єа¶Ђа¶ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶≤аІЗ, вАШа¶За¶Ча¶≤а¶Ња¶ХаІЗ а¶Ха¶њ а¶ХаІБථ а¶Ха¶Ња¶≤аІЗ බаІЗа¶Ца¶ЫаІНа¶ѓаІЗථ?вАЩ
вАШа¶Ха¶њ?вАЩ
вАШа¶ђаІБа¶Эа¶≤аІЗථථඌа¶ЦаІЛ, а¶∞а¶Ња¶ЗටаІЗа¶∞ а¶ђаІЗа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶ЧаІЗ ථඌඁ ථගටаІЗ а¶єаІЯ ථඌ, а¶Еа¶∞а¶ШаІЗ а¶Хඕඌа¶З а¶ХаІЛа¶єа¶Ыа¶ња•§вАЩ
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЛа¶Ца¶ЃаІБа¶Ц а¶Па¶Ха¶ЯаІБ පаІБа¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶Ха¶њ? а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶Ха¶Ња¶Ыа¶њ а¶ХаІЛථ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗ а¶ХаІЛаІЬа¶Њ а¶ЯаІБа¶ђа¶Яа¶ђ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Йආа¶≤аІЛ?
вАШа¶ЧаІЗа¶≤аІЛа¶ђа¶Ња¶∞ а¶∞аІЗа¶≤а¶ђаІНа¶∞аІАа¶ЬаІЗа¶∞ ථගа¶ЪаІЗ а¶Ђа¶Ха¶Ђа¶Ха¶Њ а¶ЪඌථаІНථගа¶∞ඌටаІЗ බаІЗа¶ЦථаІБ а¶ЫаІЯа¶Цඌථ බඌаІЬа¶ња¶Еа¶≤а¶Њ а¶≤аІЛа¶Х а¶єа¶Ња¶°аІБа¶°аІБ а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ХаІЛа¶Ыа¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶За¶∞а¶Њ බаІБබගа¶ХаІЗ බаІБබа¶≤ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶єа¶ЗаІЯа¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЫаІЗа•§ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ѓаІЗ а¶Ьа¶За¶Ѓа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶ШаІБа¶Ѓ а¶Жа¶Єа¶Ыа¶ња¶≤ ථඌа¶ХаІЛ, ටඌа¶З а¶ХаІЗа¶Ња¶Ба¶Ъа¶Яа¶Њ а¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶Ња¶єа¶ња¶∞ а¶єаІЯаІЗа¶З а¶Па¶За¶Ча¶≤а¶Њ බаІЗа¶ЦаІБа¶®а•§ බаІЗа¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ѓаІЗ а¶•а•§ а¶Еඁථ а¶∞а¶Ња¶ЗටаІЗ බаІНа¶ѓа¶ЊаІЬයඌට а¶Йа¶Ъа¶Њ а¶Па¶ХаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶≤аІЛа¶Ха•§ а¶Єа¶≠а¶Ња¶∞а¶З а¶ЂаІЗа¶∞ ථඌа¶≠аІА ඙а¶∞аІНඃථаІНට ඪඌබඌ බඌаІЬа¶єа¶ња•§ а¶ЂаІЗа¶∞ а¶єа¶Ња¶°аІБа¶°аІБ а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЫаІЗа•§ а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЫаІЗ ටаІЛ а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЫаІЗ – а¶Ха¶Ња¶єаІБа¶∞а¶њ ඙ඌ а¶ЂаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶њ а¶ЫаІБа¶Ба¶ЪаІЗ ථඌа¶ЦаІЛ-вАЩ
а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ъඌබа¶∞аІЗа¶∞ а¶≠ගටа¶∞аІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІАටа¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ඕඌඐඌ ඙аІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ѓаІЗථаІЛа•§ ඙аІНа¶∞аІМаІЭ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ча¶≤а¶Њ ථඌඁගаІЯаІЗ а¶ХඌථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ЃаІБа¶Ц ථගаІЯаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЛ:
вАШඁථаІЗ а¶єа¶ЫаІНа¶ѓаІЗ, а¶Еа¶∞а¶ШаІЗ а¶ХаІЗа¶є а¶ХаІЗа¶є а¶єа¶Ња¶∞а¶ШаІЗ а¶Жථа¶Ьа¶∞аІЗ ඙ඌථа¶Ьа¶∞аІЗа¶З а¶ШаІБа¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶ПаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶ЯаІБ а¶Ча¶Њ а¶Ша¶ња¶Ја¶Њ а¶ђа¶За¶ЄаІЗа¶®а•§вАЩ
а¶ђаІБа¶Эа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶Ца¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞аІЛ а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶ХඌපаІЗ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЛа•§ а¶≠а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІЗ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞а¶њ, вАШа¶Па¶Цථ а¶Ха¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ?вАЩ
вАШа¶ЪаІБ඙ а¶Ха¶∞вАМаІНа¶ѓа¶Њ а¶ђа¶ЄаІЗථ ටаІЛ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶њ බаІЗа¶Ца¶Ыа¶ња•§ а¶Еа¶∞а¶Њ а¶єа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶єа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶Жа¶За¶Єа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶њ а¶ЬඌථаІЗථ, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶≤а¶Ња¶УаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓа¶Ча¶Ња¶≤а¶Ња¶ХаІЗ ඙ඌථаІНටаІЗ а¶Ыа¶Ња¶ЗаІЬа¶Њ බаІНа¶ѓа¶ЊаІЯа•§ බаІНа¶ѓа¶Ња¶Ца¶ЫаІНඃඌථ, а¶ЃаІЛථаІЗ а¶єа¶ЫаІНа¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓа¶Ча¶Ња¶≤а¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ПаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЯаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ඙ඌаІЯа¶Ња¶ЫаІНа¶ѓаІЗа•§вАЩ
а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶Єа¶ђа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ а¶Ча¶≤а¶Њ а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶њ а¶ѓаІЗථ බаІЗа¶Ца¶ЫаІЗа•§ а¶ЈаІНа¶ЯаІЗа¶°а¶њаІЯа¶Ња¶ЃаІЗ а¶ЂаІБа¶Яа¶ђа¶≤ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Па¶Хබගа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗඁථ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З ටඌа¶Ха¶ЊаІЯ, а¶ѓаІЗඁථ а¶ђа¶≤ а¶Па¶Х ඙аІЛа¶ЈаІНа¶Я ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ ඙аІЛа¶ЈаІНа¶ЯаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Жа¶∞ ටඌа¶Ха¶њаІЯаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ ඁඌඕඌа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Ша¶ЊаІЬаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶ШаІЛа¶∞аІЗ, а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІЗа¶∞а¶Ха¶Ѓа•§
вАШа¶Па¶Цථ а¶Еа¶∞а¶Ња¶ХаІЗ а¶≤а¶њаІЯаІЗ ඃබග а¶ХඌයගථаІА а¶Ха¶єа¶њ, ටඌයа¶≤аІЗ а¶Єа¶ђ а¶≠аІБа¶≤аІНа¶ѓа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЛа•§ а¶Еа¶∞а¶ШаІЗ а¶ЧаІБථ а¶Ча¶Ња¶єа¶ња¶≤аІЗ а¶Єа¶ђ а¶≠аІБа¶За¶≤аІНа¶ѓа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§вАЩ
вАШа¶Ъа¶Ња¶∞ ඙ඌа¶Ба¶Ъ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ша¶Яථඌ а¶Ша¶ЯаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ а¶Іа¶∞а¶Ыа¶њ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ѓаІЗ ටаІЛ а¶Жа¶За¶Ьа¶Ха¶Њ ඕඌа¶ХаІЗ ථаІЯ, а¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ බගථ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Пඁථ а¶Ша¶Яථඌ а¶Жа¶∞ а¶Ша¶ЯටаІЗ බаІЗа¶Цගථගа¶ХаІЛа•§ а¶Р а¶∞а¶Ха¶Ѓа¶З а¶Па¶Х а¶∞ඌටаІЗ а¶ХаІЛа¶Ъ а¶≤а¶њаІЯаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ча¶Ња¶ЩаІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ШаІБа¶∞а¶Ыа¶њ а¶Жа¶∞ ඙ඌථග а¶≤а¶ња¶Эа¶њаІЯаІЗ а¶≤а¶ња¶Эа¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶∞ටаІЛ а¶≠аІЯа¶°а¶∞ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌа¶ХаІЛа•§ а¶Пබගа¶ХаІЗ а¶∞а¶Ња¶Зට а¶ђа¶ЊаІЬа¶ЫаІЗ ටаІЛ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ЫаІЗа¶З а¶ХගථаІНටаІБ පගа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ ඙ඌа¶Ыа¶њ ථඌа¶ЦаІЛа•§ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶≠ඌඐථаІБ а¶∞ඌටа¶Яа¶Њ а¶ђаІБа¶Эа¶њ а¶ХаІБа¶Ђа¶Ња•§ а¶Пඁථග а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ යආඌаІО а¶Ча¶Ња¶ЩаІЗа¶∞ а¶ђаІБа¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦථаІБ а¶≠аІБа¶∞а¶≠аІБа¶∞а¶ња•§ а¶Жа¶ЄаІНටаІЗ а¶Жа¶ЄаІНටаІЗ а¶≠аІБа¶∞а¶≠аІБа¶∞а¶ња¶Яа¶Њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ЫаІЗа•§ а¶Ъа¶Ња¶З඙аІНа¶ѓа¶Њ а¶Іа¶∞ථаІБ а¶ХаІЛа¶Ъа¶Яа¶Ња¶ХаІЗа•§ а¶≠аІБа¶∞а¶≠аІБа¶∞а¶њ а¶Уආඌ а¶ѓа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶Яа¶Њ ඁථаІЗ а¶єа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗථаІБ а¶ЦаІЗа¶З඙аІНа¶ѓаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Йඕඌа¶≤ ඙ඌඕඌа¶≤ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤аІЛ а¶Жа¶∞ ටа¶≤ ඕඌа¶За¶ХаІНа¶ѓа¶Њ а¶ХаІЗඁථ а¶ЖපаІНа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓ а¶Жа¶≤аІЛ а¶ђа¶Ња¶∞а¶єа¶Ња¶ЗටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤аІЛа•§ යආඌаІО а¶Ха¶За¶∞а¶Њ ඐගයඌථ а¶ђаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඁටаІЛථ а¶єаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶Жа¶≤аІЛ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ЫаІЗ, ඙ඌථගа¶∞ а¶ЦаІНඃඌ඙ඌඁаІБа¶У а¶ђа¶ЊаІЬа¶ЫаІЗа•§ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶Яа¶Њ а¶≤а¶Ња¶≤ а¶ЯаІБа¶Ха¶ЯаІБа¶Ха¶Њ а¶Ѓа¶∞а¶ња¶ЪаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶єа¶ЗаІЯа¶Њ а¶ЧаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЛа•§ ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗ а¶Й а¶≠а¶Ња¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ а¶Йආа¶≤аІЛа•§ а¶Пබගа¶ХаІЗ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶њ ටаІЛ а¶∞аІЗа¶°а¶њ, а¶ХаІЗа¶Ња¶Ба¶Ъ ටаІБа¶≤а¶Ыа¶њ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶ђаІЛ а¶Ха¶єаІНа¶ѓа¶Ња•§ බаІЗа¶ЦථаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඪඌ඙ а¶Жඪඁඌථ ඕඌа¶За¶Ха¶Њ ථඌа¶За¶Ѓа¶Њ а¶Жа¶За¶≤аІЛа•§ а¶Еа¶∞ а¶Ча¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶∞බගа¶ХаІЗа¶У а¶≤а¶Ња¶≤ а¶Жа¶≤аІЛа•§ ඁථаІЗ а¶єа¶ЫаІЗ а¶ђа¶Ња¶ђа¶≤а¶Њ а¶ХඌආаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІБථ а¶ЬаІНа¶ђа¶≤а¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶∞ а¶ЪаІЛа¶Ц බаІБа¶Яа¶Њ а¶Ха¶њ а¶Ха¶єа¶ђаІЛ, а¶ХаІЗа¶Ња¶Ба¶Ъ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶∞ යඌටаІЗа¶З ඕඌа¶За¶ХаІНа¶ѓа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤ – а¶Ѓа¶Ња¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞ථаІБ ථඌа¶ЦаІЛа•§ බаІЗа¶ЦථаІБ පඌа¶≤а¶Њ а¶єа¶ња¶єа¶њ а¶Ха¶За¶∞вАМаІНа¶ѓа¶Њ а¶єа¶Ња¶Єа¶ЫаІЗа•§ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶њ යඌට ථඌඁගаІЯаІЗ а¶≤а¶УаІЯඌටаІЗ а¶Еа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛ а¶Эа¶Ха¶Эа¶Ха¶Њ а¶∞аІВ඙ඌа¶∞ ඁටථ а¶єаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶њ ටаІЛ а¶ђаІЗа¶ХаІБа¶ђа•§ а¶ЂаІЗа¶∞ ටаІБа¶≤ථаІБ а¶ХаІЗа¶Ња¶Ба¶Ъа•§ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶ђаІБа¶За•§ а¶ѓаІЗа¶З а¶ХаІЗа¶Ња¶Ба¶Ъ ටаІБа¶≤а¶Њ, а¶Ыඌ඙аІЗа¶∞ а¶єа¶Ња¶Єа¶њ ඐථаІНа¶І а¶єаІЯаІНа¶ѓа¶Њ а¶ЧаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЛ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Њ а¶Жа¶≤аІЛ а¶Еඁථග а¶≤а¶Ња¶≤ а¶єаІЯа¶Њ а¶ЧаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЛа•§ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђаІБа¶Эගථ а¶ШаІЛа¶∞а¶З ඙ඌа¶За¶≤а•§ а¶єа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶єа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶ЂаІЗа¶∞ а¶ХаІЗа¶Ња¶Ба¶Ъа¶Яа¶Њ ථඌඁගаІЯаІЗ а¶≤ගථаІБа•§ а¶Ѓа¶Ња¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞ථаІБ ථඌа¶ХаІЛа•§ а¶ђа¶Ња¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶З а¶Ша¶Яථඌ а¶Ша¶ЯටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤аІЛа•§ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶њ а¶ХаІЗа¶Ња¶Ба¶Ъ ටаІБа¶≤а¶њ, а¶Й а¶≤а¶Ња¶≤ а¶єаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ – ථඌඁගаІЯаІЗ а¶≤а¶њ а¶Й а¶єа¶Ња¶ЄаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Єа¶єаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞ථаІБ ථඌа¶ЦаІЛа•§ а¶Ъа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Х ඁඌඕඌ ඕඌа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Х ඁඌඕඌ ඙ඌа¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶ђаІЗаІЬඌටаІЗ а¶≤а¶Ња¶ЧථаІБа•§ ඙ඌа¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶ђаІЗаІЬа¶Ња¶≤аІЗ а¶єа¶ђ а¶Ха¶њ, а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа¶Њ ඕඌඁග а¶Уа¶ЦඌථаІЗа¶З බаІЗа¶Ца¶њ а¶≠аІБа¶∞а¶≠аІБа¶∞а¶ња•§ а¶ЂаІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶Жа¶≤аІЛ, а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ, а¶Ыඌ඙, а¶ђаІБа¶Х а¶Ьа¶Ња¶≤ඌථаІНа¶ѓа¶Њ а¶єа¶Ња¶Єа¶ња•§ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶њ а¶Ха¶њ ඙ඌа¶Ча¶≤ а¶єаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶Ыа¶ња•§ ඁථаІЗ а¶єа¶ЫаІЗ а¶єа¶Ња¶Ба¶∞ а¶Єа¶ђ පа¶ХаІНටග а¶Й а¶Ха¶Ња¶За¶∞а¶Њ а¶≤а¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶њ а¶ЄаІНඐ඙ථаІЗа¶∞ а¶ШаІЛа¶∞аІЗ а¶≠ඌඪටаІЗ а¶≤а¶Ња¶ЧථаІБа•§
а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓа¶Яа¶Њ а¶єа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶єа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶Йа¶ЗආаІНа¶ѓа¶Њ а¶Жа¶За¶≤аІЛ а¶Ча¶Ња¶ЩаІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶Жа¶∞ а¶Еඁථග а¶Ыඌ඙а¶Яа¶Ња¶У а¶ХаІБථආаІЗ ඕඌа¶ХаІНа¶ѓа¶Њ а¶Жа¶За¶Єа¶Њ а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞а•§ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ ඪථа¶Эа¶Њ а¶ђаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ЬаІНа¶ЬаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ඁථаІЗ а¶єа¶Ыа¶ња¶≤аІЛа•§ а¶Йа¶∞ а¶ЪаІЛа¶Ц බаІБа¶Яа¶Њ а¶Ьඌථග а¶Ѓа¶ІаІБа¶∞ а¶ЂаІЛа¶Яа¶Ња•§ ඙ඌа¶Ча¶≤а¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ха¶ЗථаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶™а¶Ња•§ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶њ බаІЗа¶Ца¶Ыа¶њ а¶Жа¶∞ බаІЗа¶Ца¶Ыа¶њ, ඁථаІЗ а¶єа¶За¶ЫаІЗ а¶ХаІБථආаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ча¶Ња¶ЩаІЗа¶∞ а¶≠а¶∞а¶Њ ඥаІЗа¶Й а¶єа¶Ња¶Ба¶∞ а¶ђаІБа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶За¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶За¶Єа¶Њ ඙аІЬа¶ЫаІЗа•§ බаІЗа¶ЦථаІБ බаІБа¶Эථඌ а¶≤а¶Ња¶ЪටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЄаІЗ а¶Ха¶њ а¶≤а¶Ња¶Ъа¶®а•§ а¶Еа¶∞а¶ШаІЗ а¶≤а¶Ња¶ЪаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ а¶Жа¶≤аІЛа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶У ඐබа¶≤аІНа¶ѓаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤аІЛа•§ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶∞аІБа¶єа¶њ а¶Ѓа¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶∞а¶ХаІНට, а¶Ха¶ЦථаІЛ ඐථа¶Яа¶њаІЯа¶Њ, а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶ђа¶Њ а¶ђа¶Ња¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЂаІБа¶≤а•§ а¶Хට а¶ѓаІЗ а¶∞а¶В а¶Еа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ, а¶єа¶Ња¶Ѓа¶њ а¶ЬаІАа¶≠а¶∞вАМаІНа¶ѓа¶Њ බаІЗа¶Ца¶Ыа¶ња•§
а¶Ыඌ඙а¶Яа¶Њ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Ха¶ЊаІЯа¶Њ а¶єа¶Ња¶ЫටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤аІЛа•§ а¶єа¶Ња¶ЫටаІЗ а¶єа¶Ња¶ЫටаІЗ යආඌаІО а¶Ха¶За¶∞а¶Њ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓа¶Яа¶Њ а¶Єа¶є а¶Й බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶Жа¶≤аІЛа¶∞ а¶ђа¶≤ а¶єаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶Жа¶∞ а¶єа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶Ѓа¶Ња¶Э ථබаІАටаІЗа•§вАЩ
а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ පගа¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶Жа¶∞ а¶ђа¶≤а¶≤аІЛ ථඌ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа•§ а¶Ча¶≤аІН඙ පаІЗа¶Ј а¶єа¶≤аІЛ ටа¶Цථ а¶∞ඌට ටගථа¶Яа¶Ња•§ а¶ЫаІЛа¶ЯථаІМа¶Ха¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ШаІБඁඌථаІЛа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ а¶єа¶ђаІЗථඌ а¶Жа¶∞ ටඌа¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶ШаІБа¶Ѓа¶У ථаІЗа¶З а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа•§ ථаІМа¶Ха¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ђа¶њаІЯаІЗ ථඌඁටаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЛ, ඙аІЗа¶Ыථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ, вАШа¶≤а¶Ња¶Ђ а¶Эа¶Ња¶Б඙ ටаІЛ පаІЯටඌථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь-вАЩ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ХаІЬа¶Њ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ථගа¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ а¶ЯаІЗа¶∞ ඙аІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓ – а¶ХаІБаІЯඌපඌаІЯ ඃටබаІВа¶∞ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§
ථබаІАа¶∞ ඙ඌаІЬ а¶ѓаІЗථаІЛ а¶Ца¶ЊаІЬа¶Њ а¶ХаІНа¶≤аІАа¶Ђа•§ а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶ЙආаІЗ බаІЗа¶Ца¶њ ථаІМа¶Ха¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶∞а¶ња¶ХаІЗථаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛ а¶Яа¶ња¶Ѓа¶Яа¶ња¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓ පගа¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶∞ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа¶∞ ඁථග а¶єаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ බаІЗа¶Ца¶ЫаІЗа•§ ඙аІЗа¶ЫථаІЗ а¶Эඌ඙ඪඌ, а¶Еа¶ЄаІН඙ඣаІНа¶Я а¶∞ඌටаІЗа¶∞ ථබаІА а¶∞аІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤, а¶ХаІБаІЯඌපඌаІЯ а¶Ца¶ЊаІЬа¶ња¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ЕබаІГපаІНа¶ѓ, а¶ХගථаІНටаІБ යආඌаІО යආඌаІО а¶Ѓа¶Ња¶Ы а¶ђа¶Њ а¶ХаІЛථ а¶Еටගа¶≤аІМа¶Ха¶ња¶Х а¶ЬаІАа¶ђаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶∞аІА а¶Ъа¶≤а¶Ња¶ЂаІЗа¶∞а¶Ња¶∞ පඐаІНබ යටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤аІЛ, а¶ѓаІЗටаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞аІЛ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ ටඌа¶Ха¶Ња¶≤а¶Ња¶Ѓ, ථаІМа¶Ха¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶∞а¶ња¶ХаІЗථаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІАа¶£ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХаІНа¶ЈаІАа¶£а¶§а¶∞ а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђ ටа¶Цථ ථගඐගаІЬ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ ඁගපаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁථаІЗ а¶єа¶≤аІЛ а¶Р а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶Ча¶∞аІНටаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶ђаІГබаІНа¶Іа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ බаІЗа¶Ца¶ЫаІЗа•§
а¶Па¶∞඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථаІЗපඌ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶∞ඌටаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶∞а¶єаІНඁ඙аІБටаІНа¶∞аІЗа¶∞ ඙ඌаІЬ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ђаІЗаІЬඌථаІЛа•§ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАа¶∞а¶Њ ඕඌа¶ХටаІЛ, а¶УබаІЗа¶∞ а¶Па¶°а¶≠аІЗа¶ЮаІНа¶Ъа¶Ња¶∞ ඕඌа¶ХටаІЛ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Уа¶∞а¶Њ а¶ХаІНа¶≤ඌථаІНට а¶єаІЯаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤аІЛа•§ а¶Па¶Ха¶Њ а¶Па¶Ха¶Њ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤а¶Ња¶Ѓ ථටаІБථ а¶Ча¶Ьа¶њаІЯаІЗ а¶Уආඌ а¶Ъа¶∞аІЗа•§ а¶Па¶Ха¶єа¶Ња¶Ба¶ЯаІБ ඙ඌථග, а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶Ъа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ца¶ЊаІЬа¶њ ඁටаІЛථ, ථа¶ХаІНඣටаІНа¶∞а¶Ња¶≤аІЛа¶Хගට а¶∞ඌටаІЗ а¶Ца¶ЊаІЬа¶ња¶∞ ඙а¶ХаІЗа¶ЯаІЗа¶∞ ඙ඌථග а¶ЃаІБа¶Ца¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බаІЗа¶Ца¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗа•§ а¶∞ඌටа¶Ьа¶Ња¶Ча¶Њ ඙ඌа¶Ца¶ња¶∞а¶Њ බа¶≤ а¶ђаІЗа¶Ба¶ІаІЗ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ, ටඌа¶∞ а¶Па¶Х බаІБа¶Яа¶Њ ඙ඕ а¶≠аІБа¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶ЄаІЗа¶З ඙ඌа¶Ца¶ња¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶Ха¶њ а¶°а¶Ња¶Х, а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶ХаІЗ а¶ПථаІЗ а¶ѓаІЗථаІЛ а¶ђа¶Ња¶≤а¶њаІЯа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ ථගа¶ЪаІЗ а¶ЧаІБа¶Ба¶ЬаІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ බගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶∞¬† а¶Е඙ඁඌථаІЗ а¶єаІБ а¶єаІБ а¶Ха¶∞аІЗ а¶УආаІЗ а¶Ъа¶Ња¶∞බගа¶Ха•§ а¶ђаІБථаІЛа¶Эа¶Ња¶ЙаІЯаІЗа¶∞ ඐථаІЗ а¶ЧаІЛа¶Щඌථග а¶УආаІЗа•§ ඙ඌථගа¶∞ а¶≠ගටа¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶ђа¶Њ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶∞ а¶ЭаІБ඙а¶Эඌ඙ පඐаІНа¶¶а•§ а¶≠а¶ња¶ЬаІЗ а¶ђа¶Ња¶≤а¶ња¶∞ ආඌථаІНа¶°а¶Њ ථගа¶ГපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶≠аІЯаІЗ а¶Ъа¶њаІО а¶єаІЯаІЗ පаІБаІЯаІЗ ඕඌа¶Ха¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІМටаІБа¶єа¶≤ а¶ЃаІЗа¶ЯаІЗа¶®а¶Ња•§ а¶ЪаІЛа¶Ц ඙ගа¶Я඙ගа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Є ඁටаІЛ පаІАටаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ѓа¶ЊаІЯаІА ඙ඌа¶Ца¶њ ඙ඌප බගаІЯаІЗ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶ЧаІНа¶∞аІАа¶ђа¶Ња¶ХаІЗ а¶Па¶Х බаІБа¶З, а¶Па¶Х බаІБа¶З а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗа•§ а¶ЧаІЬඌටаІЗ а¶ЧаІЬඌටаІЗ а¶Уа¶∞ ඙ගа¶ЫаІБ ථаІЗа¶З, බаІБа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІЛථඌ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Жа¶∞аІЛ බаІБа¶Яа¶њ ඙ඌа¶Ца¶ња¶∞ а¶ЃаІГබаІБ а¶Жа¶≤а¶Ња¶™а•§
а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶єаІБа¶ЯаІНа¶Яа¶ња¶∞а¶њ ඙ඌа¶Ца¶ња¶ХаІЗ а¶Ъа¶њаІО а¶єаІЯаІЗ ඙ඌ බаІБа¶ЯаІЛ а¶Жа¶ХඌපаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ ටаІБа¶≤аІЗ බගටаІЗ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ЃаІЗаІЯаІЗ а¶єаІБа¶ЯаІНа¶Яа¶ња¶∞а¶њ а¶°а¶ња¶Ѓ ඙ඌаІЬа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ, а¶ЄаІЗ а¶ѓаІЗ ඐගපඌа¶≤ а¶°а¶ња¶Ѓ ඙ඌаІЬа¶ђаІЗ ටඌටаІЗ ඙аІГඕගඐаІА а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, ටඌа¶З а¶Жа¶ХඌපаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶°а¶ња¶Ѓ ඙ඌаІЬа¶ЫаІЗ а¶≠аІЗа¶ђаІЗ а¶Ъа¶њаІО а¶єаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶ЧаІНа¶∞а¶є ථගаІЯаІЗ а¶єаІБа¶ЯаІНа¶Яа¶ња¶∞а¶њ ඙ඌа¶Ца¶ња¶Яа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Ха¶Ња¶За•§ ටаІАа¶ђаІНа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІЗ ඙ඌа¶Ца¶ња¶Яа¶Њ а¶°аІЗа¶ХаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЯаІНа¶Яа¶њ, а¶ЯаІНа¶Яа¶њ, а¶єаІБа¶ЯаІНа¶Яа¶ња¶Яа¶њ, а¶єаІБа¶ЯаІНа¶Яа¶ња¶Яа¶ња•§ а¶ѓаІЗ බගа¶ЧථаІНටа¶∞аІЗа¶Ца¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤аІЛ а¶Еа¶ЄаІАа¶ЃаІЗ ටඌ а¶ѓаІЗථ ථගа¶ГපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ ථаІИа¶Ха¶ЯаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶≤аІЛа•§ а¶ПටаІЛ а¶Ѓа¶ІаІБа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛ, ඁථаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Па¶∞ පаІЗа¶Ј ථаІЗа¶З; а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶Йа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤, а¶ІаІАඁඌථ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶З ථගඪа¶∞аІНа¶Ч а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶ЂаІЛа¶∞а¶£ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З ඪඌඕаІЗ а¶ђа¶Ња¶≤а¶ња¶∞ а¶У඙а¶∞, ඙ඌථගа¶∞ а¶≠ගටа¶∞ а¶Эа¶Ња¶ЙаІЯаІЗа¶∞ ඙ඌටඌаІЯ – а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ѓа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Єа¶ђа¶З а¶Жа¶≤аІЛ а¶ЫаІЬа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ЬаІЗа¶ЧаІЗ а¶Йආа¶ЫаІЗа•§
а¶ХаІЛථ а¶∞ඌටаІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ња¶≤аІЯ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ђа¶єаІБබаІВа¶∞ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶За•§ а¶Жа¶ІаІЛ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ а¶ЦаІЬа¶ђа¶Ња¶БපаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЭаІЛ඙а¶Эа¶ЊаІЬаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ඁථаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶ЄаІЗа¶За¶Єа¶ђ ඙аІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶Жа¶∞аІЛ බаІВа¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶За•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ථබаІАа¶∞ а¶∞аІЗа¶Ца¶Њ, а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ඙ඌа¶Ца¶ња¶∞ а¶°а¶Ња¶Х – а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ха¶Ња¶ґа•§ ඙ඌаІЬаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ ඕඌа¶Ха¶њ, а¶Йа¶Ба¶ЪаІБ ඙ඌаІЬ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඁඌආаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Ъа¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Ха¶Ња¶За•§ а¶Па¶Ха¶∞ඌටаІЗ а¶Р а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Па¶Х а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ ටගථа¶Яа¶Њ а¶≤аІЛа¶Х а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶ЪටаІБа¶∞аІНඕ а¶Па¶Ха¶Ьථа¶ХаІЗ යටаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Уа¶∞а¶Њ а¶ЯаІЗа¶∞а¶З ඙ඌаІЯථග а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶∞аІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Жа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞ а¶ЃаІБа¶Ца¶ђа¶Ња¶Ба¶Іа¶Њ а¶Жа¶∞аІНටа¶Ъа¶њаІОа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ ඙ඌа¶Ца¶ња¶∞а¶Њ ඙а¶∞аІНඃථаІНට ඙ඌа¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЛа•§ ඐඌටඌඪ а¶ЄаІНටඐаІНа¶І යටඌපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗ а¶ЧаІЛа¶Ща¶Ња¶≤аІЛа•§ ටඐаІБ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶ЄаІЗ ඕඌа¶Ха¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Уа¶∞а¶Њ ඪබаІНа¶ѓа¶ЃаІГට а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ පа¶∞аІАа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඁඌඕඌ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІЗ а¶≠а¶∞аІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶≠аІЗа¶ђаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Уа¶∞а¶Њ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЪаІЗථඌа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ђаІЛ, а¶ХගථаІНටаІБ ටඌ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶єа¶≤аІЛ а¶®а¶Ња•§
а¶ХගථаІНටаІБ а¶∞ඌටаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶∞ඌට а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤, පගа¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З බаІГපаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶єа¶≤аІЛ а¶®а¶Ња•§
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЃаІЯඁථඪගа¶Ва¶є а¶ѓаІЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞аІЛ а¶Ха¶ЪаІНа¶Ы඙ පගа¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶∞ ඪඌඕаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗа•§ а¶Уа¶ЦඌථаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶Х а¶За¶єа¶≤аІМа¶Ха¶ња¶Х а¶Еа¶Ѓа¶∞а¶§а¶Ња•§ а¶Па¶З බаІАа¶∞аІНа¶Ша¶ЬаІАа¶ђаІА (ටගථප а¶ђа¶Ыа¶∞?) ඃබග බаІЯа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ටඌයа¶≤аІЗа¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ පаІЛа¶ђа¶Ња¶∞/а¶Єа¶ЩаІНа¶Ча¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ба¶ЪаІЗа¶∞ а¶Ха¶ња¶Йа¶ђ ථගаІЯаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ ඙аІЬаІЗа¶Ыа¶њ ටඌа¶∞ а¶ЄаІБа¶∞а¶Ња¶єа¶Њ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶ђа¶ЙаІЯаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶њ; ටගа¶Жа¶ХаІЗ а¶Ха¶ЪаІНа¶Ы඙аІЗа¶∞ а¶Жа¶За¶°а¶њаІЯа¶Њ а¶ЬඌථඌටаІЗ යටඌපඌаІЯ а¶У а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ පаІБа¶ІаІБ а¶Шථ а¶Шථ ඁඌඕඌ ථඌаІЬඌටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤аІЛ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶≤а¶≤аІЛ, вАШටඌа¶Ха¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶єаІЯ, а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІЛ а¶≠аІЗа¶ђаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶≠аІЗа¶ђаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ…вА٠ටගа¶Ж а¶Уа¶∞ а¶ђаІЬ а¶ђаІЬ а¶ЪаІЛа¶Ца¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶≠ඌඐථඌаІЯ а¶Жа¶ЪаІНа¶ЫථаІНථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶≠аІЛа¶≤ඌටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ьඌථග ටගа¶Ж а¶Па¶ЦථаІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶≠аІЗа¶ђаІЗ а¶ЙආටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ а¶єаІЯටаІЛ а¶Єа¶ЃаІЯ ඙аІЗа¶≤аІЗ а¶Па¶Хබගථ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЛ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶ЦථаІЛ ඙ඌа¶∞аІЗථගа¶Уа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАШа¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІЛථඌа¶≤аІА а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЪаІНа¶Ъа¶Њ а¶Ха¶ЪаІНа¶Ы඙… а¶ХаІЗඁථ а¶єаІЯ а¶ђа¶≤ටаІЛ … පаІБථග?вА٠ටගа¶Ж ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ а¶ђаІЗа¶ЧаІЗ ඁඌඕඌ ථඌаІЬа¶ЊаІЯ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶≤аІЗ, вАШථඌ…а¶Ж…вАЩ¬† а¶Уа¶∞ а¶Па¶З ථа¶Юа¶∞аІНඕа¶Х а¶≠ඌඐථඌа¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞аІНටථඌබаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ආаІЗа¶ХаІЗ… а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶≤а¶њ вАШබаІЗа¶ЦаІЛ ටගа¶Ж… а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Хබගථ… а¶ХගථаІНටаІБ а¶У а¶ХටаІЛа¶Ха¶Ња¶≤ а¶ѓаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗ… а¶Па¶З පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІЗа¶Й ටඌа¶∞ පаІЗа¶Ј බаІЗа¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ ථඌ… ටඌа¶∞඙а¶∞а¶У ඕඌа¶Ха¶ђаІЗ, а¶ђаІБа¶ЭаІЗ බаІЗа¶Ц, а¶ЕබаІНа¶≠аІБටа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗ, ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞а¶ХаІЗа¶У පගа¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶≠а¶Ња¶ђа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ, а¶Ха¶ЪаІНа¶Ы඙ පගа¶Ха¶Ња¶∞аІА… а¶Жа¶∞ ඃබග а¶Уа¶Єа¶ђ а¶Ша¶ЯаІЗа¶З…вАЩ
ඃබගа¶У ථබаІА ථаІЗа¶З – ටඌа¶∞඙а¶∞а¶У ටගа¶Ж а¶ЃаІБа¶∞аІНа¶Ыа¶Њ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБටаІЗа¶З ටගа¶Жа¶ХаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶њ а¶Ха¶∞ඌටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ а¶®а¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ха¶ЪаІНа¶Ы඙ පගа¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЛа¶За•§
а¶∞а¶Ъථඌ: аІІаІѓаІЃаІѓ
а¶≤аІЗа¶Ца¶ХаІЗа¶∞ ථаІЛа¶Я:: а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІА-а¶ђа¶Ња¶Ъа¶Х а¶Єа¶∞аІНඐථඌඁ ථඌа¶За•§ ටඌа¶З а¶Жа¶Ѓа¶њ вАШа¶ЄаІЗвАЩ а¶ХаІЗ ඙ඌа¶≤аІНа¶ЯаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶њ вАШපаІЗвАЩа•§
а¶Ха¶Ња¶Ьа¶≤ පඌයථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶Ь
Latest posts by а¶Ха¶Ња¶Ьа¶≤ පඌයථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶Ь (see all)
- а¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња¶Ѓа¶Ча¶Ња¶≤а¶Њ - ථа¶≠аІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ 27, 2013