а¶ЄаІИаІЯබ а¶Жа¶≤аІА а¶Жයඪඌථ: а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ – вАЬа¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≤а¶ња¶Ца¶ђа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐвАЭ а¶®а¶њаІЯа¶Њ Featured
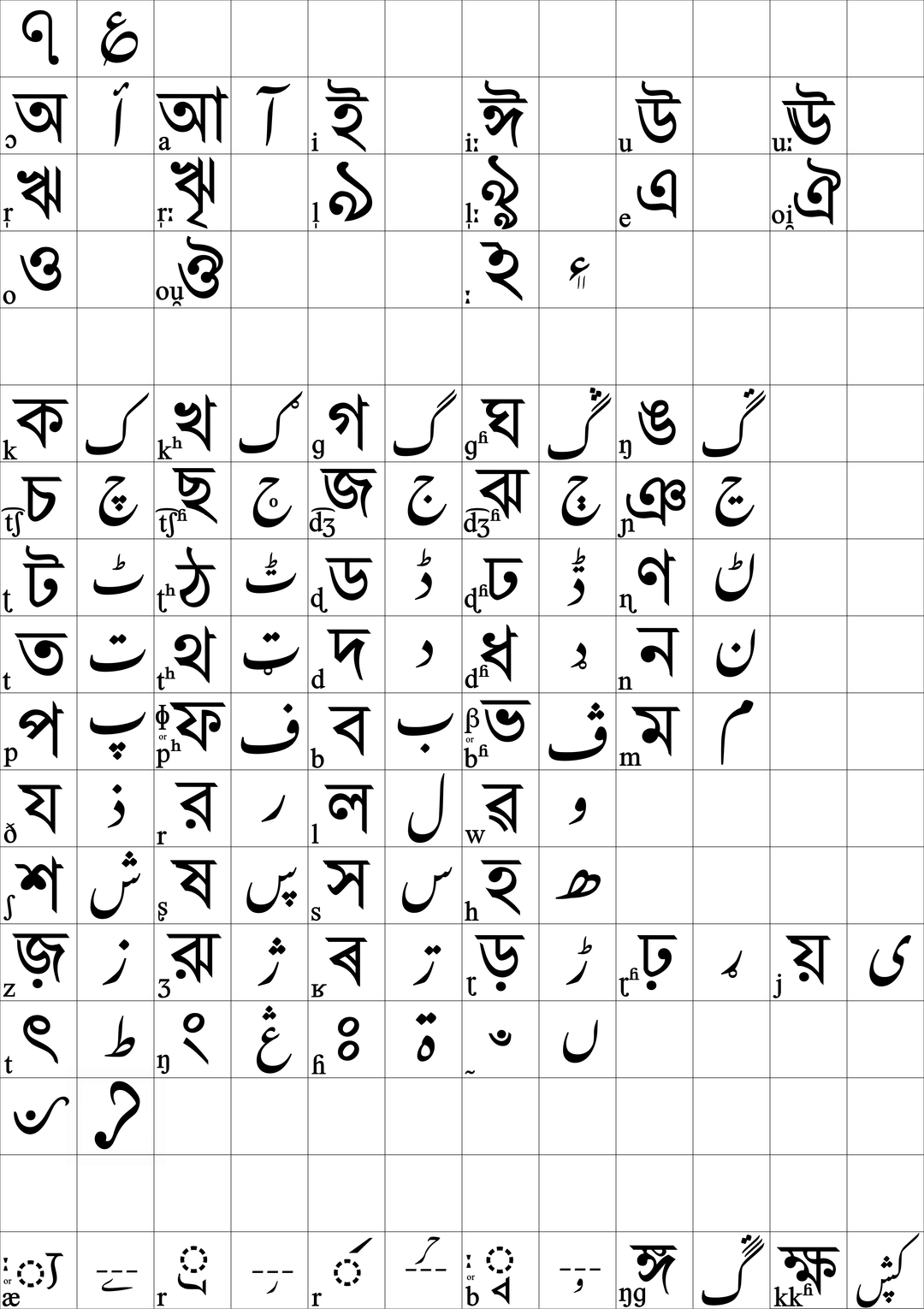
аІІаІѓаІѓаІ™ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЄаІИаІЯබ а¶Жа¶≤аІА а¶Жයඪඌථ (аІІаІѓаІ®аІ® – аІ®аІ¶аІ¶аІ®) вАЬа¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓвАЭ а¶®а¶Ња¶ЃаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶З а¶≤аІЗа¶ЦаІЗථ, а¶Йථඌа¶∞ ථඌඁаІЗ а¶Ъа¶Ња¶≤аІБ ඕඌа¶Ха¶Њ ථඌථඌථ а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶Яа¶ња¶Х а¶У а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞ඪ඙аІЗа¶ХаІНа¶Яа¶ња¶≠ ටаІБа¶За¶≤а¶Њ а¶Іа¶∞аІЗථ
ටаІЛ, а¶Еа¶ђа¶≠а¶њаІЯа¶Ња¶Єа¶≤а¶њ а¶Па¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ХаІЛථ а¶≠аІЗа¶∞а¶ња¶Ђа¶Ња¶За¶° а¶єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶≤ а¶ЯаІНа¶∞аІБඕ ථඌ, а¶ХගථටаІБ а¶Па¶Ха¶ЗඪඌඕаІЗ а¶єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶≤ а¶За¶≠аІЗථаІНа¶Яа¶ЧаІБа¶≤ඌටаІЗ а¶Пථа¶ЧаІЗа¶За¶Ь ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Па¶Ха¶Ьථ ඁඌථаІБපаІЗа¶∞ а¶ђаІЯඌථ, а¶ѓаІЗа¶За¶Яа¶Њ а¶єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶≤ а¶∞аІЗа¶Ђа¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶Є а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ а¶ЂаІБа¶≤-඙аІНа¶∞аІБа¶Ђ а¶Ша¶Яථඌ ථඌ а¶єа¶За¶≤аІЗа¶У а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞аІЗа¶Ђа¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶Єа¶њаІЯа¶Ња¶≤ ඙аІЯаІЗථаІНа¶Я, а¶ѓаІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶∞ථаІЗ а¶Йථඌа¶∞ а¶Хඕඌа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Єа¶Ња¶∞а¶ЂаІЗа¶За¶Є а¶≤аІЗа¶≠аІЗа¶≤аІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ, а¶ѓа¶Ња¶Ъа¶Ња¶З а¶Ха¶За¶∞а¶Њ බаІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ а¶єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶Ња¶Ь
а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ша¶Яථඌ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ, ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ а¶Жа¶Ѓа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђаІЗපගа¶∞а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ша¶Яථඌа¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤ඌ඙аІЗ а¶Па¶ЦථаІЛ а¶ЯаІНа¶ѓа¶Ња¶ђаІБ а¶єаІЯа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗථ а¶Па¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ථගаІЯа¶Њ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ ථඌ! а¶ХගථටаІБ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶њ а¶ЬඌථටаІЗ а¶У а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ а¶єа¶За¶≤аІЗ ටаІЛ а¶За¶Ѓа¶ња¶°а¶њаІЯаІЗа¶Я ඙ඌඪаІНа¶ЯаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗа¶З ටаІЛ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ ටඌа¶Ха¶Ња¶ЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗ а¶Жа¶ЧаІЗвА¶
ටаІЛаІЛ а¶Па¶З а¶Ьගථගඪа¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Ьඌථග а¶ѓаІЗ, а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶єа¶∞а¶Ђ а¶ЪаІЗа¶За¶ЮаІНа¶Ь а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Хඕඌ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ а¶Жа¶Ѓа¶≤аІЗ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ-а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ ඕගа¶Ха¶Њ а¶Йආа¶Ыа¶ња¶≤, ටаІЛ а¶Ша¶Яථඌа¶Яа¶Њ а¶Ха¶њ а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Ыа¶ња¶≤ – ටඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ЫаІЗථ а¶ЄаІИаІЯබ а¶Жа¶≤аІА а¶Жයඪඌථ, а¶Йථඌа¶∞ а¶ђа¶З ඕගа¶Ха¶Њ а¶ЄаІЗа¶З а¶Еа¶Вපа¶Яа¶Њ а¶Ыඌ඙ඌа¶ЗටаІЗа¶Ыа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗ
вА¶
а¶≤ග඙ග ඐග඙а¶∞аІНа¶ѓаІЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ
…а¶Па¶Цථ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶єа¶∞а¶Ђ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶њ а¶®а¶Ња•§ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථа¶З а¶УආаІЗ а¶®а¶Ња•§ ටඐаІБ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗ а¶Па¶З ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤, а¶ХගථаІНටаІБ ටඌ а¶Ха¶Цථа¶З а¶ХаІЛථ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗ а¶∞аІВ඙ ථаІЗаІЯа¶®а¶ња•§ а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞а¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Ха¶∞аІНටඌ а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІЗа¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶З а¶ѓаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ටඌ-а¶У ථаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶Хඕඌа¶Яа¶Њ а¶ђа¶≤а¶ђ а¶®а¶Ња•§ а¶≤ග඙ග а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶ЙබаІНа¶≠а¶Я ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐථඌа¶∞ а¶Хඕඌа¶З ටаІБа¶≤а¶ђа•§
ටаІОа¶Ха¶Ња¶≤аІАථ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ а¶Еа¶Вප а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶≤ග඙ග ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඪගථаІНа¶ІаІА а¶Па¶ђа¶В а¶Йа¶∞аІНබаІБ බаІБа¶З-а¶З а¶≤а¶ња¶Цගට යට а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶ђа¶Њ а¶Ђа¶Ња¶∞а¶ЄаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗа•§ ඙පටаІБа¶У а¶≤а¶ња¶Цගට යට а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗа•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ ඙ඌа¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶ђаІЗ а¶ХаІЛථ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶≤ග඙ග а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ පගа¶Ца¶∞а¶Њ а¶ЧаІБа¶∞аІБа¶ЃаІБа¶ЦаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ ඙ඌа¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶ђаІА а¶≤а¶ња¶ЦටаІЗථ а¶Па¶ђа¶В а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ а¶Ђа¶Ња¶∞а¶ЄаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗа•§ а¶Па¶Х а¶ХඕඌаІЯ, ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђ а¶Х’а¶Яа¶њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඁඌටаІНа¶∞ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶ђа¶В ටඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶∞а¶ђаІАа•§ а¶Єа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ටа¶Цථ а¶Ыа¶ња¶≤-а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶єа¶∞а¶Ђ а¶Па¶ђа¶В ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶Ђа•§ а¶Па¶З а¶єа¶∞а¶ЂаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ха¶Цථа¶У ථගа¶∞аІНබаІЗපගට а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ а¶П ථගаІЯаІЗ පаІБа¶ІаІБ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶∞ а¶ЄаІВටаІНа¶∞඙ඌට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§
а¶Па¶З а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЄаІВටаІНа¶∞඙ඌට а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Ѓа¶∞а¶єаІБа¶Ѓ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞а¶єа¶Ѓа¶Ња¶®а•§ ටගථග ඥඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶ђа¶Ња¶ЄаІА а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶ХаІЛථ а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ ටඌа¶Ба¶∞ а¶≠а¶Ња¶≤ බа¶Ца¶≤ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶єаІЗථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටග а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≤а¶ња¶Ца¶ђа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථ ටа¶Цථ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ පගа¶ХаІНඣඌඁථаІНටаІНа¶∞аІА а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ аІІаІѓаІ™аІЃ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЬаІБථ а¶Ха¶њ а¶ЬаІБа¶≤а¶Ња¶З а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ ටගථග ඥඌа¶Ха¶ЊаІЯ а¶Жа¶ЄаІЗථ а¶Па¶ђа¶В ඥඌа¶Ха¶ЊаІЯ ටඌа¶Ба¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБ а¶Ѓа¶Уа¶≤а¶Њ а¶Ѓа¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶ЊаІЯ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Па¶Хබගථ ටගථග а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶ђаІИආа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶≤аІЛа¶ЪථඌаІЯ а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞а¶Њ а¶Й඙ඪаІНඕගට а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶єа¶∞аІНටаІЗථ: а¶Ђа¶Ьа¶≤аІЗ а¶Жයඁබ а¶Ха¶∞а¶ња¶Ѓ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІА-ටගථග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Єа¶Ъа¶ња¶ђ, а¶Уඪඁඌථ а¶Ча¶£аІА-ටගථග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඥඌа¶Ха¶Њ а¶Яа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶ЯаІНа¶∞аІЗථගа¶В а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶Ј, ඥඌа¶Ха¶Њ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х а¶ЖඐබаІБа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶Ьа¶Ња¶Х, а¶ЄаІИаІЯබ а¶Єа¶Ња¶ЬаІНа¶Ьඌබ а¶єаІЛа¶Єа¶Ња¶Зථ, а¶Ха¶ђа¶њ а¶Ьа¶ЄаІАа¶Ѓа¶ЙබаІНвАМබаІАථ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶Ѓа¶ња•§ а¶Єа¶≠а¶ЊаІЯ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ ටඕаІНа¶ѓ බ඀ටа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Ха¶∞аІНටඌ а¶ЃаІЛа¶єа¶Ња¶ЃаІНඁබ а¶єаІЛа¶ЄаІЗථ а¶Й඙ඪаІНඕගට а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Ъа¶ЯаІНа¶Яа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶єаІБа¶∞аІБа¶ЂаІБа¶≤ а¶ХаІЛа¶∞а¶Жථ ඪඁගටගа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌටඌ а¶Па¶Х а¶ђаІГබаІНа¶І а¶ЃаІМа¶≤а¶≠аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђа¶У а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Й඙ඪаІНඕගට а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ьඌථටඌඁ ථඌ, а¶ХаІЗථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶°а¶Ња¶Ха¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶∞ а¶ЄаІВටаІНа¶∞඙ඌටаІЗ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶Єа¶≠а¶Њ а¶ЖයඐඌථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ ටගථග а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, ‘඙аІНа¶∞а¶ЪаІБа¶∞ а¶∞а¶ХаІНට඙ඌටаІЗа¶∞ ඐගථගඁаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶њ, а¶Па¶З ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Ъа¶њаІЯаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶Па¶ђа¶В ඐග඙බ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІНටඐаІНа¶ѓа•§ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶≠а¶Ња¶∞ටඐа¶∞аІНа¶Ј ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ђаІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ыа¶њ, а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථа¶ХаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Є а¶Ха¶∞а¶Ња•§ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ ටඌа¶З а¶ЄаІЗබගа¶ХаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ ඙аІЬа¶ђаІЗ ථඌ, ටඌබаІЗа¶∞ බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ ඙аІЬа¶ђаІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞а•§ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗ а¶ЄаІИථаІНа¶ѓ ථගаІЯаІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ බа¶Ца¶≤ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ ටඌ ථаІЯ, ටඌа¶∞а¶Њ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග, පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Па¶ђа¶В а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶ђа¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථа¶ХаІЗ а¶Жථඐඌа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа•§ а¶Па¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ ටඌබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа•§ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶У а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња•§ а¶Па¶З а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶ЕථаІБ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප ඃට а¶Єа¶єа¶ЬаІЗ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐ඙а¶∞, а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Ха¶ња¶ЫаІБටаІЗ ටඌ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ ථаІЯа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶≠ගථаІНථ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶єа¶≤аІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Хඕඌ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶Еа¶≠ගථаІНථ, а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටග ඃබග а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ, ටඌයа¶≤аІЗ а¶Еටග а¶Єа¶єа¶ЬаІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථа¶ХаІЗ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ха¶ђа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶≤а¶ња¶Цථ ඙බаІН඲ටගа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶Ша¶Яа¶Ња¶ђа•§ а¶Па¶З ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ ආගа¶Х ඁට а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ч ඐථаІНа¶І а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЄаІЗа¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶∞аІНටථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За•§’
а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶ђа¶ХаІНටаІГටඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටаІБට а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶®а¶Ња•§ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶Еа¶Єа¶Ња¶∞ටඌ а¶Па¶ђа¶В а¶Еа¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐටඌ а¶Пට ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Я а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓаІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶З а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£ ඙а¶∞аІНඃථаІНට යටа¶≠а¶ЃаІНа¶ђ а¶єаІЯаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЪаІБ඙ а¶Ха¶∞аІЗ ඕඌа¶ХටаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶Ъа¶ЯаІНа¶Яа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶єаІБа¶∞аІБа¶ЂаІБа¶≤ а¶ХаІЛа¶∞а¶Жථ ඪඁගටගа¶∞ а¶ЃаІМа¶≤а¶≠аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђа¶ХаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶Й඙ඪаІНඕගට а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЃаІМа¶≤а¶≠аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶Ыඌ඙ඌ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඙ඌа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶Х ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ ඙аІЗප а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ ටගථග а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ а¶ѓаІЗ, ටගථග බаІАа¶∞аІНа¶Шබගථ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Па¶З ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯ а¶Па¶З ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х ඙ඌආа¶Х а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶ЃаІМа¶≤а¶≠аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ටඕаІНа¶ѓ ඙аІЗප а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ а¶ѓаІЗ, а¶Па¶Х а¶Єа¶ЃаІЯ ථඌа¶Ха¶њ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≤а¶ња¶Цගට а¶єа¶§а•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙аІБа¶∞ථаІЛ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඙аІБа¶Бඕග ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶≤а¶ња¶Цගට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Па¶З ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ѓа¶Цථ а¶Па¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ටа¶Цථ පයаІАබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶Єа¶≠а¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶П ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ѓа¶Њ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ටඌ а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙аІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ђаІЛа¶ЭඌථаІЛ а¶єа¶≤а•§ а¶Єа¶ђ а¶Хඕඌ පаІБථаІЗ පයаІАබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ ඁථаІНටඐаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ, ‘а¶≠ඌඣඌඐගබ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ХаІНටඐаІНа¶ѓ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, ‘а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Њ ඙аІГඕගඐаІАа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІНа¶ЫථаІНථ а¶Па¶ђа¶В а¶ІаІНඐථගඪа¶ЩаІНа¶Чට а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Ња•§ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶ІаІНඐථගа¶ХаІЗ а¶ЄаІБа¶ЄаІН඙ඣаІНа¶Яа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶П а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Њ ටаІНа¶∞аІБа¶Яග඙аІВа¶∞аІНа¶£ ථаІЯ, а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶Па¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථ а¶ѓаІБа¶ХаІНටග ථаІЗа¶За•§ බаІНඐගටаІАаІЯටа¶Г а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ІаІНඐථග а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶Ђа¶Ња¶∞а¶ЄаІА а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Њ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ඪටаІНа¶ѓ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Єа¶ВපаІЛ඲ථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶њ а¶ІаІНඐථගа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђа¶Ња¶ІаІНа¶ѓ а¶єаІЯаІЗ а¶Ђа¶Ња¶∞а¶ЄаІАටаІЗ ඙аІЗ, а¶ЪаІЗ а¶ЗටаІНඃඌබග а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶≤ග඙ගа¶∞ а¶ЙබаІНа¶≠ඌඐථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§
඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶Жа¶∞а¶ђаІАටаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ථඌ, а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯ ‘а¶ђа¶Ња¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ’а•§ а¶Па¶ЯаІБа¶ХаІБ а¶ђа¶≤аІЗ ටගථග а¶Ъа¶ЯаІНа¶Яа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЃаІМа¶≤а¶≠аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ ‘а¶єаІБа¶∞аІБа¶ЂаІБа¶≤ а¶ХаІЛа¶∞а¶Жථ’ ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ යඌටаІЗ ටаІБа¶≤аІЗ ථගа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£. а¶ЪаІЛа¶Ц а¶ђаІБа¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, ‘а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Єа¶ђ පඐаІНබ а¶≠аІБа¶≤ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶ХаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ‘а¶ЦаІЗ පගථ ටඌඪබаІАබ а¶Жа¶≤а¶ња¶Ђ а¶Па¶ђа¶В පගථ’ බගаІЯаІЗ-а¶Па¶Яа¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌටаІЗ а¶≤а¶ња¶Ца¶≤аІЗ බඌа¶БаІЬа¶ЊаІЯ ‘ඐගපаІНපඌප’а•§ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ‘ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є’ පඐаІНබаІЗа¶∞ ඐඌථඌථа¶Яа¶њ а¶Жа¶∞а¶ђаІАටаІЗ ටගථග а¶≠аІБа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ а¶®а¶ња•§’ а¶Ьථඌඐ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථ ටа¶Цථ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, ‘а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ха¶њ а¶Ха¶њ а¶Єа¶ВපаІЛ඲ථ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ, ටඌ-а¶Ха¶њ а¶Ж඙ථග а¶Ха¶∞аІЗ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗථ?’ පයаІАබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, ‘а¶≠ඌඣඌඐගබ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІНа¶∞аІБа¶Яа¶ња¶ЧаІБа¶≤аІЛ බаІЗа¶Ца¶њаІЯаІЗ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕථ а¶Ха¶∞а¶њ а¶®а¶Ња•§’ а¶П а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ха¶ђа¶њ а¶Ьа¶ЄаІАа¶Ѓа¶ЙබаІНබаІАථ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Йආа¶≤аІЗථ, ‘а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Хඐගටඌа¶∞ а¶ђа¶З а¶Ха¶≤а¶ХඌටඌаІЯ а¶ђаІЗප а¶Ъа¶≤аІЗ, а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶≤а¶ња¶Ца¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶З а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗබаІЗපаІЗ а¶Ъа¶≤а¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ ටඌа¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЫථаІНබа¶У ආගа¶Х а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§’
а¶П ථගаІЯаІЗ а¶ЄаІЗබගථ а¶Жа¶∞ ඐගපаІЗа¶Ј а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ХаІЛථ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶ња¶®а¶ња•§ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶Га¶Єа¶Ња¶∞පаІВථаІНඃටඌ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Па¶Яа¶Њ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථබගථа¶З а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐඌаІЯගට යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ථඌ-а¶Па¶Яа¶Њ а¶Ха¶≤аІН඙ථඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Ха¶Ња¶∞а¶У ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶Еа¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶Уඪඁඌථ а¶Ча¶£а¶њ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶∞аІЛඁඌථ а¶єа¶∞а¶ЂаІЗа¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶≤а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶П а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶Чටග а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ха¶ња¶ЫаІБබගථ ඙а¶∞ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ а¶Зටගයඌඪ а¶Єа¶ЃаІНа¶ЃаІЗа¶≤ථаІЗ а¶П а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЙටаІНඕඌ඙ගට а¶єаІЯа•§ а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІНа¶ЃаІЗа¶≤ථаІЗ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථ а¶Єа¶≠ඌ඙ටග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට, а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Жа¶≤аІЗа¶Ѓ а¶Па¶ђа¶В а¶™а¶£аІНධගට а¶єа¶ѓа¶∞ට а¶ЄаІИаІЯබ а¶ЄаІБа¶≤а¶ЊаІЯඁඌථ ථඌබа¶≠аІА ඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶Еටගඕග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶Еටගඕග а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ ටගථග а¶ѓаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶≠а¶Ња¶Ја¶£ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, ටඌටаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ж඙ටаІНටගа¶Ха¶∞ а¶Хඕඌ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටගථග а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶єа¶∞а¶ЂаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶ХаІНටඐаІНа¶ѓ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ටගථග а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ѓаІЗ, ‘а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶єа¶∞а¶ЂаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ යගථаІНබаІБබаІЗа¶∞ බаІЗа¶ђаІАа¶∞ ථඌඁаІЗа¶∞ а¶ѓаІЛа¶Ч а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶Па¶З а¶єа¶∞а¶Ђ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶ЮаІНа¶ЫථаІАаІЯа•§’ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤ а¶ђаІЗа¶≤а¶Њ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Ьථ а¶єа¶≤аІЗ а¶ЙබаІНа¶ђаІЛ඲ථаІА а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗ ටගථග а¶Па¶З а¶ђа¶ХаІНටඐаІНа¶ѓ а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗа¶®а•§ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ පයаІАබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶Єа¶Ња¶Вඐඌබගа¶ХබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ථඌබа¶≠аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶ђа¶ХаІНටඐаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඐඌබ а¶Ьа¶Ња¶®а¶Ња¶®а•§ а¶Зටගඁ඲аІНа¶ѓаІЗ ථඌබа¶≠аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶ђа¶ХаІНටඐаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ ඥඌа¶Ха¶Њ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞ а¶Ѓа¶єа¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞ а¶єаІЯа•§ а¶ђа¶ња¶ХаІЗа¶≤ ටගථа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Єа¶ЃаІНа¶ЃаІЗа¶≤ථаІЗа¶∞ බаІНඐගටаІАаІЯ а¶Еа¶Іа¶ња¶ђаІЗපථаІЗ ථඌබа¶≠аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶Ча¶ЊаІЬа¶њ а¶ѓа¶Цථ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Ьථ а¶єа¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ ටа¶Цථ а¶Па¶Хබа¶≤ а¶ЫඌටаІНа¶∞ а¶Ча¶ЊаІЬа¶њ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗ а¶Па¶ђа¶В ථඌබа¶≠аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђа¶ХаІЗ а¶Ча¶ЊаІЬа¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЯаІЗථаІЗ-а¶єа¶ња¶Ба¶ЪаІЬаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЯගටаІЗ ථඌඁගаІЯаІЗ а¶ЖථаІЗа•§ а¶ЫඌටаІНа¶∞බаІЗа¶∞ а¶Ъඌ඙аІЗ ථඌබа¶≠аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђа¶ХаІНටඐаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶Ња¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶Ха¶ђа¶њ а¶Ьа¶ЄаІАа¶Ѓа¶ЙබаІНබаІАථаІЗа¶∞ а¶ЂаІБа¶≤а¶ђа¶ЊаІЬа¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶ЊаІЯ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶Жа¶ЄаІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ ටаІОа¶Ха¶Ња¶≤аІАථ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶Яа¶∞ а¶Ѓа¶ѓа¶єа¶Ња¶∞аІБа¶≤ а¶єа¶Х а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х а¶ЖඐබаІБа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶Ьа¶Ња¶Х а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х а¶Єа¶Ђа¶ња¶Йа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶Жа¶Ѓа¶ња¶У а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶ЄаІБа¶≤а¶ЊаІЯඁඌථ ථඌබа¶≠аІАа¶∞ а¶Еа¶Єа¶ЃаІНඁඌථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІЗа¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶Яа¶∞ а¶Ѓа¶ѓа¶єа¶Ња¶∞аІБа¶≤ а¶єа¶Ха¶ХаІЗ බඌаІЯаІА а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Ша¶Яථඌа¶Яа¶њ а¶Па¶ЦඌථаІЗа¶З පаІЗа¶Ј а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶Йа¶Ъගට а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ පаІЗа¶Ј а¶єа¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶∞а¶Ња¶ЪаІА ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶ВපаІЛ඲ථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐ බගаІЯаІЗ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ පයаІАබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙ටаІНа¶∞ බаІЗа¶®а•§ а¶Па¶З ඙ටаІНа¶∞а¶Яа¶њ а¶Ха¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓаІЗථ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ ‘а¶ЖථථаІНබඐඌа¶Ьа¶Ња¶∞’ ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶ЊаІЯ а¶Ыඌ඙ඌ а¶єаІЯ а¶Па¶ђа¶В ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙ඌබа¶ХаІАаІЯ а¶ЄаІНටඁаІНа¶≠аІЗ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ ටа¶Цථ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ ‘පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Й඙බаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶Ња¶ЙථаІНа¶Єа¶ња¶≤’ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ха¶Ња¶ЙථаІНа¶Єа¶ња¶≤ а¶Чආථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЄаІЗ а¶ђа¶Ыа¶∞а¶З а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐටа¶Г ථа¶≠аІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ а¶Йа¶ХаІНට а¶Ха¶Ња¶ЙථаІНа¶Єа¶ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ђаІИආа¶Х ඥඌа¶Ха¶ЊаІЯ а¶ђа¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ђа¶ња¶ХаІЗа¶≤ а¶ђаІЗа¶≤а¶Њ ඥඌа¶Ха¶Њ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ ටаІОа¶Ха¶Ња¶≤аІАථ а¶Й඙ඌа¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ а¶°а¶Г а¶ЄаІИаІЯබ а¶ЃаІЛаІЯа¶Ња¶ЬаІНа¶ЬаІЗа¶Ѓ а¶єаІЛа¶ЄаІЗථаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶ЧаІГа¶єаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Єа¶Ва¶ђа¶∞аІН඲ථඌ а¶Єа¶≠а¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Йа¶ХаІНට а¶Єа¶Ва¶ђа¶∞аІН඲ථඌ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ ටаІОа¶Ха¶Ња¶≤аІАථ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Й඙බаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶°а¶Г а¶Ѓа¶Ња¶єа¶ЃаІБබ යඌඪඌථ а¶°а¶Г පයаІАබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђа¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ХаІНඣග඙аІНට а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗථ а¶Па¶ђа¶В ටඌа¶Ба¶∞ පаІЗа¶∞а¶УаІЯඌථаІАа¶∞ а¶Ха¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗ඙аІЗ а¶Іа¶∞аІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ‘බаІЗපබаІНа¶∞аІЛа¶єаІА’ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Жа¶ЦаІНа¶ѓа¶ЊаІЯගට а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ‘а¶ЖථථаІНබඐඌа¶Ьа¶Ња¶∞’ ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶ЊаІЯ а¶Єа¶Вඐඌබ ඙аІНа¶∞а¶ХඌපаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ පයаІАබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђа¶ХаІЗ බаІЛа¶ЈаІА а¶Єа¶Ња¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНට а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶Па¶З а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§
а¶Ъа¶ЯаІНа¶Яа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶єаІБа¶∞аІБа¶ЂаІБа¶≤ а¶ХаІЛа¶∞а¶Жථ а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶ња¶∞ а¶ЃаІМа¶≤а¶≠аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ ථඌඁ а¶Па¶Цථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙аІЬа¶ЫаІЗ, ටඌа¶Ба¶∞ ථඌඁ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЃаІМа¶≤а¶≠аІА а¶ЬаІБа¶≤а¶Ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞а•§ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶≠ඌටඌ බаІЗаІЯа¶Њ යටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Ха¶Ња¶≤аІАථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶ђа¶∞ඌබаІНබ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶З ඙а¶∞а¶ња¶Ха¶≤аІН඙ථඌ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ђаІНа¶ѓа¶∞аІНඕටඌаІЯ ඙а¶∞аІНඃඐඪගට а¶єаІЯа•§ а¶Ьථඪඌ඲ඌа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЃаІВа¶∞аІНа¶Цටඌ а¶Па¶ђа¶В а¶ЧаІЛа¶БаІЯа¶Ња¶∞аІНටаІБа¶Ѓа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶Йа¶Ъගට а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ХаІЗа¶Й ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕථ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ ථඌ, ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථ ඁථаІНටаІНа¶∞аІА ටඌа¶ХаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶ђа¶ња¶ђаІГටග බаІЗа¶®а¶®а¶ња•§ පаІЗа¶Ј ඙а¶∞аІНඃථаІНට බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶ѓаІЗ, පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ ඁථаІНටаІНа¶∞а¶£а¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ බඌаІЯගටаІНа¶ђ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථ а¶Еа¶ђаІНඃඌයටග ඙аІЗаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Па¶ђа¶В ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ටඕаІНа¶ѓ ඁථаІНටаІНа¶∞а¶£а¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ බඌаІЯගටаІНа¶ђ බаІЗаІЯа¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶Па¶З а¶Е඙а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ ඐගපаІЗа¶Ја¶≠а¶Ња¶ђаІЗ බඌථඌ а¶ђа¶Ња¶Б඲ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ ටඐаІЗ а¶Ха¶ђа¶њ а¶ЧаІЛа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ЃаІЛа¶ЄаІНට඀ඌ ටඌа¶∞ ‘ථа¶Уа¶ђа¶Ња¶єа¶Ња¶∞’ ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶ЊаІЯ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶ђа¶Ња¶єа¶ња¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ‘а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Њ а¶Єа¶Ха¶≤ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЬථථаІА’ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞ඐථаІНа¶І ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞ටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа¶®а•§ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞ඐථаІНа¶Іа¶У а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ а¶ЧаІЛа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ЃаІЛа¶ЄаІНට඀ඌ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗථ ථග, а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗа¶∞ а¶ЧаІБа¶£а¶Чඌථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඁඌටаІНа¶∞а•§
а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≤а¶ња¶Ца¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶Ха¶≤аІН඙ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ පаІБа¶∞аІБටаІЗа¶З а¶ђаІНа¶ѓа¶∞аІНඕටඌаІЯ ඙а¶∞аІНඃඐඪගට а¶єаІЯа•§ а¶П ථගаІЯаІЗ ඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЗа¶Й а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶ђа¶Ња¶ЪаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶®а¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Цථа¶У а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶≤а¶Ња¶ЮаІНа¶Ыගට а¶Па¶ђа¶В а¶Е඙ඁඌථ а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ХаІЗа¶Й а¶ХаІЗа¶Й ඁගඕаІНа¶ѓа¶Њ а¶ђа¶≤аІЗ ඕඌа¶ХаІЗථ а¶ѓаІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶њ ථඌа¶Ха¶њ а¶Па¶Ха¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕа¶Х а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඪඌයගටаІНа¶ѓа¶Ха¶∞аІНа¶Ѓ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶З а¶ЙථаІНа¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІБа¶ЄаІН඙ඣаІНа¶Яа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Еа¶≠а¶ња¶≠а¶Ња¶Ја¶£аІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶З а¶ЬඌථаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Еඕඐඌ а¶ХаІЛථ а¶Йа¶ХаІНටග ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶П ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ХаІЗа¶Й ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£ а¶Й඙ඪаІНඕගට а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ ථග а¶ѓаІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ බаІБа¶∞аІНа¶ђаІГටаІНටаІЗа¶∞ а¶ЪඌටаІБа¶∞аІАа¶∞ а¶Еа¶≠а¶Ња¶ђ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В, а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞а¶Њ බаІБа¶∞аІНа¶ђаІГටаІНට ටඌа¶∞а¶Њ ඁගඕаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ха¶∞аІЗ ඪටаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶ЖаІЬа¶Ња¶≤ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඪටаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶ЖаІЬа¶Ња¶≤ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶З а¶®а¶Ња•§ а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶ХаІЛථ а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටаІЗ ඁගඕаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІЗඪඌටග а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ха¶∞а¶ња¶®а¶ња•§ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ ථගа¶∞аІНа¶≠аІЗа¶Ьа¶Ња¶≤ ඁගඕаІНа¶ѓа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞аІА ටඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞а¶ЧаІНа¶∞а¶ЄаІНටටඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ьඌටගа¶∞ а¶Жа¶Ь а¶Еа¶Єа¶єа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНа¶•а¶Ња•§ ඪටаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶Па¶З а¶Еа¶Єа¶єа¶ЊаІЯ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ බаІВа¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђа•§
඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ а¶ЄаІВටаІНа¶∞඙ඌටаІЗ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ч ථගаІЯаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶ња¶ђаІГටග ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටඌа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඐගපаІЗа¶Ј а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶Ча¶Њ а¶ЦඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ђаІГа¶§а¶ња•§ ‘඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ а¶За¶Єа¶≤а¶Ња¶ЃаІА а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞ а¶єа¶ђаІЗ’ а¶Па¶З а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Њ-පаІБථаІЗ а¶Жа¶Ча¶Њ а¶Цඌථ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ѓаІЗ а¶За¶Єа¶≤а¶Ња¶Ѓа¶ња¶Х а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ а¶За¶Єа¶≤а¶Ња¶ЃаІА а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Жа¶∞а¶ђаІАа•§ а¶Жа¶Ча¶Њ а¶ЦඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ђаІГටග ටа¶Цථ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶°а¶Г පයаІАබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶єа¶У а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Яа¶Њ а¶ХаІЛථ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗ а¶∞аІВ඙ඌථаІНටа¶∞ගට а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ а¶Жа¶∞а¶ђаІАа¶∞ ඪ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶П а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶ђа¶ња¶ђаІГටගа¶∞ а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞ටගඐඌබа¶У ටа¶Цථ а¶ХаІЗа¶Й а¶Ха¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗ а¶Іа¶∞аІЗ ථගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤, а¶Па¶Яа¶Њ ථаІЗа¶єа¶ЊаІЯаІЗටа¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ-а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞а¶Ѓа•§ а¶П ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞а¶Њ ථගа¶∞а¶∞аІНඕа¶Ха•§
а¶≤ග඙ග ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶ѓа¶Цථ а¶ХаІЛථа¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗа¶З а¶ЧаІГа¶єаІАට а¶єа¶≤ ථඌ а¶Па¶ђа¶В ‘а¶Еа¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Њ’ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ђа¶∞аІНа¶Ьගට а¶єа¶≤ ටа¶Цථ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඌබаІЗපගа¶Х а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Њ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Ѓа¶Уа¶≤ඌථඌ а¶Жа¶Ха¶∞а¶Ѓ а¶Ца¶Ња¶Б-а¶ХаІЗ а¶Єа¶≠ඌ඙ටග а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Њ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ѓа¶ња¶Яа¶њ а¶Чආගට а¶єаІЯа•§ а¶Па¶З а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ѓа¶ња¶ЯගටаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ-а¶Еа¶ІаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶Ј а¶За¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶єаІАа¶Ѓ а¶Ца¶Ња¶Б, а¶Жа¶ђаІБа¶≤ යඌඪථඌට, а¶Уඪඁඌථ а¶Ча¶£а¶ња•§ ඃබаІНබаІБа¶∞ ඁථаІЗ ඙аІЬаІЗ, а¶°а¶Г පයаІАබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶єа¶ХаІЗ а¶Па¶З а¶Ха¶Ѓа¶ња¶ЯගටаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ ඪබඪаІНඃබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඁටබаІНа¶ђаІИ඲ටඌ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶єа¶УаІЯа¶ЊаІЯ ටගථග а¶Па¶З а¶Ха¶Ѓа¶ња¶ЯගටаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗථ а¶®а¶ња•§ а¶Па¶З а¶Ха¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶∞ а¶∞ග඙аІЛа¶∞аІНа¶Я а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶Ха¶∞ а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ ඁථаІНටаІНа¶∞а¶£а¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶За¶≤ඐථаІНබаІА а¶єаІЯаІЗ පаІЗа¶Ј ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶єа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶ѓаІЗ, а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶У а¶ХаІЗа¶Й а¶Па¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶ХаІНඣ඙ඌටග ථаІЯа•§ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶≤ග඙ගа¶Ха¶∞а¶£ ඙аІНа¶∞ඕඌ а¶ѓаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗ ටඌ а¶Ьථඪඌ඲ඌа¶∞а¶£ а¶Єа¶єа¶ЬаІЗа¶З ඁඌථаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶ЫаІЗ, ටඌа¶З ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ХаІЗа¶Й а¶≠ඌඐටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯа¶®а¶ња•§ а¶ЕථаІЗа¶Х ඙а¶∞аІЗ, а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶Па¶Ха¶Ња¶°аІЗа¶ЃаІА ඐඌථඌථ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Ња¶°аІЗа¶Ѓа¶ња¶Х а¶Па¶ХаІНа¶Єа¶Ња¶∞а¶Єа¶Ња¶За¶Ь а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤, а¶ХගථаІНටаІБ ටඌ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶Ха¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ ටඌа¶∞а¶Њ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶®а¶ња•§
а¶Хටа¶Ха¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶єа¶Ња¶ЄаІНа¶ѓа¶Ха¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ ඙а¶∞аІНඃඐඪගට а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Хඕඌ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶Па¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ѓа¶∞а¶єаІБа¶Ѓ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ЄаІНටගඪаІНа¶Х඙аІНа¶∞а¶ЄаІВට а¶Па¶Ђа¶Яа¶њ පගපаІБ а¶Па¶ђа¶В а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ЄаІНටගඪаІНа¶ХаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞а¶ђа¶ЄаІНටаІБ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Хගථඌ ටඌ ථගаІЯаІЗ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ВපаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ බаІНඐගටаІАаІЯටа¶Г а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථаІЗа¶∞ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐථඌаІЯ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЃаІМථ а¶Ыа¶ња¶≤-඙аІНа¶∞а¶ХඌපаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕථа¶У а¶Ха¶∞аІЗථග, а¶ђа¶ња¶∞аІЛ඲ගටඌа¶У а¶Ха¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ ටගථග а¶Па¶Ха¶Њ а¶Па¶Ха¶Њ а¶П ථගаІЯаІЗ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶≤а¶ХаІНа¶Ј-а¶Эа¶ХаІНа¶Ј а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ХаІЛථа¶∞аІВ඙ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶Ха¶∞ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ ථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Єа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓ а¶єа¶®а¶®а¶ња•§ а¶П а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථа¶Яа¶њ а¶Ъа¶Ња¶≤аІБ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Ьථ а¶Еа¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤аІАа¶ХаІЗ ටගථග ථගаІЯаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶ХගථаІНටаІБ ටඌа¶∞а¶Њ а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඙ගа¶ЫථаІЗ а¶ХаІЛථ а¶ЙබаІНа¶ѓа¶Ѓ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶®а¶ња•§ ඃඌබаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ටඌа¶∞а¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ: а¶Ѓа¶Уа¶≤ඌථඌ а¶ЖඐබаІБа¶∞ а¶∞යඁඌථ а¶ђаІЗа¶ЦаІБබ, а¶Ђа¶Ьа¶≤аІЗ а¶Жයඁබ а¶Ха¶∞а¶ња¶Ѓ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІА а¶Па¶ђа¶В а¶°а¶Г а¶Жථබඌа¶≤а¶ња¶ђ පඌබඌථаІАа•§ а¶Па¶∞а¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶ђаІИආа¶ХаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤ගට යටаІЗථ, а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶≠ඌටඌ ඙аІЗටаІЗථ а¶Па¶ђа¶В а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІА ඙аІЯа¶Єа¶ЊаІЯ а¶Ъа¶Њ ඙ඌථ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶П а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Уа¶≤ඌථඌ а¶ђаІЗа¶ЦаІБබ а¶ЕථаІЗа¶Х ඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Па¶Хබගථ а¶Ча¶≤аІН඙ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ටගථග а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, ‘බаІЗа¶ЦаІБථ, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ьඌථටඌඁ а¶ѓаІЗ а¶Па¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶єа¶ђаІЗ ථඌ, ටඐаІБ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶≤а¶Ња¶≠аІЗа¶∞ ඐගථගඁаІЯаІЗ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶∞ а¶∞යඁඌථаІЗа¶∞ а¶Ца¶Ња¶Ѓа¶ЦаІЗаІЯа¶Ња¶≤аІАටаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ч බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§’
а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ ඐගපаІНа¶ђаІЯа¶Ха¶∞а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶ЬаІАа¶ђ а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≤ග඙ගа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථа¶У а¶ЖථථаІНබගටа¶∞аІВ඙аІЗ а¶Єа¶∞аІНа¶ђа¶Ьථа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶єаІНа¶ѓа•§ ටඌа¶З а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞ටගඐථаІНа¶Іа¶Хටඌа¶З а¶Па¶З а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶У а¶≤ග඙ගа¶∞ а¶Еа¶ЧаІНа¶∞ඃඌටаІНа¶∞а¶Ња¶ХаІЗ а¶∞аІБබаІНа¶І а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ а¶≤ග඙ගа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ха¶≤аІН඙ථඌ а¶єа¶Ња¶ЄаІНа¶ѓа¶Ха¶∞а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶єа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£ බගටаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ аІІаІѓаІЂаІ® а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЬඌටаІАаІЯ а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ца¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶Ша¶Яа¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЬඌටаІАаІЯ а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ ඙аІНа¶∞ටගඐඌබ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶ђа¶В а¶ЕපаІБа¶≠ පа¶ХаІНටග а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඐඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶Єа¶Ва¶Ха¶Яඌ඙ථаІНථ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶Ьඌටගа¶∞ а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єаІЯ а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌа¶∞ ඃඌටаІНа¶∞ඌ඙ඕа¶ХаІЗ а¶ЙථаІНа¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞аІЗа•§
а¶ђа¶Ња¶Ыа¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞
Latest posts by а¶ђа¶Ња¶Ыа¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞ (see all)
- а¶ЄаІИаІЯබ а¶Жа¶≤аІА а¶Жයඪඌථ: а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ – вАЬа¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶єа¶∞а¶ЂаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≤а¶ња¶Ца¶ђа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐвАЭ а¶®а¶њаІЯа¶Њ - а¶ЂаІЗа¶ђаІНа¶∞аІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ 21, 2025
- ටа¶∞аІНа¶Х: а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ-а¶≤аІЗа¶Ца¶ХබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඪඌයගටаІНа¶ѓ – а¶ђаІБබаІН඲බаІЗа¶ђ а¶ђа¶ЄаІБ а¶У а¶Жа¶ђаІБа¶≤ ඁථඪаІБа¶∞ а¶Жа¶єа¶ЃаІЗබ (аІІаІѓаІ™аІ®) - а¶ЬඌථаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ 23, 2025
- а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞඙ටගа¶∞ а¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶З඙ග а¶Хථа¶≠а¶Ња¶∞а¶ЄаІЗපථ (аІ®аІ¶аІІаІ®) – ඙ඌа¶∞аІНа¶Я аІ®: а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶єа¶≤аІЛ а¶ЬаІЗа¶Па¶Єа¶°а¶њ, а¶Жа¶∞ а¶Уа¶З ආඌа¶ХаІБа¶∞ а¶єа¶≤аІЛ а¶Єа¶ња¶™а¶ња¶ђа¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Жа¶УаІЯа¶Ња¶ЃаІА а¶≤аІАа¶Ч а¶¶а¶ња¶ђа•§ - а¶°а¶ња¶ЄаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ 24, 2024