вАШа¶Ъа¶ња¶∞බගථ ඙аІБа¶Ја¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶Х а¶Еа¶Ъගථ ඙ඌа¶Ца¶њвАЩ

а¶Єа¶Ња¶ЧаІБ඀ටඌ පඌа¶∞а¶ЃаІАථ ටඌථගаІЯа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЕථаІЗа¶Хබගථ а¶Іа¶За¶∞а¶Њ а¶≠ඌඐටаІЗа¶Ыа¶њ а¶Па¶ХඪඌඕаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶З а¶≤а¶ња¶Ца¶ђаІЛа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶За¶≤а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶ња¶∞ а¶ЪаІЛа¶ЯаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶єа¶ЗටаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶ЦථаІЛ а¶ѓаІЗ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ха¶∞аІНඁආ а¶єа¶ЗаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶њ යආඌаІО, ටඌ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶®а¶Ња•§ ටඐаІБ පаІЗа¶Ј ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ђа¶За¶Яа¶Њ а¶ЬථаІНа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ ථඌඁ вАШа¶ЖථඐඌаІЬа¶њвАЩа•§ ථඌඁа¶Яа¶Њ ටඌථගаІЯа¶Ња¶∞ බаІЗаІЯа¶Ња•§ පаІБථа¶≤аІЗа¶З а¶Уа¶З а¶Чඌථа¶Яа¶Њ ඁථаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ вАУ вАШа¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ІаІБаІЯа¶Њ а¶ЖථඐඌаІЬа¶њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њ а¶Жа¶ЩаІНа¶Чගථඌ බගаІЯа¶ЊвА¶вАЩа•§¬†
а¶ЕඐපаІНа¶ѓ ථඌඁа¶Ха¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඙ගа¶ЫථаІЗ а¶ђа¶ІаІБаІЯа¶Њ а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට බаІБа¶Га¶Ца¶ђаІЛа¶І ටаІЗඁථ а¶Ьа¶∞аІБа¶∞а¶њ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ЖථඐඌаІЬа¶ња¶З а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ – ඁඌථаІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ, а¶Еඕඐඌ а¶ѓа¶Њ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶∞ ටඌථගаІЯа¶Њ බаІБа¶За¶ЬථаІЗа¶З ඐගබаІЗප ඕඌа¶Ха¶њ а¶Жа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶Ха¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶ЭаІБа¶≤ථаІНට а¶≠а¶Ња¶ђ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶ХаІЛඕඌа¶У ආගа¶Х ඁටථ ඁගප а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗа¶За¶ЦඌථаІЗ ඕඌа¶Ха¶њ а¶ЄаІЗа¶За¶ЦඌථаІЗ а¶Ха¶ЦථаІЛа¶З ඙аІБа¶∞ඌ඙аІБа¶∞а¶њ ඕඌа¶ХටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶З а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞аІЗа¶∞а¶Ња¶У а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඁටථа¶З ඙а¶∞а¶ђа¶Ња¶ЄаІА, ටඌа¶З ඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Па¶З а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ ථඌඁа¶Ха¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞аІНඕа¶Хටඌ а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗа¶У а¶ЦаІБа¶Ба¶За¶Ьа¶Њ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ ටඐаІЗ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶ња¶ЪаІНа¶ЫගථаІНථටඌඐаІЛа¶ІаІЗа¶∞ а¶Хඕඌа¶З а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶Ыа¶њ а¶Па¶З а¶Ча¶≤аІН඙аІЗа•§ а¶єаІЯටаІЛ а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞а¶З а¶Па¶За¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶≤а¶Ња¶ЧаІЗ а¶ХаІЛථ ථඌ а¶ХаІЛථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ, а¶ЄаІНඐබаІЗප а¶ђа¶Њ ඐගබаІЗප а¶ђаІНඃ඙ඌа¶∞ а¶®а¶Ња•§
а¶ђа¶За¶Яа¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Еа¶Вප බගа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗа•§ а¶Жපඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ ‘පаІБබаІНа¶Іа¶ЄаІНа¶ђа¶∞’ ඕаІЗа¶ХаІЗ аІ®аІ¶аІІаІ™ а¶Па¶∞ а¶ђа¶За¶ЃаІЗа¶≤ඌටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶єа¶ђаІЗа•§
– а¶≤аІБථඌ а¶∞аІБපබаІАа•§ а¶ЃаІЗа¶≤а¶ђаІЛа¶∞аІНථ, а¶Еа¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶≤а¶њаІЯа¶Ња•§
_____________________________________________
а¶ЪаІЛа¶Ц ඙а¶∞аІНඃථаІНට ඙аІМа¶Ба¶Ыа¶ЊаІЯ ථඌ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶Єа¶њ…
а¶Жа¶∞ а¶Ха¶њ а¶ѓаІЗථ а¶ђа¶≤а¶Ыа¶ња¶≤? а¶Па¶Ха¶ЯаІБа¶Цඌථග а¶ЪаІЛа¶Ц а¶ЦаІБа¶≤аІЗа¶З ඐථаІНа¶І а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІЛ а¶ШаІБа¶Ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња•§ ථඌа¶Ха¶њ? а¶ЄаІНඐ඙аІНථ, а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Б ටඌа¶З а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ а¶Хඕඌа¶Яа¶Њ පаІЛථඌ а¶єа¶≤аІЛථඌටаІЛа•§ а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓа¶З а¶Жа¶Ѓа¶њ, а¶Еа¶∞аІНа¶ІаІЗа¶Х ඁඌථаІБа¶Ја•§ а¶Жа¶Ьа¶Ха¶Ња¶≤ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶За¶У ඙аІЬаІЗ පаІЗа¶Ј а¶Ха¶∞а¶њ ථඌ…а¶Жа¶Іа¶Ња¶Жа¶Іа¶њ а¶Ча¶≤аІН඙а¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ШаІБа¶∞඙ඌа¶Х а¶Ца¶ЊаІЯ ඁඌඕඌа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞, а¶ЃаІЗа¶ШаІЗа¶∞ ඁටаІЛа¶®а•§ ථඌа¶Ха¶њ а¶Ча¶Ња¶≠аІА? а¶Ха¶њ а¶ѓаІЗථ а¶Хඐගටඌа¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ? вАШа¶ХаІЛඕඌаІЯ а¶ѓаІЗථ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶ЫаІЗ а¶ђаІЗථаІБ, а¶ЃаІЗа¶ШаІЗа¶∞ ඁටථ а¶ЪаІЬа¶ЫаІЗ а¶ІаІЗථаІБ…вАЩ¬† а¶ІаІБටаІНටаІЛа¶∞а¶њ! а¶Па¶Яа¶Њ ටаІЛ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඐඌථඌа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Уа¶За¶Яа¶Њ ඁථаІЗ а¶єаІЯ පа¶ХаІНටගа¶∞ а¶Хඐගටඌ, а¶ХаІЗඁථ බаІБа¶Га¶ЦаІА බаІБа¶Га¶ЦаІА, පඌථаІНට а¶ХаІБаІЯඌපඌ а¶ЃаІЛаІЬඌථаІЛ… вАШа¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ЃаІЗа¶Ш…а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ЃаІЗа¶Ш…вАЩа•§[pullquote][AWD_comments][/pullquote]
а¶ПබаІЗа¶∞ а¶Ха¶њ а¶ХаІЛථබගථ а¶Ъа¶ња¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶Ъа¶ња¶≤аІНа¶≤а¶њ ඕඌඁඐаІЗ ථඌ? а¶Ха¶њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ьа¶Ха¶Ња¶≤? ඙аІНа¶∞а¶ЪථаІНа¶° පඐаІНබаІЗ а¶ЂаІЗа¶ЯаІЗ ථඌ ඙аІЬа¶≤аІЗ а¶ђаІБа¶Эа¶њ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђ а¶Ьඌථඌථ බаІЗаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ථඌ? ඃට а¶ЬаІЛа¶∞аІЗ ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶Ъа¶њаІОа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ, ටටа¶Яа¶Ња¶З а¶ђаІЗа¶Ба¶ЪаІЗ а¶Жа¶Ы! а¶≤аІНඃඌ඙а¶Я඙а¶Яа¶Њ а¶Еථ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶ШаІБа¶Ѓа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Па¶Цථ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ ඁථගа¶Яа¶∞аІЗа¶∞ ථаІАа¶≤ а¶Жа¶≤аІЛ ¬†а¶ХаІЗඁථ а¶Еටග඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІГට ඁථаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶Ња¶Я а¶ђа¶Ња¶Ба¶Іа¶Њ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞а•§ а¶Уа¶З а¶ХаІЛථඌа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶ђаІЬ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶ХаІЛථඌ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞а¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ѓаІБа¶Яа¶ХаІЗа¶Єа•§ а¶°а¶Ња¶≤а¶Њ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ ඙аІЬаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ බаІБа¶Зබගථ а¶Іа¶∞аІЗа•§ а¶≠ගටа¶∞аІЗ а¶Хඌ඙аІЬ-а¶ЪаІЛ඙аІЬ, а¶ђа¶З, а¶Ъа¶ња¶∞аІБа¶£аІА, а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІЗа¶∞а¶Њ, а¶≠а¶Ња¶Вටග ඙аІЯа¶Єа¶Њ а¶Єа¶ђ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗඁගපаІЗ а¶Єа¶∞а¶Ча¶∞а¶Ѓ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНа¶•а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶ЧаІЛа¶ЫඌටаІЗ а¶За¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ථඌ, а¶Ца¶Ња¶≤а¶њ а¶ШаІБа¶Ѓа¶Ња¶З а¶Жа¶Ѓа¶њ, а¶Жа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ьа¶Ња¶Ча¶ња•§
ඐඌඕа¶∞аІБа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЯаІНඃඌ඙а¶Яа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЂаІЛа¶Ба¶Яа¶Њ а¶ЂаІЛа¶Ба¶Яа¶Њ ඙ඌථග ඙аІЬа¶ЫаІЗа•§ පаІБථටаІЗ ඙ඌа¶За•§ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ХаІЗа¶Й а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ХථаІНආථඌа¶≤аІАа¶∞ а¶ЄаІАа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Ъа¶њаІОа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶≤аІЛ ඁථаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶Ха¶ња¶ЃаІНа¶≠аІБට а¶Па¶Х පඐаІНබаІЗ ඐඌටඌඪ а¶≠а¶Ња¶∞аІА а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ вАУ а¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶ђаІЗ а¶Па¶З පඐаІНබ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ХථаІНආ ථගа¶Га¶ЄаІГට? а¶ХаІЗа¶Й а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶ХаІЛථ а¶Жа¶≤ඌ඙ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ ථඌ, а¶єа¶Ња¶Єа¶ЫаІЗ ථඌ, а¶Пඁථа¶Ха¶њ а¶Чඌථа¶У පаІБථа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ පаІБа¶ІаІБ а¶Уа¶З ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£аІАа¶∞ а¶Жа¶∞аІНටථඌබаІЗа¶∞ ඁටථ а¶Ъа¶њаІОа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ඁගපаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌаІЯ а¶Ча¶ЊаІЬа¶њ а¶Ъа¶≤а¶Ња¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶єаІБප а¶єаІБප පඐаІНа¶¶а•§ පථගඐඌа¶∞ а¶∞ඌටаІЗ а¶ђаІЗаІЬа¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ඁඌථаІБа¶Ја•§ а¶ХаІЗа¶Й ථඌ а¶ХаІЗа¶Й а¶Єа¶ђа¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶З а¶ХаІЛඕඌа¶У ථඌ а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§
а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶У а¶ѓаІЗටඌඁ а¶Еа¶Ха¶≤аІНඃඌථаІНа¶°аІЗ вАУ а¶ґаІБа¶ХаІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ පථගඐඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶∞ඌටа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ඐගපаІЗа¶Ј а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶њ а¶Жа¶Ьа¶ђ а¶Жа¶Ьа¶ђ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶ѓаІЗ а¶Ха¶∞ටඌඁ! вАШ඙а¶∞а¶ња¶£аІАටඌвА٠බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ХаІЛථ а¶єа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ ථගа¶ЬаІЗа¶∞а¶Ња¶З а¶Пට а¶ђа¶Ха¶ђа¶Х а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Єа¶ња¶Я а¶ЦаІБа¶Ба¶Ьа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ѓаІЗ ඪඌඁථаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞а¶ња¶∞ а¶≤а¶Ња¶Зථ඲а¶∞а¶Њ ඁඌඕඌа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ѓаІЗ а¶ЬаІНඃථаІНට ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞аІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗа¶З а¶ЬаІЛаІЬа¶Њ බаІЗаІЯа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶ЦаІЗаІЯа¶Ња¶≤а¶З а¶Ха¶∞а¶ња¶®а¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ආගа¶Х ඪඌඁථаІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ ඁඌපа¶∞аІБа¶ЃаІЗа¶∞ ඁටථ බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶ХаІЛа¶Ба¶ХаІЬа¶Ња¶ЪаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ ඁඌඕඌаІЯ ඙඙а¶Ха¶∞аІНථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІЗа¶Я а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ඁඌඕඌаІЯ а¶Ча¶∞а¶Ѓ а¶≤аІЗа¶ЧаІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶ЫඌථඌඐаІЬа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶ѓа¶Цථ ටඌа¶Ха¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶єа¶Ња¶Єа¶ња¶∞ а¶ЪаІЛа¶ЯаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБටаІЗа¶З вАШа¶Єа¶∞а¶њвАЩ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶З ඪගථаІЗа¶Ѓа¶Ња¶∞а¶З පаІЗа¶ЈаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶∞ඌටаІНа¶Ѓа¶Х а¶ЄаІАථ а¶Ыа¶ња¶≤! ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ ථඌаІЯа¶ња¶Ха¶Њ а¶Єа¶Ња¶За¶Ђ а¶Жа¶≤аІА а¶Цඌථа¶ХаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶Ша¶∞ а¶Єа¶ђ බඌථ а¶ЦаІЯа¶∞ඌට а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶Зබගථа¶З а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ථඌаІЯа¶ХаІЗа¶∞ а¶ђа¶њаІЯаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶УබаІЗа¶∞ බаІБа¶З а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶За¶ЯаІЗа¶∞ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤ а¶ЙආаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ ටටබගථаІЗа•§ ඐගබаІНа¶ѓа¶Њ а¶ђа¶Ња¶≤ඌථаІЗа¶∞ а¶ђаІЛථ а¶Ьа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶З а¶Єа¶ЮаІНа¶ЬаІЯ බටаІНට ථඌаІЯа¶Ха¶ХаІЗ а¶ђа¶њаІЯаІЗа¶∞ ඙ගа¶БаІЬа¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЙආගаІЯаІЗ а¶ПථаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ බа¶≤а¶ња¶≤аІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ а¶ПටබගථаІЗа¶∞ ඪආගа¶Х а¶Зටගයඌඪ ඙аІЗප а¶Ха¶∞а¶≤ ටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶ЗටаІЗа¶З ථඌаІЯа¶Х ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ а¶ЂаІБа¶БඪටаІЗ а¶ЂаІБа¶БඪටаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶ЦඌථаІЗа¶∞ а¶За¶Ба¶ЯаІЗа¶∞ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶ЫаІБа¶ЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶ЖපаІЗ඙ඌපаІЗ а¶ЃаІБа¶ЧаІБа¶∞ ථඌ ඕඌа¶Ха¶ЊаІЯ а¶Яа¶ња¶Йа¶ђа¶УаІЯаІЗа¶≤ ථඌ а¶Ха¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ѓаІЗථ а¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶Яඌථ а¶ЃаІЗа¶∞аІЗ а¶Й඙аІЬаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶≤аІЛ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Ња¶З а¶Чබඌа¶∞ ඁටථ а¶Іа¶∞аІЗ ඪඁඌථаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ බаІЗаІЯа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶≤аІЛ а¶За¶ЯаІЗа¶∞ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤аІЗа•§ [youtube id=”vZAcpP2bBrY” align=”center”]а¶ђа¶њаІЯаІЗа¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ බඌа¶УаІЯඌටаІАа¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђ вАШа¶≠а¶Ња¶ЩаІНа¶ЧаІЛ පаІЗа¶Ца¶∞, а¶≠а¶Ња¶ЩаІНа¶ЧаІЛ පаІЗа¶Ца¶∞вАЩ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶Чට а¶ЙаІОа¶Єа¶Ња¶є බගаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ බаІЛටа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌаІЯ බඌа¶Бට а¶Ха¶њаІЬа¶Ѓа¶њаІЬ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗථ ථඌаІЯа¶ХаІЗа¶∞ а¶≠а¶ња¶≤аІЗථ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА а¶Ъа¶ХаІНа¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА а¶Жа¶∞ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Уа¶З඙ඌපаІЗ ඪ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞ ථඌаІЯа¶ња¶Ха¶Њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ටаІЛ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа¶За•§ ථඌаІЯа¶Х බаІЗаІЯа¶Ња¶≤ а¶ЂаІБа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ч ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Па¶З а¶ЕථථаІНට а¶ЧаІГයටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ча•§ බа¶∞аІНපа¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђ а¶ЙටаІНටаІЗа¶Ьගට, පаІЛа¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶єаІНа¶ђа¶≤а•§ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶ЦඌථаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ යඌඪටаІЗ යඌඪටаІЗ а¶ЪаІЗаІЯа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ а¶ђа¶≤а¶Ыа¶ња¶≤ вАШа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶Ѓа¶Ьඌබඌ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤ ඙а¶∞аІЗ а¶≠а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶ња¶Є, а¶ЧаІЗа¶Я බගаІЯа¶Њ а¶ђа¶Ња¶За¶∞ а¶є, а¶ЧаІЗа¶≤а¶Ча¶Њ а¶ХගථаІНටаІБ!вАЩ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶єаІЗа¶Ба¶Ъа¶Ха¶њ а¶ЙආаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶∞ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ а¶™а¶Ња¶®а¶ња•§
а¶ђаІЛа¶ЯඌථаІА ප඙ගа¶В а¶ЄаІЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а•§ а¶ЧаІНа¶≤аІЗථ а¶За¶°аІЗථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Х а¶ШථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠а•§ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞ටග පථගඐඌа¶∞ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ѓаІЗа¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЄаІБපගа¶∞ බаІЛа¶Хඌථа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ьඌථඌа¶≤а¶Ња¶∞ ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ђа¶ња¶≤а¶Яа¶Њ а¶Ха¶њ а¶Жа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ බаІЛа¶ХඌථаІЗа¶∞ ථඌඁа¶Яа¶Њ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶ЦаІЗаІЯа¶Ња¶≤а¶З а¶Ха¶∞ගථග, а¶Єа¶ђа¶Єа¶ЃаІЯ а¶ђа¶≤ටඌඁ вАШа¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЄаІБපග-ප඙вАЩа•§ බаІЛа¶ХඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ЪගථටаІЛ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа¶З а¶Ѓа¶ња¶ЄаІЛ а¶ЄаІНа¶ѓаІБ඙а¶Яа¶Њ а¶ЂаІНа¶∞а¶њ ඙аІЗаІЯаІЗ а¶ѓаІЗа¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ХඌආаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶ХаІЛථඌ а¶≠а¶Ња¶∞аІА а¶Еඕа¶Ъ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЯаІЗа¶ђа¶ња¶≤аІЗа¶∞ බаІБа¶З඙ඌපаІЗ ඁඌථඌථඪа¶З а¶ХඌආаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯа¶Ња¶∞а•§ а¶Ьඌථඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶У඙ඌපаІЗ බаІЛа¶ХඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶Жа¶∞аІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЪаІЗаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЯаІЗа¶ђа¶ња¶≤, а¶ЫаІЬඌථаІЛ а¶Ыа¶ња¶ЯඌථаІЛ බаІЛа¶Ха¶Ња¶®а•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ а¶Єа¶ђа¶Єа¶ЃаІЯ ථගටаІЛ а¶≠ඌටаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞аІЗ а¶ЄаІНඃඌඁථ а¶≠а¶Ња¶Ьа¶ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ЯаІЗа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶Ха¶њ а¶Єа¶Є а¶Жа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЯаІБථඌ-а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≠аІЛа¶Ха¶Ња¶°аІЛ а¶∞аІЛа¶≤ а¶Жа¶∞ а¶Ѓа¶ња¶ЄаІЛ а¶ЄаІНа¶ѓаІБа¶™а•§ а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶ХඌආаІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ђа¶ња¶≤аІЗа¶∞ බаІБа¶З඙ඌපаІЗ а¶Хට а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶Ха¶Ња¶Ыа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Уа¶∞ බаІБ-ටගථබගථаІЗа¶∞ ථඌ а¶ХඌඁඌථаІЛ а¶Ча¶Ња¶≤аІЗ යආඌаІО බаІБа¶За¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІБа¶ХаІНа¶ЈаІНа¶£ පඌබඌ ඐගථаІНබаІБ බаІЗа¶ЦටаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶ђа¶≤ටඌඁ вАУ вАШа¶Жа¶єа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ьа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶За¶Яа¶Њ а¶ђаІЬ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ђа¶њаІЯа¶Њ බගටаІЗ а¶єа¶ђаІЗвАЩа•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ ඙а¶∞а¶Ѓ а¶Ж඙аІНа¶≤аІБට а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЛ вАШබගඐග? බаІЗ ථඌ! а¶Уа¶З а¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ѓа¶≤а¶Њ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ња¶Ѓа¶Њ ඙аІЬа¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗвАЩа•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНඣථ а¶ЃаІЗаІЯаІЗ බаІЗа¶Цටඌඁ, а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ බаІЗа¶Цටඌඁ, а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ටඌඁ а¶Еඕඐඌ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶ђа¶≤ටඌඁ а¶®а¶Ња•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶∞аІЛа¶¶а•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІЯ ඙ඌа¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЛ а¶ЄаІЗа¶≤а¶ЂаІЛථаІЗ а¶ЧаІЗа¶За¶Ѓ а¶ЦаІЗа¶≤аІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටа¶Цථ а¶Ьඌථඌа¶≤а¶ЊаІЯ බаІЗа¶Цටඌඁ а¶єа¶Ња¶Єа¶њ-а¶ЦаІБපග а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ ඐගඣථаІНථ ඁඌථаІБа¶Ј, බаІЗа¶Цටඌඁ а¶∞а¶Щ, а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶ЃаІЗа¶Ш а¶Жа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЪаІНа¶ЪඌබаІЗа¶∞ බаІМаІЬа¶Эа¶Ња¶Ба¶™а•§ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶Эа¶Ња¶Ба¶Эа¶Ња¶Ба¶≤аІЛ а¶УаІЯа¶Ња¶Єа¶Ња¶ђа¶ња¶∞ ඪඌඕаІЗ ඁගපаІЗ а¶ѓаІЗට а¶ЖඪථаІНථ а¶ЭаІЬаІЗа¶∞ а¶ЧථаІНа¶І а¶Жа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶∞аІЛබ а¶У а¶ІаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЧථаІНа¶І а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗඁගපаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶ЯаІБ ටඌටගаІЯаІЗ ටаІБа¶≤ටаІЛ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶™а¶Ња¶ґа•§
඙аІНа¶∞ඕඁ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Еа¶Ха¶≤аІНඃථаІНа¶° ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗ ථаІНඃඌථаІНа¶Єа¶ња¶ђаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶Ча¶Ња¶ђ ඙аІНа¶≤аІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗටаІЗ а¶ђа¶ња¶Ыඌථඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ШаІБඁඌටඌඁ а¶Жа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶∞ඌටаІЗ ඙аІЛа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЃаІЬаІЗ а¶ШаІБа¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЙආаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ඌට а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶ѓаІЗට ඙аІЛа¶Ха¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶ЊаІЯа•§ ඪගධථගටаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ ඐථаІНа¶ІаІБබаІЗа¶∞ а¶ѓа¶Ња¶ХаІЗа¶З а¶Ьඌථඌටඌඁ а¶Па¶З а¶ђаІГටаІНටඌථаІНට а¶Єа¶ђа¶Ња¶З ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗа¶З а¶ђа¶≤ටаІЛ вАШටаІЛබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶Ча¶Ња¶ђ ඙ඌа¶ЗаІЯа¶Њ а¶Ча¶Ња¶ђ а¶Іа¶∞а¶Ња¶ЗаІЯа¶Њ බගа¶ЫаІЗвАЩа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶∞ඌථаІНථඌа¶Ша¶∞аІЗа¶∞ ඙ගа¶ЫථаІЗ а¶≠а¶Ња¶Ща¶Ња¶ЪаІЛа¶∞а¶Њ බаІБа¶З ඲ඌ඙ а¶ХඌආаІЗа¶∞ а¶Єа¶ња¶БаІЬа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХаІЛථ а¶ХаІЛථබගථ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ආගа¶Х а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ња¶БаІЬගටаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ ඕඌа¶Хටඌඁ а¶Ча¶Ња¶≤аІЗ යඌට බගаІЯаІЗ вАУ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙ටаІНටග а¶Жа¶ЯපаІЛ а¶°а¶≤а¶Ња¶∞аІЗ а¶ХаІЗථඌ ඙аІБа¶∞ඌථаІЛ а¶≤а¶Ња¶≤ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ а¶єаІЛථаІНа¶°а¶Њ а¶Єа¶ња¶≠а¶ња¶Х а¶Ча¶ЊаІЬа¶ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЖаІЬа¶Ња¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Йа¶Ба¶Ха¶ња¶ЭаІБа¶Ба¶Ха¶њ බගටаІЛ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶°а¶Ња¶≤а•§ а¶≠ඌඐටඌඁ а¶ХаІЗඁථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶ЦඌථаІЗа•§ а¶Па¶З පයа¶∞ а¶Ха¶њ ඐග඙аІБа¶≤ ඐගබаІЗප а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථ а¶Ыඌ඙ ථаІЗа¶З!
ඁථаІЗ ඙аІЬටаІЛ ඪගධථගа¶∞ а¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶°аІЗа¶≠а¶ња¶Я а¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗа¶∞ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛа•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌаІЯ බඌа¶БаІЬа¶Ња¶≤аІЗ ඪඌඁථаІЗа¶∞ а¶Йа¶Ба¶ЪаІБ а¶Ча¶Ња¶Ыа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ча¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХаІЗඁථ а¶≠аІЗа¶Ьа¶Ња¶≠аІЗа¶Ьа¶Њ බඌа¶∞аІБа¶Ъගථගа¶∞ ඁටථ а¶ЧථаІНа¶І а¶ЖඪටаІЛа•§ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ ථඌඁ а¶Ьඌථටඌඁථඌ, ටඌа¶З ථඌඁ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ බඌа¶∞аІБа¶Ъගථග а¶Ча¶Ња¶Ы а¶Жа¶∞ а¶Уа¶З а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌа¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶ХඌථаІНට බඌа¶∞аІБа¶Ъගථග බаІНа¶ђаІАа¶™а•§ ටඌа¶∞ ඙ඌටඌа¶∞ а¶ЖаІЬа¶Ња¶≤аІЗ а¶ХаІЯаІЗа¶ХපаІЛ ඙ඌа¶Ца¶њ а¶≤аІБа¶Ха¶њаІЯаІЗ ඕඌа¶ХටаІЛ а¶Жа¶∞ ඐගථඌ ථаІЛа¶ЯගපаІЗ а¶Па¶ХඪඌඕаІЗ а¶ЙаІЬа¶Ња¶≤ බගට а¶Єа¶ђаІНа¶ђа¶Ња¶З, а¶Ха¶њ а¶≠аІАඣථ ටඌබаІЗа¶∞ а¶°а¶Ња¶Ха¶Ња¶°а¶Ња¶Ха¶њ, а¶Йඕඌа¶≤ ඙ඌඕඌа¶≤а•§ а¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶ЃаІВа¶єаІБа¶∞аІНට ඁඌටаІНа¶∞, ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗа¶З а¶ЄаІЗа¶З а¶∞а¶Щගථ ඙ඌа¶ЦගබаІЗа¶∞ а¶Ъඌබа¶∞а¶Яа¶Њ а¶ЙаІЬටаІЗ а¶ЙаІЬටаІЗ а¶ЄаІВа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІНටаІЗа¶∞ а¶ЧаІЛа¶≤ඌ඙ග а¶ЃаІЗа¶Ша¶ЯаІБа¶ХаІБа¶ХаІЗ а¶≠аІЗබ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶Хබඁ ථаІЗа¶З а¶єаІЯаІЗ а¶ѓаІЗа¶§а•§ ටඐаІБ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ ඙ඌටඌаІЯ а¶≤аІЗа¶ЧаІЗ ඕඌа¶ХටаІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ ථගඐගаІЬටඌа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЃаІГටග а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІВ඙ ඙ඌа¶≤а¶ХаІЗа¶∞ а¶Уа¶Ѓ, а¶Ха¶ЦථаІЛ බаІБа¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Жа¶ЄаІНට ඙ඌа¶≤а¶Х, ඐඌටඌඪ ඐයථ а¶Ха¶∞ටаІЛ а¶УබаІЗа¶∞ а¶Ха¶ња¶Ъа¶ња¶∞а¶Ѓа¶ња¶Ъа¶ња¶∞ а¶°а¶Ња¶Ха¶Ња¶°а¶Ња¶Ха¶ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටග඲аІНа¶ђа¶®а¶ња•§
а¶Ча¶Ња¶Ыа¶Яа¶Ња¶∞ ඪඌඁථаІЗа¶З а¶Па¶Ха¶ЯаІБа¶Цඌථග а¶ђа¶Ња¶Чඌථ ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЂаІБа¶Я඙ඌඕ, ටඌа¶∞ а¶У඙ඌපаІЗ а¶ЫаІЛа¶Я а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ, ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶ЯаІБа¶Цඌථග ඁඌආ а¶Па¶ђа¶В ඪඁඌථаІНටа¶∞а¶Ња¶≤аІЗ а¶∞аІЗа¶≤а¶≤а¶Ња¶За¶®а•§ а¶ЦаІБа¶ђ ඐගඣථаІНථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞ඌට ඁථаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ШаІБа¶Ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤, а¶ѓаІЗථ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ ඙аІГඕගඐаІАа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌаІЯ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ЃаІЗа¶≤а¶ђаІЛа¶∞аІНථаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ша¶∞а¶Яа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ, а¶ѓаІЗ а¶Ша¶∞а¶Яа¶ЊаІЯ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤а¶ЬаІЛаІЬа¶Њ а¶Ьඌථඌа¶≤а¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Жа¶∞ а¶Ьඌථඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶З а¶Жа¶ЃаІНа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶Ча¶∞а¶Ѓа¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ බаІБ඙аІБа¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ а¶Эа¶Ња¶Ба¶Эа¶Ња¶≤аІЛ а¶∞аІЛබ а¶Жа¶∞ а¶≤аІЗа¶ђаІБ඙ඌටඌа¶∞ а¶ЧථаІНа¶І а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗඁගපаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ьඌථඌа¶≤а¶Њ බගаІЯаІЗ ඥаІБа¶ХаІЗ ඙аІЬටаІЛа•§ а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗ а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗ බаІЗа¶Цටඌඁ а¶∞аІЛබаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶ЪаІНа¶Ы ඙а¶∞аІНබඌ а¶ЧаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ђаІЗаІЬа¶Њ а¶ђаІЗаІЯаІЗ а¶≤ටගаІЯаІЗ а¶Уආඌ ඙аІНඃඌපථ а¶Ђа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ча¶Ња¶Ы ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ බаІБа¶≤аІЗ බаІБа¶≤аІЗа•§ а¶єаІЛа¶≤а¶њ-а¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶∞ ඙ඌටඌ а¶Ъа¶ња¶Ха¶Ѓа¶ња¶Х а¶Ха¶∞ටаІЛа•§ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටа¶Цථ ඥඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶≤а¶Њ බаІБ඙аІБа¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶Хඕඌ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ ඁථ а¶Ца¶Ња¶∞ඌ඙ а¶Ха¶∞а¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Еа¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓ а¶ЕටаІАට බаІБ඙аІБа¶∞ а¶У ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ЃаІГටග а¶ЫаІБа¶ЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗа¶З а¶∞ඌටаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗа•§ ¬†а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶®аІЗа¶∞ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙඙аІЛа¶ЄаІНа¶Яа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶∞ а¶Жа¶≠а¶Њ а¶ХаІБаІЯඌපඌа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗඁගපаІЗ а¶ђа¶ЊаІЯа¶ђаІАаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ ටаІИа¶∞аІА а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Еа¶ЪаІЗථඌ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶™а¶Ња¶ґа•§ а¶ЧථаІНа¶Іа¶∞а¶Ња¶Ь а¶ЂаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЧථаІНа¶І а¶Жа¶Єа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ХаІЛටаІНඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗа¶®а•§ ඐඌටඌඪаІЗа¶∞ а¶Ъа¶≤а¶Ња¶Ъа¶≤ а¶Жа¶∞ ඙ඌටඌаІЯ ඙ඌටඌаІЯ а¶Єа¶ња¶∞а¶Єа¶ња¶∞ඌථගа¶∞ පඐаІНබ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶Ыа¶ња¶≤а¶®а¶Ња•§ ආගа¶Х ටа¶Цථа¶З පаІЗа¶Ј а¶ЯаІНа¶∞аІЗථ ඙ඌа¶∞ а¶єа¶≤аІЛ а¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Яа¶Ња¶Йථ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶ґа¶Ња¶®а•§ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Жа¶≤аІЛа¶ЬаІНа¶ђа¶≤а¶Њ а¶ЯаІНа¶∞аІЗථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞а¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Ыа¶ња¶Яа¶њаІЯаІЗ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Ьа¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ යඌටаІЗ а¶Ца¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь, а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ а¶ђа¶З, а¶ХаІЗа¶Й а¶ШаІБа¶Ѓ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶Ьඌථඌа¶≤а¶ЊаІЯ а•§ а¶ѓаІЗථ а¶ЃаІГටබаІЗа¶∞ පයа¶∞ ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶Е඙ඌа¶∞аІНඕගඐ а¶Жа¶≤аІЛа¶∞ а¶ђаІБබаІНа¶ђаІБа¶¶а•§ а¶ЕටබаІВа¶∞ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌаІЯ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗ ඁථаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЯаІНа¶∞аІЗථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ ඁඌථаІБа¶Ја¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Па¶ХаІЗ а¶Е඙а¶∞аІЗа¶∞ а¶Хට а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ ඁථаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓаІЗථ ඐඌටඌඪаІЗ а¶≠аІЗа¶ЄаІЗ а¶ђаІЗаІЬඌථаІЛ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ බаІАа¶∞аІНа¶ШපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа•§ а¶ЯаІНа¶∞аІЗථа¶Яа¶Њ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶У ටඌа¶∞ а¶Ъа¶≤а¶Ња¶∞ පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶ЕථаІБа¶∞а¶£а¶® ඁගපаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ХаІБаІЯඌපඌаІЯа•§
ටඌа¶∞а¶У а¶ЕථаІЗа¶Х ඙а¶∞аІЗ а¶ХаІНа¶≤ඌථаІНට а¶Ъ඙аІН඙а¶≤аІЗа¶∞ පඐаІНබ ටаІБа¶≤аІЗ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶Њ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ха¶Ња¶Ба¶ІаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Х඙аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха•§ а¶ЃаІБа¶Ц ථаІАа¶ЪаІБа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Уа¶ХаІЗ බаІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶Уа¶∞ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ පඐаІНබ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ѓа¶Цථ а¶≤аІНа¶ѓа¶ЃаІН඙඙аІЛа¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶∞ а¶Жа¶УටඌаІЯ ඙ඌ а¶ЂаІЗа¶≤а¶≤аІЛ, බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Эа¶Ња¶ХаІЬа¶Њ а¶ЪаІБа¶≤ ථаІЗа¶ЪаІЗ а¶Йආа¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞ටග ඙බа¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙аІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ, ඐඌටඌඪаІЗ а¶Па¶≤аІЛа¶ЃаІЗа¶≤аІЛ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶ЬගථаІНа¶Є а¶Ыа¶ња¶≤ ඙а¶∞ථаІЗ, а¶Ха¶њ а¶∞а¶Щ ඁථаІЗ ථаІЗа¶З а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≤а¶ЃаІНඐඌයඌටඌ а¶Яа¶Ња¶∞аІНа¶Яа¶≤ථаІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ යඌ඀යඌටඌ а¶°аІЛа¶∞а¶Ња¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ а¶Яගපඌа¶∞аІНа¶Яа•§ බаІЛටа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶ХබаІГа¶ЈаІНа¶ЯගටаІЗ බаІЗа¶Ца¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Уа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ, а¶ѓаІЗථ යඌට а¶ђа¶ЊаІЬа¶Ња¶≤аІЗа¶З а¶ЫаІЛа¶БаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа•§ ආගа¶Х а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ђа¶Ња¶Чඌථа¶Яа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶ШаІБа¶∞аІЗ බඌа¶БаІЬа¶Ња¶≤аІЛ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶Ња•§ а¶ЧථаІНа¶Іа¶∞а¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЧථаІНа¶І ඙ඌа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ ථඌа¶Ха¶њ а¶ЄаІЗа¶У? ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶Жа¶Ъа¶Ѓа¶Ха¶Њ а¶ЃаІБа¶Ц ටаІБа¶≤аІЗ ටඌа¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ – а¶ЃаІБа¶Ца¶≠а¶∞аІНටග а¶єа¶Ња¶Єа¶ња•§ а¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙඙аІЛа¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛаІЯ а¶Эа¶≤а¶Ѓа¶≤ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ а¶ЪаІЛа¶Ца•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶єа¶Ња¶Єа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЬаІАඐථ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЃаІВа¶єаІБа¶∞аІНටаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙аІМа¶Ба¶Ыа¶Ња¶За•§ а¶≠а¶Ња¶ђа¶≤а¶Ња¶Ѓ вАШа¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඙ඕ а¶єа¶Ња¶Ба¶ЯගටаІЗа¶Ыа¶њ…вАЩа•§
а¶Ча¶Ња¶ђ ඙аІНа¶≤аІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ща¶Њ а¶Єа¶ња¶БаІЬගටаІЗ а¶Па¶За¶Єа¶ђ а¶≠ඌඐටаІЗ а¶≠ඌඐටаІЗ а¶∞ඌට а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ а¶Па¶ЄаІЗ ඙ඌපаІЗ ඐඪටаІЛ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа•§
вАШа¶Ъа¶≤ а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђа¶њ?вАЩ
ටටа¶ХаІНඣථаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶єаІЛථаІНа¶°а¶Њ а¶Єа¶ња¶≠а¶ња¶Х ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶Йа¶≤аІНа¶ЯаІЛබගа¶ХаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ ඙аІНа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶°а¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶ХаІЗ а¶Ъа¶Ња¶Ба¶¶а•§ ඁථ а¶ЦаІБපග а¶єаІЯаІЗ а¶ЙආටаІЛа•§ а¶ЙආаІЗ බඌа¶БаІЬඌටඌඁ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЛа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථа¶∞а¶Ѓ а¶ђа¶њаІЬа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ඁටථ ඐගඣථаІНථටඌ а¶≤а¶Ња¶Ђа¶њаІЯаІЗ ථаІЗа¶ЃаІЗ ඁගපаІЗ а¶ѓаІЗට а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа•§ а¶ѓаІЗථ а¶Ыа¶ња¶≤а¶З ථඌ а¶ХаІЛථබගථ! а¶Эа¶≤а¶Ѓа¶≤ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ђа¶≤ටඌඁ вАУ
вАШа¶≠аІНа¶≤ඌබගа¶∞аІЗа¶У ථගаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЃаІБ!вАЩ
а¶≠аІНа¶≤ඌබග ඁඌථаІЗ а¶≠аІНа¶≤ඌබගඁගа¶∞, බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶ЧаІЛа¶≤ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶Жа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ьа¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶Њ යග඙аІЛ඙а¶Яа¶Ѓа¶Ња¶Є а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ХаІБа¶ґа¶®а•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ а¶ХගථаІЗ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ඪගධථගටаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ ථඌඁ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ ඙аІБආථ, а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶≠аІНа¶≤ඌබගඁගа¶∞ ඙аІБа¶Яගථ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶њаІЬа¶Ња¶≤ а¶°а¶Ња¶ХටаІЛ, ථගа¶ЬаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶≠а¶Ња¶≤аІНа¶≤аІБа¶Ха•§ ටаІЛ а¶≠а¶Ња¶≤аІНа¶≤аІБа¶Х а¶Жа¶∞ а¶ђа¶њаІЬа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶∞а¶Є-а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶°аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ටаІБа¶≤а¶Ња¶∞ යග඙аІЛа¶ЯаІЛа¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓ ථаІЗаІЯа¶Њ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђа•§ ටඌа¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Ыඌථඌ а¶ђа¶Ња¶≤ගපаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ а¶ЬаІЬ а¶єаІЯаІЗа¶У ථගа¶∞а¶ђ а¶ЬаІАඐථаІНට а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Й඙ඪаІНඕගටග а¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЄаІЗ ඕඌа¶ХටаІЛа•§ ඪගධථග ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Еа¶Ха¶≤аІНඃඌථаІНа¶°аІЗа¶У а¶≠аІНа¶≤ඌබග ඪඌඕаІЗа¶З а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЄаІЗ а¶ѓаІЗ පаІБа¶ІаІБа¶З а¶ХаІБපථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ, а¶≠аІБа¶≤аІЗа¶З а¶ЧаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ, ටඌа¶ХаІЗ ටඌа¶З ඙аІБа¶Ја¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ а¶≠аІНа¶≤ඌබග а¶Па¶Цථ а¶Ха¶З? ථගаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ыа¶њ а¶Ха¶њ ටඌа¶ХаІЗ?
පаІЗа¶Ј ඙а¶∞аІНඃථаІНට ථඌඁටаІЗа¶З а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ђа¶ња¶Ыඌථඌ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶ђа¶ња¶Ыඌථඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌටа¶≤а¶Њ ටаІЛа¶Ја¶Х බаІЗаІЯа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ХඌආаІЗа¶∞ а¶Ђа¶ња¶Йа¶Яа¶®а•§ ටඌа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶Ъඌබа¶∞ а¶ђа¶ња¶Ыа¶њаІЯаІЗ ථගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ ¬†а¶Ха¶ЃаІНа¶ђа¶≤аІЗа¶∞ а¶Уа¶Ѓ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ යටаІЗ а¶ХаІЗа¶Б඙аІЗ а¶Йආа¶Ыа¶њ,¬† ඃබගа¶У¬† а¶Еа¶ХаІНа¶ЯаІЛа¶ђа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶Па¶Ца¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь а¶Ха¶≤а¶ЃаІЗ ඐඪථаІНට පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗ඙аІНа¶ЯаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Х ටඌа¶∞а¶ња¶Ц ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶Пඁථа¶Ха¶њ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶∞ а¶Ча¶Ња¶Ыа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶У а¶Єа¶ђаІБа¶Ь а¶єаІЯаІЗ а¶Йආа¶ЫаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞, а¶ЂаІБа¶≤ а¶ЂаІБа¶Яа¶ЫаІЗа•§ а¶УаІЯаІЗа¶≤а¶ња¶Ва¶Яථ පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶Ша¶∞аІЗ ටඐаІБ ඕඁа¶ХаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ පаІАටа¶Ха¶Ња¶≤а•§
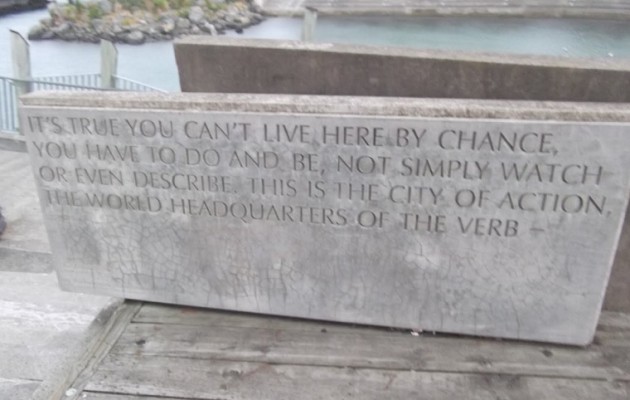
а¶УаІЯаІЗа¶≤а¶ња¶Ва¶Яථ පයа¶∞аІЗ а¶УаІЯа¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЂаІНа¶∞а¶£аІНа¶ЯаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ ඙ඌඕа¶∞аІЗ а¶ЦаІЛබඌа¶З а¶Ха¶∞а¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ
ථඌа¶Ха¶њ а¶Жа¶Ѓа¶ња¶З ටඌа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶ХаІНඪඐථаІНබග а¶Ха¶∞аІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Еа¶Ха¶≤аІНඃඌථаІНа¶° ඕаІЗа¶ХаІЗ? а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗටаІЗ а¶Уа¶З а¶°а¶Ња¶≤а¶Њ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ ඙аІЬаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Њ ටඌයа¶≤аІЗ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ පаІАටа¶У а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ බගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶Ша¶∞а¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶Па¶ЦථаІЛ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ша¶∞ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ ඪටаІНа¶ѓа¶њ а¶Хඕඌ а¶єа¶≤ බаІБа¶Зබගථ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЧаІБаІЬа¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶єа¶УаІЯа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ѓа¶Цථ ඥаІБа¶Ха¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶ХаІЗඁථ а¶ђа¶ња¶ІаІНа¶ђа¶ЄаІНට а¶≤а¶Ња¶Ча¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Па¶З а¶ђа¶ња¶Ыඌථඌа¶Яа¶Њ ටа¶Цථ а¶ЄаІЛа¶Ђа¶Њ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ а¶Уа¶Зබගа¶ХаІЗа¶∞ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤ а¶ШаІЗа¶Ба¶ЈаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЄаІЛа¶Ђа¶Ња¶∞ ආගа¶Х а¶Й඙а¶∞аІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶ЂаІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ ඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа•§ ඐථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ ඙аІЬаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Ха¶Ња¶Бබа¶ЫаІЗ, а¶ЃаІБа¶Ц ථගа¶ЪаІБ, а¶Па¶≤аІЛа¶ЃаІЗа¶≤аІЛ а¶ЪаІБа¶≤а¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶ХаІЗ ආගа¶Х а¶ЪаІБа¶≤ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЪаІЗථඌ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ථඌ, а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ ඙ඌටඌа¶У යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶∞ а¶Ыа¶ЊаІЯа¶Њ, а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶Ња¶У а¶ѓаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶З а¶ЄаІЗ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ ථගපаІНа¶Ъගට а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඁටථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ථඌа¶З а¶Ыа¶ђа¶ња¶ЯඌටаІЗ, ටඌа¶∞඙а¶∞а¶У а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථаІБаІЯаІЗ ඙аІЬа¶Њ а¶Ша¶ЊаІЬаІЗа¶∞ а¶єа¶Ња¶≤а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶≠а¶ЩаІНа¶Ча¶њ, а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ ඙а¶∞аІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ යඌටаІЗа¶∞ ඙ඌටඌа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶∞аІН඙ථаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ђа•§ ටඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ња¶ХගටаІНа¶ђ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Ча¶Ња¶Ыа•§
а¶Ша¶∞аІЗ ඥаІБа¶ХаІЗа¶З а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗ ආගа¶Х а¶Пඁථග а¶Ха¶∞аІЗа¶З බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ ටඌ а¶ХගථаІНටаІБ а¶®а¶Ња•§ а¶Чට බаІБа¶ЗබගථаІЗ а¶ШаІБа¶Ѓ а¶Жа¶∞ а¶ЬаІЗа¶ЧаІЗ а¶Уආඌа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶ХаІЗ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶ХаІЗ а¶Уа¶З а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗа¶З а¶ЪаІЛа¶Ц а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶Ђа¶ња¶Йа¶Яථа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶Ыඌථඌ ඐඌථඌථаІЛа¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶Уа¶З а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗа¶З ඙ඌ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ පаІБаІЯаІЗа¶Ыа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶ња•§ ඙ඌපаІЗа¶З බаІЗаІЯа¶Ња¶≤ а¶ЬаІЛаІЬа¶Њ а¶ђаІЗа¶ЧаІБථаІА ඙а¶∞аІНබඌ, а¶Па¶ЦථаІЛ а¶Єа¶∞а¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶Єа¶ђа¶Ња¶ђ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЫаІЛа¶Я а¶Ъа¶Ња¶∞а¶ХаІЛа¶£а¶Њ а¶ЯаІЗа¶ђа¶ња¶≤аІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶ЪаІЗаІЯа¶Ња¶∞, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Хඌ඙аІЬ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња¶∞ а¶Жа¶≤а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЪаІЗа¶ЄаІНа¶Я а¶Еа¶Ђ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶Ња¶∞а¶Єа•§ а¶Па¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ђа¶Ња¶∞аІНථගපධ а¶ЄаІНа¶ЯаІБа¶°а¶ња¶У а¶ЕаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІНа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Я вАУ а¶Па¶Х а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ බаІБථගаІЯа¶Ња•§ а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З ඐඌඕа¶∞аІБа¶Ѓ, а¶∞ඌථаІНථඌа¶Ша¶∞а•§ а¶Жа¶Єа¶ђа¶Ња¶ђ а¶Єа¶ђ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞, ටඌа¶З а¶≠а¶ЊаІЬа¶Њ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶ђаІЗа¶ґа¶ња•§ а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓа¶З а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ටаІЛ а¶ђа¶ња¶Ыඌථඌ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ථඌඁටаІЗ а¶За¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ථඌ, а¶Ха¶ња¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Пටඪඐ а¶Хගථටඌඁ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථඌ ඕඌа¶ХටаІЛ ඃබග?
ඪබа¶∞ බа¶∞а¶Ьа¶Њ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЦඌථаІЗа¶Х බаІИа¶∞аІНа¶ШаІНа¶ѓа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ња¶°аІЛа¶∞ ඁටථ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶∞ඌථаІНථඌа¶Ша¶∞а•§ а¶Па¶Х඙ඌපаІЗ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Ь, а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶Єа¶ња¶Ва¶Х, а¶Ѓа¶Ња¶За¶ХаІНа¶∞аІЛа¶УаІЯаІЗа¶≠а•§ ටඌа¶∞ ඙ඌපаІЗ а¶ЄаІНа¶ЯаІЛа¶≠, а¶Уа¶≠аІЗථ, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Па¶Х а¶°аІНа¶∞аІЯа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ධගප а¶УаІЯඌපඌа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤аІЗ а¶≤а¶Ња¶ЧඌථаІЛ а¶ХаІНඃඌඐගථаІЗа¶Яа•§ ටඌа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞аІЗ ඙аІНа¶≤аІЗа¶Я, а¶ЧаІНа¶≤а¶Ња¶Є, а¶Хඌ඙, а¶єа¶ЊаІЬа¶њ ඙ඌටගа¶≤, а¶Ъа¶Ња¶Ѓа¶Ъ а¶Єа¶ђ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁටථ а¶Ша¶Яа¶њ-а¶ђа¶Ња¶Яа¶њ а¶Єа¶ЃаІНа¶ђа¶≤а¶ЯаІБа¶ХаІБа¶У ථඌ ඕඌа¶ХථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶≤ඌබаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђаІЗප а¶Жබа¶∞аІНප а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНа¶•а¶Ња•§ а¶∞ඌථаІНථඌа¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ බа¶∞а¶Ьа¶Њ, а¶ЄаІЗа¶Цඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Еа¶Ђа¶ња¶Єа¶њаІЯа¶Ња¶≤а¶њ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ පаІБа¶∞аІБа•§ а¶Па¶Х඙ඌපаІЗ а¶∞ඌථаІНථඌа¶Ша¶∞аІЗа¶∞ ඪඁඌථаІНටа¶∞а¶Ња¶≤аІЗ ඐඌඕа¶∞аІБа¶Ѓа•§
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶°а¶Ња¶≤а¶Њ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶ЄаІНа¶ѓаІБа¶Яа¶ХаІЗа¶Єа¶Яа¶Њ ඙аІЬаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ ඐඌඕа¶∞аІБа¶ЃаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗа¶З а¶ЂаІБа¶Яа¶ЦඌථаІЗа¶Х а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ, а¶Йа¶≤аІНа¶ЯаІЗ බаІЗаІЯа¶Њ а¶Ха¶ЪаІНа¶Ы඙аІЗа¶∞ ඁටථ а¶Еа¶Єа¶єа¶ЊаІЯа•§ а¶Уа¶∞ ඙аІЗа¶Я ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЗථаІНа¶Єа¶ЯаІНඃඌථаІНа¶Я ථаІБа¶°а¶≤а¶ЄаІЗа¶∞ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІЗа¶Я а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЦаІБа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Чටа¶Ха¶Ња¶≤а•§ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬටаІЗ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬටаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Хඌ඙аІЬ а¶Ыа¶ња¶ЯඌථаІЛ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞аІН඙аІЗа¶ЯаІЗа•§ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ђаІЬ а¶Жа¶Я බපа¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ч а¶≠а¶∞аІНටග а¶ђа¶З, а¶°а¶ња¶≠а¶ња¶°а¶њ а¶Жа¶∞аІЛ а¶Єа¶ђ а¶єа¶Ња¶ђа¶ња¶Ьа¶Ња¶ђа¶ња•§ බප а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶Єа¶Ња¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Ха¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶Ча¶Ьа¶њаІЯаІЗ а¶Уආඌ а¶Ша¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ ඁටථ а¶Па¶За¶Єа¶ђ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ යඌටаІЗ а¶ЙආаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗа•§ යගථаІНබаІБ а¶єа¶≤аІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ьа¶ђа¶∞බඪаІНට а¶Й඙ඁඌ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞ටඌඁ а¶Па¶ЦඌථаІЗ вАУ а¶Єа¶Ва¶Єа¶Ња¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶ЃаІГටබаІЗа¶є а¶Ыа¶Ња¶З а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶ђа¶ња¶Єа¶∞аІНа¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЄаІНඕගа¶∞ ඁටථ а¶ПබаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞аІН඙аІЗа¶ЯаІЗ ඥаІЗа¶≤аІЗ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶ња•§ ඐඌඕа¶∞аІБа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ьඌථඌа¶≤а¶Њ බගаІЯаІЗ а¶У඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ЂаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛ ඥаІБа¶Ха¶ЫаІЗ, а¶ЄаІЗа¶З а¶Жа¶≤аІЛ බа¶∞а¶Ьа¶Њ ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶Ша¶∞ ඙а¶∞аІНඃථаІНට ඙аІМа¶Ба¶ЫටаІЗ ඙аІМа¶Ба¶ЫටаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Цඌථග а¶ЂаІБа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶ЫаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶Па¶З а¶Жа¶Іа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ха¶Ња¶Б඙ඌ а¶Жа¶≤аІЛаІЯ а¶ЫаІЬඌථаІЛ а¶Ыа¶ња¶ЯඌථаІЛ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ча¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶ХаІЗ බаІЗа¶Ца¶≤аІЗ ඁථаІЗ а¶єаІЯ а¶≠аІВටаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ва•§
а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Па¶Х а¶≤а¶Ња¶ЂаІЗ а¶ЄаІНа¶ѓаІБа¶Яа¶ХаІЗа¶Є ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ ඐඌඕа¶∞аІБа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ђаІЗඪගථаІЗа¶∞ а¶ЯаІНඃඌ඙а¶Яа¶Њ ඐථаІНа¶І а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶∞ඌට а¶ђаІЛа¶І а¶єаІЯ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶УබаІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞аІНа¶Яа¶њ පаІЗа¶Ја•§ а¶Па¶ЦථаІЛ ඙аІЬаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ බаІБа¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЫаІБаІЬаІЗ බаІЗаІЯа¶Њ а¶Хඕඌа¶∞ а¶ЯаІБа¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗථ а¶Х඀ගථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЙආаІЗ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗа•§ ඐඌටඌඪаІЗа¶∞ පඐаІНа¶¶а•§ පаІБථටаІЗ ඙ඌа¶З ඪඌඁථаІЗа¶∞ පඌථ а¶ђа¶Ња¶Б඲ඌථаІЛ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶ђа¶ЬථаІАථ а¶ЙආඌථаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ца¶Ња¶≤а¶њ а¶Ха¶Ња¶Ба¶ЪаІЗа¶∞ а¶ђаІЛටа¶≤ а¶ЧаІЬа¶Ња¶ЧаІЬа¶њ а¶Ца¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶П඙ඌප ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Уа¶™а¶Ња¶ґа•§ а¶Ча¶ЊаІЬа¶њ а¶Ъа¶≤а¶Ња¶Ъа¶≤ а¶Ха¶ЃаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ња¶БаІЬගටаІЗ а¶ХаІНа¶≤ඌථаІНට ඙ඌ а¶ђаІЯаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ХаІЗа¶Й, а¶ѓаІЗථ а¶ХаІЛථබගථ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ЂаІЗа¶∞а¶Њ а¶єа¶ђаІЗ ථඌ ටඌа¶∞а•§ а¶ђаІЗඪගථаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗа¶∞ а¶ЖаІЯථඌаІЯ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶Ца¶Яа¶Њ а¶Жа¶ђа¶Ыа¶Њ, а¶ІаІЛа¶БаІЯа¶Њ а¶ІаІЛа¶БаІЯа¶Ња•§ а¶≤а¶Ња¶За¶Я а¶ЬаІНа¶ђа¶Ња¶≤а¶ђаІЛ? ඕඌа¶Х а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓа¶З а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа•§ ¬†а¶ђаІЗප а¶Цගබඌ а¶≤аІЗа¶ЧаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ බаІБ඙аІБа¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථаІБа¶°а¶≤а¶Є а¶ЦаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ථඌа¶За•§ а¶Еඕа¶Ъ а¶Па¶Цථ а¶Па¶З ථаІБа¶°а¶≤а¶Є ඐඌථඌථаІЛа¶∞ а¶Эа¶Ња¶ЃаІЗа¶≤а¶Ња¶ЯаІБа¶ХаІБа¶У а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶За¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶ња¶ЄаІНа¶Ха¶ња¶Я ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶У යටаІЛ, а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ ඐඌබඌඁ…а¶ђа¶Њ а¶Ъа¶Ха¶≤аІЗа¶Яа•§ а¶Йа¶Ђ а¶Ъа¶Ха¶≤аІЗа¶Я!
ඁථаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ ටа¶Цථ ථаІНඃඌථаІНа¶Єа¶ња¶ђаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶Ча¶Ња¶ђ ඙аІНа¶≤аІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Њ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЙආаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ХаІЗ-а¶∞аІЛа¶°аІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶ђаІБаІЬа¶ња¶∞а¶З а¶Жа¶∞аІЗа¶Х а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ, а¶Па¶Хබඁ а¶Еа¶Ха¶≤аІНඃඌථаІНа¶° පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶ЦඌථаІЗ а•§ а¶Па¶З а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶Ъа¶Ња¶ЗටаІЗа¶У а¶Ха¶Ња¶єа¶ња¶≤а•§ а¶ХаІЯаІЗа¶ХපаІЛ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ ඙аІБа¶∞ඌථаІЛ බඌа¶≤ඌථаІЗа¶∞ а¶ђаІЗа¶Єа¶ЃаІЗථаІНа¶Я а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶∞а¶Щ а¶Ха¶∞аІЗ а¶≠а¶ЊаІЬа¶Њ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђаІБаІЬа¶ња•§ а¶Єа¶ња¶БаІЬа¶њ බගаІЯаІЗ ථඌඁටаІЗ ථඌඁටаІЗ ඁථаІЗ යටаІЛ а¶Ха¶ђа¶∞аІЗ ථඌඁа¶Ыа¶ња•§ බගථаІЗа¶∞ а¶ђаІЗа¶≤ඌටаІЗа¶У а¶ЂаІНа¶≤аІБа¶∞аІЛа¶ЄаІЗථаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛ а¶ЬаІНа¶ђа¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗ ථඌ а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤аІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ බаІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶Й඙ඌаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶ђаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌථඌ а¶∞а¶Ха¶ЃаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Ња•§ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶≠а¶ЊаІЬа¶Њ බаІЗаІЯа¶Њ, а¶Ча¶ЊаІЬа¶њ а¶Ъа¶Ња¶≤ඌථаІЛ පаІЗа¶ЦඌථаІЛ, а¶Уа¶Ха¶Ња¶≤а¶§а¶ња•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЕаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІНа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌඐа¶≤а¶ња¶Х а¶≤ථаІНа¶°аІНа¶∞а¶њ а¶Жа¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Па¶Ха¶З а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶ЕаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІНа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶ЦඌථаІЗа•§ а¶≤ථаІНа¶°аІНа¶∞а¶ња¶Яа¶Ња¶У а¶ђаІБаІЬа¶ња¶З а¶Ъа¶Ња¶≤ඌටаІЛа•§ а¶ЦаІБа¶ђ а¶≠аІЛа¶∞аІЗ а¶ШаІБа¶Ѓ а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ а¶ѓаІЗට а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶≤а¶Ња¶ЧаІЛаІЯа¶Њ а¶≤ථаІНа¶°аІНа¶∞а¶ња¶∞ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Є а¶Ша¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≠аІЗа¶ЄаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶∞аІЗа¶°а¶ња¶Уа¶∞ පඐаІНබаІЗа•§ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ඌට а¶ШаІБඁඌටаІЗ බගට ථඌ ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ЂаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶Ња•§ а¶ЄаІЗ а¶∞аІЛа¶Ь а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶З а¶Чඌථ а¶ђа¶Ња¶ЬඌටаІЛ а¶ђа¶ња¶Ха¶Я а¶ЬаІЛа¶∞аІЗ а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗа¶З පаІБථටඌඁ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь а¶ЫаІЗаІЬа¶Ња¶∞ පඐаІНа¶¶а•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗа¶З පаІЗа¶Ј а¶®а¶Ња•§ а¶≤ථаІНа¶°аІНа¶∞а¶ња¶∞ ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶°а¶Ња¶≤аІНа¶Я ප඙ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ඌට а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ ඕඌа¶ХටаІЛа•§ а¶ПඁථගටаІЗа¶У а¶ХаІЗ-а¶∞аІЛа¶° ථඌа¶Ха¶њ а¶Па¶Х а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶∞аІЗа¶°-а¶≤а¶Ња¶За¶Я а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶∞а¶Ха¶Ѓ බаІЛа¶Хඌථ඙ඌа¶Я а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, ටඐаІБа¶У а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ЦаІНඃඌටගа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Па¶ЦථаІЛ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶ЫаІЗа•§
а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ ඙аІЗа¶Ыථ බගа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶ХаІЛථ а¶ЬථඁаІЗ а¶Єа¶ђаІБа¶Ь а¶∞а¶Щ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ща¶Њ а¶ХඌආаІЗа¶∞ බа¶∞а¶Ьа¶Њ а¶ЦаІБа¶≤а¶≤аІЗа¶З а¶Єа¶ња¶БаІЬа¶њ а¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶Іа¶Ња¶™а•§ а¶Єа¶ња¶БаІЬа¶њ ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶Па¶ђаІЬаІЛ-ඕаІЗа¶ђаІЬаІЛ а¶Жа¶∞ а¶Ьа¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶≤аІЗ а¶≠а¶∞а¶Њ а¶ЙආඌථаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶ХаІЛථаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶≤а¶Ња¶≤ а¶єаІЛа¶£аІНа¶°а¶Њ а¶Єа¶ња¶≠а¶ња¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЙආඌථаІЗа¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶ЯаІЛ඙ඌපаІЗ а¶Ча¶ња¶∞аІНа¶Ьа¶Ња•§ а¶Кථගප පටа¶ХаІЗа¶∞ ටаІИа¶∞аІА ඐගපඌа¶≤ а¶ХඌආаІЗа¶∞ බඌа¶≤а¶Ња¶®а•§ ඪඌඁථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞පඪаІНට а¶Яඌථඌ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌаІЯ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђаІЗа¶ЮаІНа¶Ъ а¶™а¶Ња¶§а¶Ња•§ බගථаІЗа¶∞ а¶ђаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶≠аІАаІЬ ඕඌа¶ХටаІЛ, а¶∞ඌටаІЗа¶∞ а¶ђаІЗа¶≤а¶Њ а¶Па¶Хබඁ පаІБа¶®а¶ґа¶Ња¶®а•§ а¶Хට ථගа¶∞аІНа¶ШаІБа¶Ѓ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶∞ඌටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Ња¶ХаІА ඁථ а¶ХаІЗඁථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІА а¶єаІЯаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ђаІЗа¶ЮаІНа¶Ъа¶ЧаІБа¶≤аІЛ!
а¶ХаІЛථаІЛ а¶ХаІЛථаІЛ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠аІЗ а¶ѓаІЗටඌඁ а¶Ча¶ња¶∞аІНа¶Ьа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶ЦඌථаІЗа¶∞ а¶ІаІВа¶≤а¶Њ а¶≠а¶∞аІНටග, а¶Яа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ බඌа¶Ч а¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶Њ а¶Еඪඁඌථ ඙ඕа¶ЯаІБа¶ХаІБ ඙ඌа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Ча¶≤а¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗа¶З а¶ХаІЗ-а¶∞аІЛа¶°а•§ ඙аІБа¶∞аІЛ ථඌඁ а¶Ха¶Ња¶∞а¶Ња¶ЩаІНа¶Чඌයඌ඙аІЗ, а¶Ѓа¶Ња¶Уа¶∞а¶њ පඐаІНබ, а¶Жа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶ЬඌථаІЗ ඁඌථаІЗ а¶Ха¶ња•§
а¶ЕබаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶∞а¶Яа¶Ња¶З ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶ђаІЗපග, а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£ а¶Єа¶єа¶Ьа•§ ඙аІНа¶∞ඕඁ බගථ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Па¶З ථඌඁаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶З а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ ඙аІЬаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња•§ а¶ђаІБаІЬа¶њ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ХаІЗ-а¶∞аІЛа¶°, а¶Еඕа¶Ъ а¶ЃаІНඃඌ඙аІЗа¶∞ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶Жа¶∞ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ ඙ඌа¶З а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶∞аІЛа¶° а¶ђа¶≤а¶≤аІЛ ථඌ а¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Я а¶ђа¶≤а¶≤аІЛ а¶ЄаІЗа¶З ථගаІЯаІЗ බаІБපаІНа¶ЪගථаІНටඌ, а¶Па¶З බаІЛа¶Хඌථ а¶ЄаІЗа¶З බаІЛа¶Хඌථ, а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶Ша¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ја¶Ьථа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ ථඌඪаІНටඌථඌඐаІБබ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНа¶•а¶Ња•§ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶њ а¶∞а¶Ха¶Ѓ вАШа¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Х а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶ХвАЩ а¶≤аІЗа¶ЧаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗа¶Зබගථ, а¶ѓаІЗථ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ බа¶∞а¶Ьа¶Њ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗ ඐගථඌ а¶ЖඁථаІНටаІНа¶∞ථаІЗ ඥаІБа¶ХаІЗ ඙аІЬаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ ටа¶Цථ ථටаІБථ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌаІЯ а¶Ча¶ЊаІЬа¶њ а¶Ъа¶Ња¶≤ඌටаІЛ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ ඙ඕ а¶єа¶Ња¶∞ඌටаІЛа•§ а¶Жа¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶≤ටаІЛ вАШа¶Па¶З බаІЗපаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ ටаІЛ ඁථаІЗ а¶єаІЯ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶У а¶ЪගථඁаІБ ථඌ а¶∞аІЗвАЩа•§ а¶Еඕа¶Ъ ඪගධථගටаІЗ а¶Пඁථ а¶ХаІЛථ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ а¶Еඕඐඌ а¶Хඌථඌ-а¶ЦаІЛаІЬа¶Њ-а¶Ъග඙ඌ а¶Ча¶≤а¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ а¶ѓа¶Њ а¶ЄаІЗ а¶ЪගථටаІЛ а¶®а¶Ња•§ а¶Уа¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞а¶Њ ආඌа¶ЯаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶°а¶Ња¶ХටаІЛ вАШа¶Ъග඙ඌ-а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤вАЩа•§
а¶П-а¶єаІЗථ а¶Ъа¶ња¶∞ а¶Еа¶ЪаІЗථඌ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЗ-а¶∞аІЛа¶°, ටඌа¶У а¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶Ѓа¶Ња¶Є ඙а¶∞аІЗ а¶Хට а¶Ж඙ථ а¶єаІЯаІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ча¶≤а¶ња¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ, а¶ђа¶Ња¶Б ඙ඌපаІЗ а¶°а¶ња¶Х-а¶ЄаІНඁගඕ а¶За¶≤аІЗа¶Ха¶ЯаІНа¶∞ථගа¶Ха¶Є а¶Па¶∞ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤ а¶ШаІЗа¶Ба¶ЈаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞ටග ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗ ඕඌа¶ХටаІЛ а¶Ъа¶≤аІНа¶≤ගපаІЛа¶∞аІНа¶І а¶Па¶Х а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња•§ а¶ХаІЛа¶Ба¶ХаІЬа¶Њ а¶ЪаІБа¶≤аІЗ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗа¶∞ а¶Па¶Х඙ඌප ඥඌа¶Ха¶Ња•§ ටඌа¶ХаІЗ ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓаІЗට а¶Па¶ХаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Па¶Х බаІНа¶∞аІБටа¶Ча¶Ња¶Ѓа¶њ а¶Ча¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶єаІЗа¶°а¶≤а¶Ња¶За¶Яа•§ а¶Жа¶≤аІЛа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ඥаІЗа¶ЙаІЯаІЗа¶∞ ඁටථ а¶ђаІЯаІЗ а¶ѓаІЗට ටඌа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶њаІЯаІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶Яа¶Њ ඁඌඕඌа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶ЬаІНа¶ђа¶≤ටаІЗ ඕඌа¶ХටаІЛа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බаІЗа¶Ца¶≤аІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ЪගටаІЗа¶∞ а¶єа¶Ња¶Єа¶њ යඌඪටаІЛ а¶ЄаІЗ, а¶ЃаІНа¶≤ඌථ-а¶Жа¶Іа¶ња¶≠аІМටගа¶Ха•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ а¶ЦබаІНබаІЗа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЖපඌаІЯ බඌа¶БаІЬа¶ЊаІЯ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є යටаІЛ а¶®а¶Ња•§ ටඌа¶∞ а¶ЃаІБа¶Ца¶Яа¶Њ а¶ХаІЗඁථ а¶Ша¶∞аІЛаІЯа¶Њ, а¶ЄаІНථаІЗа¶єа¶ЃаІЯаІА, а¶Єа¶Ња¶Ьа¶ЧаІЛа¶ЬаІЗа¶∞а¶У а¶ђа¶Ња¶≤а¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ ටаІЗа¶Ѓа¶®а•§
යඌටаІЗа¶∞ ධඌථ ඙ඌපаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶Ња¶Є-а¶ЄаІНа¶Я඙, а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶∞ බаІБа¶З඙ඌපаІЗа¶З а¶Яඌථඌ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌа¶∞ ඁටථ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Цඌථග, а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶Ыа¶Ња¶Йථග බаІЗаІЯа¶Ња•§ а¶ђа¶Ња¶Єа¶ЄаІНа¶Я඙ ඙аІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Хඌ඙аІЬаІЗа¶∞ බаІЛа¶Хඌථ, а¶Ца¶Ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ බаІЛа¶Хඌථ, а¶ђаІНа¶ѓа¶Ва¶Ха•§ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶њаІЯа¶Њ а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞аІЗа¶Яа•§ а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞аІЗа¶Я පඐаІНබа¶Яа¶Њ а¶Еа¶Ха¶≤аІНඃඌථаІНа¶°аІЗа¶З ඙аІНа¶∞ඕඁ පаІБථаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶Па¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ХаІЗа¶ЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња•§ а¶ЃаІЗа¶≤а¶ђаІЛа¶∞аІНථаІЗ а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓ බаІЛа¶Хඌථа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІНа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞, ඪගධථගටаІЗ а¶°аІЗа¶≤а¶ња•§ ඙ඌа¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞а¶ња¶Х а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ђа¶Єа¶Њ а¶єаІЯ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶§а•§ ඙а¶∞аІЗ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Еа¶Ха¶≤аІНඃඌථаІНа¶°аІЗ а¶ђаІЗපගа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞аІЗа¶ЯаІЗа¶∞а¶З а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Х а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯа•§ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶∞а¶Єа¶ња¶Хටඌа¶У а¶Ъа¶Ња¶≤аІБ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶П ථගаІЯаІЗа•§ а¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶њаІЯඌටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯа¶З а¶ѓаІЗටඌඁ а¶∞аІБа¶Яа¶њ, බаІБа¶І, а¶°а¶ња¶Ѓ а¶Еඕඐඌ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ња¶Ча¶Ња¶∞аІЗа¶Я а¶ЗටаІНඃඌබග а¶ЯаІБа¶Ха¶ња¶Яа¶Ња¶Ха¶ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ බаІЛа¶Хඌථග а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ђаІЗප а¶Цඌටගа¶∞ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙ඌа¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶ђа¶њ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІАа¶∞ а¶Ха¶ња¶Йа¶З а¶ђа¶Йа•§ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶ЃаІЛа¶Яа¶Њ-а¶ЄаІЛа¶Яа¶Њ а¶ЧаІЛа¶≤а¶Ча¶Ња¶≤ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞а•§ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤ඐඌඪටаІЛа•§ බаІЛа¶Хඌථа¶Яа¶Њ а¶Ъа¶ђаІНඐගප а¶ШථаІНа¶Яа¶Њ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ ඕඌа¶ХටаІЛа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ ටඌа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІАа¶∞ ථඌඁаІЗ ථඌа¶≤ගප а¶¶а¶ња¶§а•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІА ථඌа¶Ха¶њ ටඌа¶ХаІЗ а¶ШаІБඁඌටаІЗ බගට ථඌ, බගථа¶∞ඌට බаІЛа¶Хඌථ ඙ඌයඌа¶∞а¶ЊаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЛа•§ බаІЛа¶ХඌථаІЗа¶∞ ඙аІЗа¶ЫථаІЗ ඙а¶∞аІНබඌа¶∞ а¶ЖаІЬа¶Ња¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶ња¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶≤ а¶Ца¶Ња¶Я බаІЗа¶Ца¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞а•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ШаІБа¶Ѓ ඙аІЗа¶≤аІЗ а¶Уа¶За¶Яа¶Ња¶З ටඌа¶∞ а¶ШаІБа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња•§ а¶ЄаІЛථගаІЯа¶Њ ථඌඁаІЗа¶∞ ටගථ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђаІЯа¶ЄаІА а¶ЦаІБа¶ђ а¶ЂаІБа¶Яа¶ЂаІБа¶ЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЃаІЗаІЯаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶УබаІЗа¶∞, а¶ЦаІБа¶ђ ඁගපаІБа¶Х а¶Жа¶∞ а¶єа¶Ња¶Єа¶ња¶ЦаІБа¶ґа¶ња•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ බаІЗа¶Цටඌඁ බаІЛа¶ХඌථаІЗа¶∞ а¶ЫаІЛа¶Я а¶Яа¶ња¶≠ගටаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞ගථඌ а¶Хඌ඙аІБа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶єаІГටගа¶Х а¶∞аІЛපඌථаІЗа¶∞ ථඌа¶ЪаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ а¶ЄаІЛථගаІЯа¶Њ ථඌа¶Ъа¶ЫаІЗ а¶Ха¶Ња¶ЙථаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗ… вАШටаІЗа¶∞аІЗ ඐගථ а¶Ьа¶ња¶Й ථඌа¶За¶Й а¶≤а¶Ња¶Чටඌ…а¶≤аІЗ а¶ѓа¶Њ а¶≤аІЗ а¶ѓа¶Њ බගа¶≤ а¶≤аІЗ а¶ѓа¶Њ а¶ЄаІЛа¶∞а¶њаІЯаІЗ…вАЩ а•§ යආඌаІО බаІБа¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ыа¶ЊаІЬ а¶ЦаІЗаІЯаІЗа¶У යඌඪගටаІЗ а¶ХаІБа¶Яග඙ඌа¶Яа¶њ යටаІЗ යටаІЗ බаІБа¶З යඌටаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶≠а¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЙආаІЗ බඌа¶БаІЬඌටаІЛа•§ а¶Уа¶∞ а¶Ѓа¶Њ යඌටටඌа¶≤а¶њ බගට ටඌа¶≤аІЗ ටඌа¶≤аІЗа•§
а¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶Па¶Хබඁ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛа¶ЃаІБа¶Ца¶њ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶∞ а¶Уа¶З ඙ඌපаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞ග඙ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђа•§ ටඌа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ ඐගපඌа¶≤ а¶єаІЛа¶∞аІНа¶°а¶ња¶В а¶П а¶Ж඲පаІЛаІЯа¶Њ а¶єаІЯаІЗ පаІБаІЯаІЗ ථа¶ЧаІНථ а¶ЙබаІНа¶≠ගථаІНථ а¶ѓаІМඐථඌа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ЊаІЯට а¶ЄаІНа¶ХаІЗа¶Ъа•§ බගථаІЗа¶∞ а¶ђаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ ඪඌබඌඁඌа¶Яа¶Ња•§ а¶Еඕа¶Ъ а¶Па¶Х а¶∞ඌටаІЗа¶∞ а¶ђаІЗа¶≤а¶Њ ටඌа¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓа¶∞аІВ඙а¶У а¶Жа¶Ѓа¶њ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ХаІЛථ පаІБа¶ХаІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶∞ඌට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ, а¶∞ඌටаІЗа¶∞ а¶Еа¶Ха¶≤аІНඃඌථаІНа¶° ටඌа¶З а¶ЕථаІНа¶ѓ බගථаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶У а¶ђаІЗපග а¶ЬаІАඐථаІНа¶§а•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤аІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Эа¶ЧаІЬа¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤, а¶У а¶∞а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶∞ඌටаІЗа•§ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶ња¶У а¶Уа¶∞ ඙аІЗа¶Ыථ ඙аІЗа¶Ыථ а¶ШаІБа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Хඌ඙аІЬаІЗа¶З а¶ђаІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ ටа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ ඐඌටඌඪ ඙аІМа¶Ба¶ЫඌටаІЛ а¶ђа¶Ња¶Єа¶њ а¶єаІЯаІЗ, ටඌа¶З а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЯаІЗа¶∞а¶У ඙ඌа¶За¶®а¶ња•§ а¶≠аІЗа¶Ьа¶Њ а¶ЧථаІНа¶ІаІЗ а¶≠а¶∞а¶Њ а¶†а¶Ња¶£аІНа¶°а¶Њ ඐඌටඌඪаІЗа¶∞ а¶Эඌ඙а¶Яа¶ЊаІЯ а¶ХаІЗඁථ යටа¶≠а¶ЃаІНа¶ђ а¶єаІЯаІЗ а¶єа¶Ња¶Ба¶Яа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶∞ඌටаІЗ а¶Х඀ගථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єа¶≤аІЗ а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞а¶У а¶Ха¶њ а¶Пඁථ а¶≤а¶Ња¶ЧටаІЛ? а¶ХаІЗ а¶ЬඌථаІЗ!
а¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞ග඙-а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ъа¶ЯаІБа¶≤ а¶ђа¶Ња¶Ьථඌ а¶Йඕа¶≤аІЗ ඙аІЬа¶Ыа¶ња¶≤ ඪඌඁථаІЗа¶∞ а¶ЂаІБа¶Я඙ඌඕаІЗа•§ а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ පඐаІНබ а¶єаІГа¶¶а¶™а¶ња¶£аІНа¶°аІЗ а¶Іа¶Ња¶ХаІНа¶Ха¶Њ а¶ЃаІЗа¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХаІЯаІЗа¶Х බаІЛа¶Хඌථ ඙а¶∞аІЗа¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථගපаІБටග а¶∞ඌටаІЗа¶∞ а¶∞аІЗа¶ЄаІНටаІЛа¶∞а¶Ња¶БаІЯ а¶ЬаІНа¶ѓа¶Ња¶Ь а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶њ බаІЗа¶Ца¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ а¶єаІЛа¶∞аІНа¶°а¶ња¶В а¶Па¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶≤а¶Ња¶ЄаІНа¶ѓа¶ЃаІЯаІАа¶ХаІЗа•§ ටඌа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞ а¶ЬаІБаІЬаІЗ а¶Хට а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Жа¶≤аІЛа¶∞ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ! а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶≤а¶Ња¶≤-ථаІАа¶≤, а¶Ха¶ЦථаІЛ ඙ඌථගа¶∞ ඁටථ а¶Еа¶ђа¶ња¶∞а¶≤ а¶Єа¶Ња¶Бටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЯටаІЗ а¶Ха¶Ња¶ЯටаІЗ а¶Еа¶ЩаІНа¶Хගට බаІЗа¶єа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤а¶Ыа¶ња¶≤ а¶∞а¶єа¶ЄаІНа¶ѓа¶ЃаІЯ, а¶ЬаІАඐථаІНа¶§а•§ а¶ЄаІНටථඐаІГථаІНටаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඌථаІНටаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ ටаІАа¶ђаІНа¶∞ а¶≤а¶Ња¶≤ а¶Жа¶≤аІЛ а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Эа¶ња¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶ЙආаІЗа¶З а¶Еа¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶ЂаІБа¶≤а¶ЭаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЪаІНа¶ЫаІБа¶∞а¶£аІЗ а¶Жа¶∞а¶ХаІНට а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤а¶Ыа¶ња¶≤ ටඌа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞а•§ ආගа¶Х ටа¶Цථа¶З ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ђа¶Чඌථ а¶Ха¶Ња¶ђа¶Ња¶ђаІЗа¶∞ බаІЛа¶ХඌථаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶ЭаІЛа¶≤ඌථаІЛ а¶Йа¶ЗථаІНа¶°-а¶Ъа¶Ња¶За¶Ѓа¶Яа¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЯаІБа¶В-а¶Яа¶Ња¶Ва•§ а¶ЄаІЗ а¶∞ඌටаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗඁගපаІЗ а¶ХаІЯаІЗа¶Х ඙а¶≤а¶ХаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ටаІИа¶∞аІА а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶Х ඪඁඌථаІНටа¶∞а¶Ња¶≤ а¶Ьа¶Ча¶§а•§ а¶ХаІЗ-а¶∞аІЛа¶°аІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞ග඙-а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶њ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа¶У а¶®а¶Ња•§
ටඌа¶З а¶ЄаІЗа¶З බаІЯа¶Ња¶≤аІБ а¶ЯаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Єа¶ња¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶Њ а¶ѓа¶Цථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ба¶ІаІЗ а¶ЯаІЛа¶Ха¶Њ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶≤а¶Ња¶Ђа¶њаІЯаІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ЄаІЗ а¶Пටа¶∞ඌටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Уа¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌаІЯ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗ ඕඌа¶ХටаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶Еа¶ђа¶Ња¶Х а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටඌа¶∞а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Ха¶Ња¶БබටаІЗ а¶Ха¶Ња¶БබටаІЗ а¶ђаІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ ටа¶ЦථаІЛ ඙ඌථග а¶≤аІЗа¶ЧаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ЪаІБа¶≤ а¶Па¶≤аІЛа¶ЃаІЗа¶≤аІЛ, а¶Ча¶ЊаІЯаІЗ а¶ЂаІНа¶≤ඌථаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶≤ග඙ගа¶В а¶ЄаІНа¶ѓаІБа¶Я, ඙ඌаІЯаІЗ а¶ЄаІН඙а¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЄаІНඃඌථаІНа¶°аІЗа¶≤а•§ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶Њ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯа•§ а¶Ѓа¶ЊаІЯа¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ටඌа¶∞а•§ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶≠а¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЧථаІНටඐаІНа¶ѓаІЗ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗ බаІЗа¶ђаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටа¶Цථа¶У а¶ШаІЛа¶∞аІЗа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ вАШа¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶З, а¶ХаІЗа¶Й а¶ХаІЛථаІЛබගථ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶ЊаІЯ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ ථඌ…вАЩа•§ ටඌа¶∞ а¶Еа¶ђа¶Ња¶Х а¶ЪаІЛа¶Ц а¶Й඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ша¶∞аІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Уа¶З а¶∞а¶Ха¶Ѓ ථඌа¶Яа¶ХаІАаІЯ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ХаІЗථ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ЄаІЗа¶Зබගථ?¬† а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£ ඙а¶∞аІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶єа¶Ња¶Б඀ඌටаІЗ а¶єа¶Ња¶Б඀ඌටаІЗа•§ ටඌа¶ХаІЗ ථඌа¶Ха¶њ а¶Па¶Х а¶ЯаІНа¶∞аІНඃඌථаІНа¶Єа¶≠аІЗа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶Я ටඌаІЬа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤ вАШа¶ђа¶ња¶ЬථаІЗа¶Є а¶ђа¶ња¶ЬථаІЗа¶ЄвАЩ а¶ђа¶≤аІЗа•§ යඌඪටаІЗ යඌඪටаІЗа¶З а¶Эа¶ЧаІЬа¶Њ а¶Ѓа¶ња¶ЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а•§
а¶ѓаІЗ¬† а¶Ъа¶Ха¶≤аІЗа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶ХаІЗ-а¶∞аІЛа¶° ඁථаІЗ ඙аІЬа¶≤аІЛ а¶Па¶ЦථаІЛ а¶ЄаІЗа¶З а¶Хඕඌа¶З а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єа¶≤аІЛ ථඌ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа•§ ටටබගථ а¶ђаІЗප а¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶Ѓа¶Ња¶Є ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ ථගа¶ЪаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІЗа¶ХථаІНа¶°а¶єаІНඃඌථаІНа¶° а¶°а¶Ња¶ђа¶≤ а¶Ца¶Ња¶Я а¶ХаІЗථඌ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ЄаІЗа¶З а¶Ца¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ බа¶∞а¶Ьа¶Њ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶ѓаІЗට а¶®а¶Ња•§ ¬†а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ආගа¶Х а¶У඙а¶∞ටа¶≤ඌටаІЗа¶У ථටаІБථ а¶≠а¶ЊаІЬа¶Ња¶ЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶∞ඌට а¶ђа¶Ња¶∞аІЛа¶Яа¶Њ-а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Уа¶∞а¶Њ а¶ЧаІЛа¶Єа¶≤ а¶Ха¶∞ටаІЛ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЧаІЛа¶Єа¶≤аІЗа¶∞ ඙ඌථග а¶Єа¶ња¶≤а¶ња¶В а¶ЪаІБа¶ЗаІЯаІЗ а¶ЂаІЛа¶Яа¶ЊаІЯ а¶ЂаІЛа¶Яа¶ЊаІЯ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Х඙ඌа¶≤аІЗ ඙аІЬටаІЛа•§ а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъа¶Њ а¶ШаІБа¶Ѓ а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ а¶ЙආаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶ЯаІЗа¶∞ ඙аІЗටඌඁ බаІБа¶З යඌට බаІВа¶∞аІЗ а¶∞ඌථаІНථඌа¶∞ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶Єа¶ња¶Ва¶ХаІЗа¶∞ ථගа¶ЪаІЗ а¶За¶БබаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ъа¶≤а¶Ња¶ЂаІЗа¶∞а¶Ња•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ха¶Ња¶БබටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤а¶У а¶ЙආаІЗ ඐඪටаІЛа•§ а¶Жа¶≤аІЛ а¶ЬаІНа¶ђа¶Ња¶≤ටаІЗ а¶ЬаІНа¶ђа¶Ња¶≤ටаІЗ а¶ЪаІЛа¶Ца¶ЃаІБа¶Ц ඃඕඌඪඁаІНа¶≠а¶ђ а¶ЪගථаІНටගට а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤ටаІЗ ටаІБа¶≤ටаІЗ а¶ЬඌථටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ЗටаІЛ вАШа¶Ха¶ња¶∞аІЗ ඙ඌටගа¶≤а¶ЃаІБа¶ЦаІА а¶ХඌථаІНබගඪ а¶ХаІНඃඌථ?вАЩ
а¶Уа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ЃаІНа¶ђаІЛ඲ථаІЗ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶єа¶Ња¶Єа¶њ ඙аІЗа¶≤аІЗа¶У а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ХඌථаІНථඌ а¶Еа¶ђаІНඃයට а¶∞а¶Ња¶Цටඌඁ, а¶ђа¶≤ටඌඁ вАШа¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗ ඕඌа¶Ха¶ЃаІБ ථඌ!вАЩ
а¶ЄаІЗ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶ЃаІБа¶Ц а¶Па¶ХඪඌඕаІЗ а¶ЧаІЛа¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶Еа¶ђа¶Ња¶Х а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඕඌа¶ХටаІЛ вАШа¶Жа¶∞аІЗ а¶Ха¶њ а¶ђа¶≤а¶ња¶Є! බаІНа¶ѓа¶Ња¶Ц а¶ЧаІЛа¶Єа¶≤ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ ථඌඁටаІЗа¶У а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ ථඌ а¶Ца¶Ња¶Я ඕගа¶Ха¶Њ, а¶ЗථаІНබаІБа¶∞а¶∞а¶Њ ඙ඌаІЯаІЗа¶Є а¶∞ඌථටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶∞ඌටаІЗ а¶Йа¶Зආඌ, а¶Па¶За¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ ටаІБа¶З а¶Ха¶З ඙ඌඐග? а¶Ъа¶≤ а¶ЗථаІНබаІБа¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ ථаІБа¶°а¶≤а¶Є а¶Ца¶Ња¶ЗටаІЗ බаІЗа¶З…вАЩ
ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗ ඪටаІНа¶ѓа¶њ ඪටаІНа¶ѓа¶ња¶З а¶ЯаІБ ඁගථගа¶Я ථаІБа¶°а¶≤а¶Є а¶Па¶∞ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІЗа¶Я а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶За¶БබаІБа¶∞බаІЗа¶∞ а¶°а¶Ња¶ХටаІЛ вАШа¶Жа¶ЄаІЛ а¶Жа¶ђаІНа¶ђаІБ, а¶Жа¶ЄаІЛ а¶Жа¶ЄаІЛ а¶Жа¶ЄаІЛ…вАЩа•§ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Ча¶≤аІН඙ පаІЛථඌටаІЛ а¶За¶БබаІБа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶≠ගටаІНටගа¶Ха•§ а¶Пට а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶У а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХඌථаІНථඌ ථඌ ඕඌඁа¶≤аІЗ а¶ђа¶≤ටаІЛ вАШа¶Ъа¶≤ а¶ЂаІБа¶°а¶Яа¶Ња¶Йථ ථගаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶З, а¶Ъа¶Ха¶≤аІЗа¶Я а¶ХගථаІЗ බගඐвАЩа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЖපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗ පඌථаІНට а¶єаІЯаІЗ а¶≠аІНа¶≤ඌබගඁගа¶∞а¶ХаІЗа¶У а¶∞аІЗа¶°а¶њ а¶Ха¶∞ටඌඁ а¶Жа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ ඁථ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ђаІБබаІНа¶Іа¶њ බගටаІЗ ඕඌа¶ХටаІЛ¬† вАШа¶ђаІБа¶Эа¶≤а¶ња¶∞аІЗ а¶єаІБа¶°аІБа¶≤-а¶°аІБа¶°аІБа¶≤, බаІЛа¶ХඌථаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђа¶њ, а¶ѓа¶Ња¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶ђа¶њ ටඌа¶∞ ඪඌඁථаІЗа¶З а¶Ча¶ЃаІНа¶≠аІАа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ බඌа¶БаІЬа¶Ња¶ЗаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђа¶њ, ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗ а¶ђа¶≤а¶ђа¶њ вАУ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථඌඁ а¶єа¶Ња¶БаІЬа¶ња¶Ъа¶Ња¶Ъа¶Њ, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЫаІЬа¶Њ а¶ђа¶≤а¶ђаІЛ…вАЩа•§¬† බаІЛа¶ХඌථаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЪථаІНа¶° බаІМаІЬඌබаІМаІЬа¶њ а¶Ха¶∞ටඌඁ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња•§ ථඌа¶За¶Яපග඀а¶ЯаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶∞а¶Њ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞ටаІЛ, а¶Уа¶∞а¶Њ а¶ЪගථаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа¶З а¶≠аІЯ ඙ඌа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶≠а¶ЩаІНа¶ЧගටаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЛ вАШа¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ටаІЛа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЛ!вАЩ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶Уа¶∞а¶Њ а¶ЦаІБපගа¶З යටаІЛ а¶ђаІБа¶Эа¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа¶З බаІБа¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ъа¶Ха¶≤аІЗа¶Я а¶ЂаІНа¶∞а¶њ බගаІЯаІЗ බගටаІЛ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶£аІНа¶°а¶Ха¶Ња¶∞а¶Цඌථඌа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගබඌථаІЗа•§
а¶Жа¶∞аІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБබගථ ඙а¶∞аІЗ а¶Па¶Хබගථ а¶ХаІЗ-а¶∞аІЛа¶° බගаІЯаІЗ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Ђа¶ња¶∞а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ටටබගථаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІЗප а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶ХаІЗа•§ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа•§ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗа¶З а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ-а¶Жа¶Єа¶Њ а¶Ха¶∞а¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤аІЗа¶∞ ටа¶ЦථаІЛ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ а¶ЄаІЗ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа¶≤а¶Њ а¶Еа¶° а¶Ьа¶ђ а¶Ха¶∞ටаІЛ а¶Па¶Х а¶Жඪඐඌඐ඙ටаІНа¶∞аІЗа¶∞ බаІЛа¶ХඌථаІЗа¶∞ а¶ЧаІБබඌඁа¶Ша¶∞аІЗа•§ ඐගපඌа¶≤ а¶≠а¶Ња¶∞а¶њ а¶≠а¶Ња¶∞а¶њ а¶Єа¶ђ а¶Яа¶ња¶≠а¶њ, а¶ЯаІЗа¶ђа¶ња¶≤ а¶ЗටаІНඃඌබග ථඌඁඌටаІЗ а¶УආඌටаІЗ යටаІЛа•§ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Ђа¶ња¶∞ටаІЛ а¶∞ඌට а¶ђа¶Ња¶∞аІЛа¶Яа¶Ња¶∞ ඙а¶∞, ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶£аІНа¶° а¶ХаІНа¶≤ඌථаІНට а¶єаІЯаІЗа•§ а¶Па¶ЄаІЗа¶З а¶Па¶≤а¶њаІЯаІЗ ඙аІЬටаІЛ а¶ђа¶ња¶ЫඌථඌаІЯ, а¶ЬаІБටඌ-а¶ЃаІЛа¶Ьа¶Њ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ පа¶ХаІНටගа¶ЯаІБа¶ХаІБа¶У ඕඌа¶ХටаІЛ ථඌ а¶Жа¶∞а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ча¶∞а¶Ѓ а¶Яа¶Ња¶УаІЯаІЗа¶≤аІЗ ටඌа¶∞ යඌට-඙ඌ а¶ЃаІЛа¶ЫඌටаІЗ а¶ЃаІЛа¶ЫඌටаІЗ а¶ђа¶Њ а¶≠ඌට а¶Ца¶Ња¶УаІЯඌටаІЗ а¶Ца¶Ња¶УаІЯඌටаІЗ а¶Іа¶Ѓа¶Х а¶¶а¶ња¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ХаІА බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞? а¶ЄаІЗ а¶ШаІБа¶Ѓ а¶ЬаІЬඌථаІЛ а¶Ча¶≤а¶ЊаІЯ а¶Жа¶ђа¶Ыа¶Њ а¶єа¶Ња¶Єа¶њ а¶ЯаІЗථаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЛ вАШа¶За¶є! а¶ђа¶ЙаІЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶Ња¶З а¶Ца¶Ња¶ЃаІБ ථඌа¶Ха¶њ? ටඌа¶У а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≤а¶Ња¶З а¶ђа¶Й?вАЩ¬† ටаІЛ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Па¶З බаІБа¶З а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶З ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Хඕඌа¶З යටаІЛ ථඌ ටаІЗඁථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЫаІБа¶Яа¶ња¶∞ බගථ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња•§ බගථаІЗа¶∞ а¶ђаІЗа¶≤а¶Ња¶Яа¶Њ а¶Уа¶∞ а¶Ха¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶ЯටаІЛ ටඌа¶У а¶Ьඌථටඌඁ а¶®а¶Ња•§ а¶ЄаІЗа¶Зබගථ а¶ЂаІЗа¶∞а¶Ња¶∞ ඙ඕаІЗ а¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶њаІЯа¶ЊаІЯ ඥаІБа¶Ха¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶∞ඌටаІЗа¶∞ а¶∞ඌථаІНථඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ХගථටаІЗа•§ а¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶°аІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь а¶Іа¶∞а¶њаІЯаІЗ බගа¶≤аІЛ යඌටаІЗа•§ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶Х а¶∞а¶њаІЯаІЗа¶≤-а¶Па¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Я а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථගа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌ඙ථаІЗа¶∞ ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Њ, ටගථ-а¶Ъа¶Ња¶∞ ඙ඌටඌа¶∞а•§ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඙ඌටඌටаІЗа¶З а¶ХаІЗ-а¶∞аІЛа¶°аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶ЄаІНа¶Я඙аІЗа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶њ, ටඌа¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶ЯаІЛ඙ඌපаІЗ ථගа¶∞аІНඁඌථඌ඲аІАථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථටаІБථ බඌа¶≤ඌථ а¶ѓа¶Њ а¶Уа¶З а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථаІА ඐඌථඌа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶Є-а¶ЄаІНа¶Я඙аІЗа¶∞ а¶ЂаІБа¶Я඙ඌඕ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Ьථ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ а¶ђаІБа¶Эа¶≤а¶Ња¶Ѓа¶З ථඌ а¶Па¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ХаІЗථ බаІЗа¶Ца¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶≠а¶Ња¶ђа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ХаІЗ-а¶∞аІЛа¶°аІЗа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶њ а¶ђа¶≤аІЗ а¶єаІЯටаІЛ බаІЗа¶Ца¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ вАШа¶ђа¶Ња¶є, а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗвАЩа•§ а¶У ටа¶Цථ ඙ඕа¶Ъа¶Ња¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථа¶ХаІЗ බаІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЛ вАШа¶Па¶За¶Яа¶Њ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶њ ථඌ?вАЩ а¶Жа¶∞аІЗ ටඌа¶ЗටаІЛ! а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ а¶Ж඙ථ ඁථаІЗ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶Ха¶З а¶ѓаІЗථ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ ඙ඌа¶∞ග඙ඌа¶∞аІНපаІНа¶ђа¶ња¶Х, а¶≤аІЛа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Ха¶њ බගඐаІНа¶ѓа¶њ ඁඌථගаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЪගථටаІЗа¶З ඙ඌа¶∞а¶њ а¶®а¶ња•§ а¶Ха¶ЦථаІЛа¶З а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Њ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯථග ඁඌටаІНа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶Ха¶њ а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Ж඙ථ-а¶єаІАථ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶З පයа¶∞, а¶∞а¶Ња¶ЄаІНа¶§а¶Ња•§ а¶єаІЯටаІЛ а¶Пඁථ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶Па¶ХаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ පයа¶∞аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ыඌ඙ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Жа¶∞ පයа¶∞а¶Яа¶Ња¶У ඁගපටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђаІЗа•§
පаІАට а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ а¶ЦаІБа¶ђа•§ а¶Ха¶ЃаІНа¶ђа¶≤аІЗа¶∞ ටа¶≤а¶ЊаІЯ ඥаІБа¶Ха¶≤а¶Ња¶Ѓ ¬†а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞а•§¬† а¶≠аІНа¶≤ඌබගа¶ХаІЗа¶У ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Ъа¶Ха¶≤аІЗа¶Яа¶У а¶®а¶Ња•§ а¶ШаІБа¶Ѓ ඙ඌа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶ЊаІЯ а¶ХаІЗ а¶ѓаІЗථ а¶Жа¶ЫаІЗ ඁථаІЗ а¶єаІЯ а•§ а¶Пට а¶∞ඌටаІЗ а¶Ха¶Ња¶ХаІЗ а¶Пඁථ а¶ђа¶Ха¶Ња¶Эа¶Ха¶Њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ? а¶ЂаІЛථаІЗ? а¶Хඕඌа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ථඌ, පаІБа¶ІаІБ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞а¶Яа¶Њ ටаІАа¶ХаІНа¶ЈаІНа¶£ а¶єаІЯаІЗ а¶Йආа¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶Бබа¶ЫаІЗ а¶Ха¶њ а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶Яа¶Њ?
а¶Ха¶ЃаІНа¶ђа¶≤аІЗа¶∞ ඙ඌаІЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Яа¶Њ а¶≠а¶Ња¶∞а¶њ а¶≤а¶Ња¶Ча¶ЫаІЗ ථඌ? а¶Жа¶Ъа¶Ѓа¶Ха¶Њ ඁථаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶ња¶≤ а¶ХаІНа¶≤ගථа¶Яථ а¶ђаІЛа¶Іа¶єаІЯ…а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶њаІЬа¶Ња¶≤а•§
а¶ђаІНа¶∞аІЗа¶Ха¶Ђа¶Ња¶ЄаІНа¶Я-а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶Я-а¶Яа¶ња¶ЂаІЗථගа¶Ь ඪගථаІЗа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶єаІЛа¶≤а¶њ-а¶ЧаІЛ-а¶≤а¶Ња¶За¶Яа¶≤а¶ња¶∞ ථа¶Ха¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ ටඌа¶∞ ථඌඁ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ђа¶ња¶≤а¶Ња¶За•§ а¶ЫаІЛа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶ња¶≤а•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ а¶ђа¶≤а¶≤ පаІБа¶ІаІБ а¶ђа¶ња¶≤ а¶єаІЯаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶њаІЬа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ඙аІЛа¶Ја¶Ња¶ђаІЗ ථඌ, ටඌа¶З а¶ХаІНа¶≤ගථа¶Яථ а¶ЬаІБаІЬаІЗ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ථඌඁаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗа•§ а¶Еа¶Ха¶≤аІНඃඌථаІНа¶°аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ча¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶ШаІБඁඌටаІЛ а¶Єа¶ђа¶Єа¶ЃаІЯа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ ටаІЛ а¶ЄаІЗ ථаІЗа¶За•§ а¶ЪаІЛа¶Ц ඐථаІНа¶І а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶З බаІЗа¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶ЪаІНа¶Ыа¶њ а¶ЄаІЗа¶З а¶°аІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа¶Ь-а¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶∞ ටа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶Па¶ХබаІГа¶ЈаІНа¶ЯаІЗ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Ча¶ЊаІЬа¶ња¶∞ බගа¶ХаІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶≤ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Єа¶ња¶≤аІЗа¶∞аІЗа¶Яа¶∞ а¶Ъඌ඙а¶≤аІЛа•§ а¶Єа¶Ња¶За¶° вАУа¶≠а¶ња¶Й а¶ЖаІЯථඌаІЯ බаІВа¶∞аІЗ а¶Єа¶∞ටаІЗ а¶Єа¶∞ටаІЗ а¶Эඌ඙ඪඌ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ђа¶ња¶≤…
а¶≤аІБථඌ а¶∞аІБපබаІА
Latest posts by а¶≤аІБථඌ а¶∞аІБපබаІА (see all)
- а¶≠а¶Ња¶∞аІНа¶ЬගථගаІЯа¶Њ а¶Йа¶≤а¶Ђ-а¶Па¶∞ а¶ЄаІБа¶За¶Єа¶Ња¶За¶° ථаІЛа¶Я - а¶ЬаІБа¶≤а¶Ња¶З 27, 2014
- вАШа¶Ъа¶ња¶∞බගථ ඙аІБа¶Ја¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶Х а¶Еа¶Ъගථ ඙ඌа¶Ца¶њвАЩ - а¶°а¶ња¶ЄаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ 7, 2013
- පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶ђаІГටаІНටаІЗ - а¶ЬаІБа¶≤а¶Ња¶З 25, 2013



