а¶ХаІНа¶∞ථගа¶Ха¶≤а¶Є а¶Еа¶Ђ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Њ а¶≤а¶ња¶ХаІБа¶За¶° а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶ња•§а•§ а¶Йа¶Ѓа¶ђаІЗа¶∞аІНටаІЛ а¶Па¶ХаІЛ а•§а•§
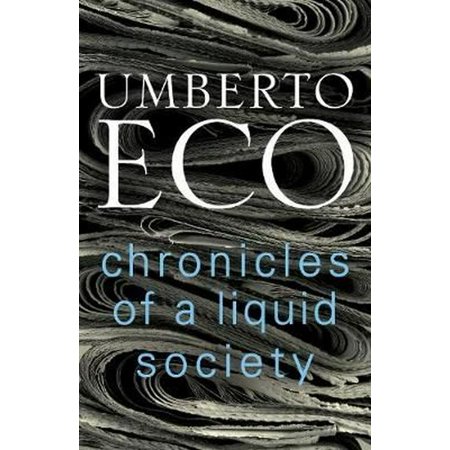
а¶ђа¶За¶Яа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶њ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපа¶Г аІ®аІ¶аІІаІ≠а•§
а¶Па¶З පටඌඐаІНබаІАа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ බаІЗаІЬ බපа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ха¶≤ а¶Ша¶Яථඌа¶∞ а¶Шඌට-඙аІНа¶∞ටගа¶ШඌටаІЗа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞ බගаІЯаІЗ а¶Жа¶Ча¶Ња¶За¶ЫаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ ටඕඌ а¶За¶Яа¶Ња¶≤а¶њ, вАШа¶ХаІНа¶∞ථගа¶Ха¶≤а¶Є а¶Еа¶Ђ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Њ а¶≤а¶ња¶ХаІБа¶За¶° а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶њвАЩ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞а¶З а¶ђаІЯа¶Ња¶®а•§ а¶Па¶З а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶ХаІЛ-а¶∞аІЛඁඌථ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶За¶єаІБබගබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤аІНа¶Я а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞ බගаІЯаІЗ а¶ѓаІЗа¶З а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶Жа¶За¶°аІЗථаІНа¶Яа¶ња¶Яа¶њ ථගаІЯа¶Њ බඌа¶БаІЬа¶ЊаІЯа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ, ටඌа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶∞а¶Щගථ а¶Жа¶Йа¶Яа¶≤аІБа¶Х ථඌථඌ а¶Ша¶Яථඌа¶∞ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶Ба¶ЪаІЗ а¶Чට පටඌඐаІНබаІАа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Па¶З පටඌඐаІНබаІАа¶∞ පаІБа¶∞аІБටаІЗ а¶Яа¶Ња¶≤а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶≤ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Хටඌ ථඌඁаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶ЧаІНа¶∞аІНඃඌථаІНа¶° а¶Жа¶За¶°а¶њаІЯа¶Њ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶ЬථаІНа¶Ѓ බගа¶Ыа¶ња¶≤аІЛ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЃаІЯ, ටඌа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Х а¶ЂаІЛа¶Ха¶∞ බගаІЯаІЗ а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞ а¶єа¶За¶ЫаІЗ а¶ђа¶ња¶ЪගටаІНа¶∞ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я а¶Жа¶∞ а¶Еа¶≠ගථඐ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣඌ඙а¶Яа•§ а¶Па¶З а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я а¶Жа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣඌ඙а¶Я а¶ЃаІЛа¶Ха¶Ња¶ђаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ ඙аІБа¶∞ඌථඌ а¶ЪගථаІНටඌ඙බаІН඲ටග а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶Ха¶∞ а¶®а¶Ња•§[pullquote][AWD_comments][/pullquote]
а¶Па¶ХаІЛа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐථඌ а¶Па¶За¶Цඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З පаІБа¶∞аІБа•§
඙а¶ЮаІНа¶Ъඌප а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Па¶ХаІЛ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІОа¶ђа¶Ња¶£аІА а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Жа¶Ча¶Ња¶ЃаІАа¶∞ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶єа¶ђаІЗ ථඌථඌ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞, ථඌථඌ а¶ЕටаІАටаІЗа¶∞, ථඌථඌ පаІЗа¶ХаІЬаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞а•§ ටඌа¶∞ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶ѓаІОа¶ђа¶Ња¶£аІА, а¶ѓаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶єаІЛа¶Х ඪටаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£а¶ња¶§ а¶єа¶За¶ЫаІЗа•§ ඙а¶≤а¶ња¶Яа¶ња¶ХаІНа¶ЄаІЗа¶∞ ඙ඌа¶Ха¶Ъа¶ХаІНа¶∞аІЗ а¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶ђа¶∞аІН඲ඁඌථ а¶Па¶ХаІАа¶≠аІВටа¶Ха¶∞а¶£ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ а¶ШаІБа¶Ѓ а¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗ බගа¶≤аІЗа¶У а¶Па¶ХаІЛ¬† а¶ђа¶Ња¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ බа¶∞аІЛа¶Ьа¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶єаІЛа¶Ха•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤аІЗа¶З а¶≤а¶Ња¶≠ а¶ђаІЗපග а¶Ѓа¶Ња¶®а¶ђа¶Ѓа¶£аІНа¶°а¶≤аІЗа¶∞, ටඌටаІЗ ඀ගටථඌ а¶ПаІЬඌථаІЛ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ බа¶∞аІЛа¶Ьа¶Њ ඐථаІНа¶І а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ පаІБථа¶≤аІЗа¶З а¶Па¶ХаІЛа¶∞ ඁථаІЗ ඙а¶ЗаІЬа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ටඌа¶∞ පаІИපඐаІЗа¶∞ а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯබаІЗа¶∞ а¶Ха¶•а¶Ња•§ а¶Па¶З а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶ЄаІНа¶Яа¶∞а¶Ња¶З а¶ђа¶≤ටаІЛ, а¶За¶Яа¶Ња¶≤а¶њаІЯඌථа¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа•§ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ ඙аІЛа¶≤а¶Ња¶∞а¶Ња¶За¶ЬаІЗපථаІЗ а¶Жа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට ඪබඌ඙аІГඕගඐаІАටаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Жа¶∞а¶У а¶ЙථаІНа¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶єа¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ, а¶Па¶З а¶ђа¶ЗаІЯаІЗ а¶ЄаІЗ ටඌа¶З а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ а¶ЗටගයඌඪаІЗа¶∞ а¶∞аІЗа¶Ђа¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶ЄаІЗ, а¶РටගයаІНа¶ѓ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЬаІНа¶Юа¶ЊаІЯථаІЗа•§ ටඌа¶∞ а¶ђаІЯඌථаІЗа¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථ а¶Жа¶∞ а¶ЪගථаІНටඌ඙බаІН඲ටග а¶Зටගයඌඪඐගа¶ЪаІНа¶ѓаІБට а¶ЯаІНа¶∞аІНඃඌධගපථඌа¶≤ а¶Жа¶ІаІБථගа¶ХබаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ථඌ, а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ХаІЗ ඙ඌආ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯ а¶Іа¶∞аІНඁඌටаІАට а¶Па¶Х а¶Еа¶≤аІАа¶Х а¶У а¶Жබа¶∞аІНප а¶Ша¶Яථඌа¶∞ а¶Ђа¶≤а¶Ња¶Ђа¶≤ යගපඌඐаІЗа•§ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІАаІЯ а¶ЪගථаІНටඌඐගබ යගපඌඐаІЗ а¶Па¶ХаІЛ а¶ЃаІЗථаІЗ ථගа¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶Жа¶∞ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗබаІНа¶ѓа¶§а¶Ња•§ а¶Па¶З පටඌඐаІНබаІАටаІЗ ටඌ а¶Ъа¶ња¶єаІНථගට а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ња¶З а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я а¶ЃаІЛа¶Ха¶Ња¶ђаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Іа¶Ња¶™а•§
а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Па¶З а¶У඙аІЗථථаІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕථаІИටගа¶Х а¶Па¶ђа¶В а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х ඙аІНа¶∞ටගа¶ХаІВа¶≤ටඌа¶У а¶ђа¶∞аІНа¶§а¶Ѓа¶Ња¶®а•§ а¶Па¶Хබගа¶ХаІЗ а¶Ъа¶∞а¶Ѓ ටа¶∞а¶≤ටඌаІЯ а¶Жа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶ЄаІН඙ගа¶∞а¶ња¶Яа¶єаІАථ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ගаІЯඌථ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞ а¶Жබа¶∞аІНපගа¶Х ටඌа¶∞а¶≤аІНа¶ѓ, а¶Е඙а¶∞බගа¶ХаІЗ ඐගපаІНа¶ђаІЗа¶∞ ථඌථඌ ඙аІНа¶∞ඌථаІНට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ගаІЯඌථ а¶≠аІВа¶Ца¶£аІНа¶°аІЗ ඙ඌаІЬа¶њ а¶ЬඁඌථаІЛ а¶ЖබඁගබаІЗа¶∞ а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞а¶Њ а¶Єа¶Ва¶Ха¶ЯаІЗа¶∞ ඁඌටаІНа¶∞а¶Њ а¶Жа¶∞а¶У а¶ЂаІНඃඌථඌаІЯа¶Њ ටаІБа¶≤а¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶ХаІЛа¶∞ ඁටаІЗ, а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටаІЗ а¶Жබа¶∞аІНපගа¶Х а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я ථටаІБථ а¶∞а¶Ха¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶Ьа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Жබа¶∞аІНප а¶Йа¶∞аІНа¶ђа¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶ња•§ а¶Па¶ХаІЛ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞аІНа¶Ѓ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶Чට – а¶Па¶З а¶Жබа¶∞аІНපගа¶Х а¶Єа¶Ва¶Ха¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ ඙඙аІБа¶≤а¶ња¶Ьа¶Ѓа¶З а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х а¶Жබа¶∞аІНප යගපඌඐаІЗ а¶Ча¶£аІНа¶ѓ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ъа¶Ња¶∞බගа¶ХаІЗ – а¶Па¶Яа¶Ња¶З а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶Ьа¶Ѓ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞¬† ඙аІНа¶∞ටග඲аІНඐථග, а¶Єа¶Ња¶ђа¶Іа¶Ња¶®а•§
а¶Па¶З ඙඙аІБа¶≤а¶ња¶ЄаІНа¶Я а¶ЬаІБа¶≤аІБа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Яа¶Ња¶∞аІНа¶ЧаІЗа¶Я а¶Ха¶Ња¶∞а¶Њ? а¶Еа¶ђа¶Іа¶Ња¶∞ගටа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ШаІБа¶∞а¶Ња•§ а¶Ђа¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Жа¶ЄаІЗ, а¶Па¶З а¶Єа¶Ва¶Ха¶ЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ вАШа¶Е඙а¶∞вАЩබаІЗа¶∞ а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Я а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙? ඪථඌටථаІА а¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶За¶°аІЗථаІНа¶Яа¶ња¶Яа¶ња¶∞ а¶ђаІЯඌථ ටаІЛ ටඌа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ, පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ вАШа¶Єа¶ња¶Яа¶ња¶ЬаІЗථвА٠යගපඌඐаІЗ а¶Жබඁа¶ХаІЗ а¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Я а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶З ටඌа¶∞ а¶Рටගයඌඪගа¶Х ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶ђа¶ња¶≤аІАථ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ЄаІЛපаІНа¶ѓа¶Ња¶≤¬† а¶ЗථаІНа¶Яа¶ња¶ЧаІНа¶∞аІЗපථаІЗа¶∞ а¶Па¶Х ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ а¶ѓа¶Цථ а¶Жа¶За¶°аІЗථаІНа¶Яа¶ња¶Яа¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථ ඪඌඁථаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ ථඐඌа¶Чට а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІАаІЯබаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ – а¶Па¶ХаІЛ ටа¶Цථ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ටඌа¶∞ а¶ЕටаІАටа¶ХаІЗа¶У а¶Еа¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Е඙ඌа¶∞а¶Ча•§ а¶Па¶ХаІЛ ඁඌථаІЗ, а¶Па¶З а¶ЕටаІАටаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶ђа¶Ња¶єа¶ња¶Хටඌ а¶Жа¶ЫаІЗа¶Г а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶Чට, а¶РටගයаІНа¶ѓа¶Чට, ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Жа¶∞ а¶ЕඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶Ча¶§а•§ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶За¶Яа¶Ња¶≤а¶њаІЯඌථ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶Єа¶∞аІБа¶ЃаІЗ а¶ХаІНа¶∞аІБප а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶єа¶ђаІЗ а¶ХаІА ථඌ а¶Па¶З а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ђа¶ња¶Ъа¶≤ගට – а¶ХаІЛථ а¶ЙටаІНටа¶∞ ථඌ බගаІЯаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗථ ටа¶∞аІНа¶Х а¶Жа¶Ча¶ЊаІЯа¶Њ ථගටаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Ъа¶ња¶єаІНථටටаІНටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶Па¶ХаІЛ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗථ а¶ХаІНа¶∞аІБපаІЗа¶∞ вАШа¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞вАЩ а¶Єа¶ња¶ЃаІНа¶ђа¶≤ а¶єаІЯаІЗ а¶Уආඌа¶∞ а¶Ха¶•а¶Ња•§ а¶Жа¶∞ බаІЗපаІЗа¶∞ а¶≤а¶ња¶ЄаІНа¶Я බගටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Іа¶∞а¶ЊаІЯа¶Њ – а¶ѓаІЗа¶За¶ЦඌථаІЗ а¶Ъа¶Ња¶Бබටඌа¶∞а¶Њ а¶Й඙ඪаІНඕගට а¶ђа¶єа¶Ња¶≤ ටඐගаІЯටаІЗа•§ а¶Па¶ХаІЛа¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථ, а¶Па¶За¶Єа¶ђ а¶Єа¶ња¶ЃаІНа¶ђа¶≤аІЗа¶З а¶Ха¶њ ¬†а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗ? ථඌ а¶ХаІА а¶Єа¶ња¶ЃаІНа¶ђа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЬаІНа¶Юа¶ЊаІЯථ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶Зටගයඌඪ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶≠ගටаІНටගටаІЗ а¶ЬථаІНа¶Ѓ ථаІЗаІЯ? а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶ХаІА а¶ђаІБа¶Эа¶ЊаІЯ?
а¶Па¶З ඙аІНа¶∞පаІНථаІЗа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶Па¶ХаІЛ ඙а¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶ЗටаІЗ ථඌ බගа¶≤аІЗа¶У а¶ЕථаІНටට а¶Па¶За¶ЯаІБа¶ХаІБ а¶ђаІБа¶ЭаІЗ ථаІЗаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ – ථඌථඌ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣඌ඙а¶Я а¶У ඁඌටаІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Хථа¶Ьа¶Ња¶∞а¶≠аІЗа¶Яа¶ња¶≠аІЗа¶∞ а¶°аІЗ඀ගථගපථаІЗа¶∞ а¶Еබа¶≤ඐබа¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶ЗටගයඌඪඐගබබаІЗа¶∞ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶ЊаІЯ а¶ѓаІЗ а¶ЪаІЗа¶За¶ЮаІНа¶Ь а¶ЖඪටаІЗа¶ЫаІЗ вАУ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ђа¶ња¶≤а¶ХаІВа¶≤ а¶Єа¶Ьа¶Ња¶Ча•§ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ а¶Іа¶∞аІНඁඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Хටඌа¶ХаІЗ ඐඌබ බගаІЯаІЗ а¶Па¶ХаІЛ а¶Жа¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗථ ථඌ а¶ХаІЛථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З – а¶єаІЛа¶Х а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ගаІЯ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ а¶ђа¶Њ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ ථඐඌа¶Чට а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ,а¶ђаІМබаІНа¶І, а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ගඁබаІЗа¶∞ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа•§ а¶ЄаІЗ а¶ђа¶ња¶Ъа¶∞а¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶ЯаІБ ඪයථපаІАа¶≤ а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Па¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶§а¶ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£, а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ ටඌටаІЗа¶З а¶ЗථаІНа¶Яа¶ња¶ЧаІНа¶∞аІЗපථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථа¶Яа¶Њ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ ථටаІБථ а¶ХаІЛථ а¶єа¶≤аІЛа¶Ха¶Ња¶ЄаІНа¶Я а¶Жа¶∞ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶ѓаІБබаІНа¶І а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶З඙ඌа¶∞ а¶єа¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗа•§
а¶Па¶З ඪයථපаІАа¶≤ටඌа¶∞ а¶ђаІЯඌථ а¶єаІЯටаІЛ ථටаІБථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ථඌ, ටඌа¶∞ බаІЛа¶єа¶Ња¶ЗаІЯаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶Єа¶ђа¶Єа¶ЃаІЯа¶З а¶ѓа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ ටඌබаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Па¶ХаІЛа¶∞ ඙ඌа¶∞аІНඕа¶ХаІНа¶ѓа¶Яа¶Њ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ – а¶Па¶ХаІЛ а¶Па¶Яа¶≤а¶ња¶ЄаІНа¶Я а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІАаІЯ а¶Єа¶≠аІНඃටඌаІЯ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶ЯඌථබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ, ඙аІНа¶∞ටග඙ටаІНටග а¶У а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Ж඲ග඙ටаІНа¶ѓ а¶Еа¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗථ ථඌа¶За•§ а¶Па¶ХаІЛа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ – а¶Жа¶ІаІБථගа¶Хටඌа¶∞ ඙ටථаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ථඐаІНа¶ѓ а¶≠аІЛа¶Чඐඌබ а¶Жа¶∞ ඙аІБа¶Ба¶ЬගඐඌබаІЗ ථඣаІНа¶Я а¶єа¶ЗටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ ටа¶∞а¶≤ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶Жа¶ІаІНඃඌටаІНа¶Ѓа¶ња¶Х а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я බаІЗа¶Ца¶Њ බගа¶ЫаІЗ – ටඌ а¶ЃаІЛа¶Ха¶Ња¶ђаІЗа¶≤а¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ ථටаІБථ а¶ЄаІН඙ගа¶∞а¶ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶Жඁබඌථග а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЖඪටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶Па¶Яа¶Ња¶З а¶Єа¶єа¶Ьඌට а¶Па¶ђа¶В ටඌа¶З а¶ЄаІВа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ථටаІБථ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඪයථපаІАа¶≤ටඌа¶∞ а¶ђаІЯඌථ, а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Њ-а¶Іа¶≤а¶Њ-යගථаІНබаІБ-а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ-а¶За¶єаІБබග а¶Жа¶∞ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඐගථаІЛබаІЗа¶∞ а¶Ж඙ථඌаІЯа¶Њ ථаІЗаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶За¶Ьа¶ња¶≤а¶ња•§ а¶Па¶ХаІЛ а¶Па¶У а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Ъඌථ, а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ගаІЯඌථ а¶ЗටගයඌඪаІЗ ටඌ ථටаІБථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶®а¶Ња•§
а¶Жа¶∞аІЗа¶Хබගа¶ХаІЗ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Ьа¶∞аІБа¶∞аІА, ඪයථපаІАа¶≤ටඌа¶∞ а¶ђаІЯඌථ බගа¶≤аІЗа¶У а¶За¶Єа¶∞а¶ЊаІЯаІЗа¶≤ а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶°а¶ња¶Яа¶њ ථගаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞පаІНථ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶∞аІНඕаІНа¶ѓ а¶Йථග а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ ථඌа¶За•§ ටඌа¶∞ ඁටаІЗ, вАШа¶За¶єаІБබගබаІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Рටගයඌඪගа¶Х а¶Па¶ђа¶В а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ ඐඪටග а¶ЄаІНඕඌ඙ථаІЗа¶∞вАЩа•§ а¶Па¶З а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶За¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Я බаІЗаІЯа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶ЗථаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ගඁබаІЗа¶∞ а¶ХаІА а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗ ටඌа¶∞аІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶≤ටаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ථඌ а¶Па¶З а¶ђа¶ЗаІЯаІЗ (а¶Жපඌ а¶Ха¶∞а¶њ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ђа¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ඙аІЬа¶≤аІЗ а¶Па¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ)а•§ а¶Пඁථ а¶ХаІА, බаІБа¶З а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ча¶Ња¶∞аІЛ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶За¶Єа¶∞а¶ЊаІЯаІЗа¶≤ а¶ђаІЯа¶Ха¶Я а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞а¶У а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ХආаІЛа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶≤аІЛа¶Ъа¶Х а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ ටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£, вАШа¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ЄаІНа¶Ха¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠аІЗа¶Я а¶Єа¶ња¶Яа¶ња¶ЬаІЗථа¶ХаІЗ ටඌа¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІАටගа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶ЊаІЯа¶Њ බаІЗа¶Ца¶Њ ඀ඌථаІНа¶°а¶Ња¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Ња¶≤а¶њ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶∞аІЗа¶Єа¶ња¶ЄаІНа¶Я а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЪගථаІНටඌвАЩа•§ а¶ХඕඌаІЯ а¶ѓаІБа¶ХаІНටග а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ ටඌа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶У а¶ђаІЬ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶ЗථаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ ථගаІЯаІЗ а¶Па¶ХаІЛа¶∞ ථаІАа¶∞а¶ђа¶§а¶Ња•§ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЬаІБа¶ЬаІБ а¶Жа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶Па¶ХаІЛ а¶Ха¶њ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶ЗථаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ගඁබаІЗа¶∞¬† а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶У а¶Рටගයඌඪගа¶Х ථаІНа¶ѓа¶Ња¶ѓаІНඃටඌ ථගаІЯаІЗ а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗථ а¶Ха¶ЦථаІЛ?
а¶Ьඌථග а¶®а¶Ња•§ බගථаІЗа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶Па¶ХаІЛ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ගаІЯඌථ а¶ЪගථаІНටඌඐගබаІЗа¶∞ а¶ЄаІАඁඌඐබаІН඲ටඌ ථගаІЯаІЗа¶З а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ха¶∞аІЗථ, а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶З ටඌа¶∞ ඃඕඌа¶∞аІНඕටඌ, а¶ЃаІЗа¶З а¶ђа¶њ а¶ЄаІМථаІНබа¶∞аІНа¶ѓа¶У! а¶Ж඙ඌටට а¶≤а¶ња¶ХаІБа¶За¶° а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶ња¶∞ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ, ඙аІНа¶∞а¶ђа¶£а¶§а¶Њ, а¶ЄаІЗа¶≤а¶ЂаІЛථ, а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞, а¶Йа¶ЗථаІНа¶°аІЛа¶Ь а¶≠а¶ња¶ЄаІНටඌ, а¶ЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ථаІЗа¶Я, ඙а¶∞аІНථ, а¶Ьа¶ња¶Єа¶Ња¶Є, а¶ђа¶З, а¶°а¶ња¶Ьа¶ња¶Яа¶Ња¶≤ а¶Ѓа¶ња¶°а¶њаІЯа¶Њ, а¶Ѓа¶ња¶Є а¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶≤аІНа¶°, ඙а¶≤а¶ња¶Яа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶ХаІНа¶ЯථаІЗа¶Є, а¶ХаІЛа¶ХаІЗа¶Зථ, ඙аІЛ඙, ථඐаІНа¶ѓ ථඌаІОඪගඐඌබ, а¶ЗථаІНа¶ЯаІЗа¶≤а¶ња¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶°а¶ња¶Ьа¶Ња¶Зථ, ඙аІЗථධаІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠, а¶Жа¶За¶ЂаІЛථ, а¶≠аІЛа¶Ч, а¶Па¶≠аІЛа¶≤аІНа¶ѓаІБපථ, а¶Жа¶Ча¶Ња¶ЃаІЗථථ, а¶ђаІБප а¶ЗටаІНඃඌබග- а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ථගаІЯаІЗа¶З ඙аІЬа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶Х а¶ЕථаІБඐඌබа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња•§
ප඀ගа¶Йа¶≤ а¶ЬаІЯ
බаІНа¶ѓа¶Њ а¶≤а¶ња¶ХаІБа¶За¶° а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶њ (аІ®аІ¶аІІаІЂ)
вАШа¶≤а¶ња¶ХаІБа¶За¶°вАЩ а¶Ѓа¶°а¶Ња¶∞аІНථගа¶Яа¶њ а¶ђа¶Њ а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶њ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶ХаІНටඌ а¶Ьа¶ња¶Ча¶ЃаІБථаІНа¶Я а¶ђа¶Ња¶Йа¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶®а•§ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Па¶З а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ ථඌථඌබගа¶Х ථගаІЯаІЗ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ а¶Жа¶ЧаІНа¶∞а¶єаІА, ටඌа¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶Йа¶ЃаІНඃඌථ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶∞аІНබථගа¶∞ вАШа¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶За¶Я а¶Еа¶Ђ а¶ХаІНа¶∞а¶Ња¶За¶Єа¶ња¶ЄвА٠඙аІЬаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Йа¶ХаІНට а¶≤аІЗа¶Ца¶ЊаІЯ а¶ђа¶Ња¶Йа¶ЃаІНඃඌථ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶≤аІЛ а¶ђа¶∞аІНබථග а¶Па¶З а¶≠а¶Ња¶ђ а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞ ථඌථඌ බගа¶Х ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶≤ඌ඙ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа¶®а•§
а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, а¶ЙටаІНටа¶∞а¶Ња¶ІаІБථගа¶Хටඌ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗа¶З а¶≤а¶ња¶ХаІБа¶За¶° а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶њ а¶ЧආථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶Яа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЛа•§ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶Ња¶ІаІБථගа¶Хටඌ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІНඃඌ඙а¶Х а¶Яа¶Ња¶∞аІНа¶Ѓ- а¶ЄаІНඕඌ඙ටаІНа¶ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ බа¶∞аІНපථ, ඪඌයගටаІНа¶ѓ а¶Єа¶ђ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Ша¶Яථඌ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђаІБа¶Эа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶З а¶Яа¶Ња¶∞аІНа¶Ѓа¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶Ња¶ІаІБථගа¶Хටඌа¶З ඙аІНа¶∞ඕඁ вАШа¶ЧаІНа¶∞аІНඃඌථаІНа¶° ථаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Яа¶ња¶≠вАЩ а¶Па¶∞ а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я а¶Ъа¶ња¶єаІНථගට а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤аІЛа•§ ටඌබаІЗа¶∞ ඁටаІЗ, ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЧаІНа¶∞аІНඃඌථаІНа¶° ථаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Яа¶ња¶≠аІЗа¶∞ а¶Эа¶Ња¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ а¶єа¶За¶≤аІЛ а¶Па¶∞а¶Њ а¶Па¶Ха¶З а¶Ѓа¶°аІЗа¶≤ බගаІЯа¶Њ ඙аІБа¶∞а¶Њ බаІБථගаІЯа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶ЕටаІАටаІЗа¶∞ ඙аІБථа¶∞аІНа¶ђа¶ња¶ђаІЗа¶ЪථඌаІЯ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶Ња¶ІаІБථගа¶ХටඌаІЯ а¶Па¶Х а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶ЗаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Хග඙аІНа¶∞а¶ђа¶£ а¶ЄаІНа¶ђа¶ђа¶ња¶∞аІЛа¶ІаІАටඌ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х, а¶ѓа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ ථගයගа¶≤а¶ња¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶Х ඙аІНа¶∞а¶ђа¶£а¶§а¶Ња¶∞а¶У а¶Ѓа¶ња¶≤ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶Еа¶ЃаІВа¶≤а¶Х а¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶∞аІНබගථගа¶∞ ඁටаІЗ, а¶ЙටаІНටа¶∞а¶Ња¶ІаІБථගа¶Хටඌа¶У ටඌа¶∞ පаІЗа¶Ј а¶Жа¶Ѓа¶≤аІЗ ඙аІМа¶Ыа¶Ња¶За¶ЫаІЗа•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶П а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ХаІНа¶Ја¶£а¶ЄаІНඕඌаІЯаІА, а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗа¶З а¶ЄаІЗ ඐගබඌаІЯ ථගаІЯаІЗ ථගа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶Цථ а¶ѓаІЗඁථ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞а¶њ-а¶∞аІЛа¶ЃаІНඃඌථаІНа¶Яа¶ња¶Єа¶ња¶Ьа¶ЃаІЗа¶∞ ඙ඌආ ථаІЗа¶З, а¶Па¶Ха¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶Ња¶ІаІБථගа¶Хටඌа¶∞а¶У ඙ඌආ ථаІЗаІЯа¶Њ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Хටඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗа¶∞ ථඌඁයаІАථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶Жа¶За¶Єа¶Њ ඙аІМа¶Ба¶ЫඌථаІЛа¶∞ а¶Ша¶Яථඌа¶ХаІЗ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶З а¶ЙටаІНටа¶∞а¶Ња¶ІаІБථගа¶Хටඌа¶∞ а¶Еа¶ђа¶¶а¶Ња¶®а•§
а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я බаІЗа¶Ца¶Њ බගа¶ЫаІЗ, а¶ђа¶Ња¶Йа¶ЃаІНඃඌථаІЗа¶∞ ඁටаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ђа¶ЊаІЬථаІНට а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНඃටඁ а¶ђаІИපගඣаІНа¶ЯаІНа¶ѓа¶Г а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ පа¶ХаІНටගа¶ХаІЗ а¶ЃаІЛа¶Ха¶Ња¶ђаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶Ьඌටගа¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථ а¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶°а¶Ѓ а¶Ха¶њ а¶Жа¶ЫаІЗ? а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗа¶Ыа¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ча¶ЊаІЯаІЗа¶ђ а¶єаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ а¶ЃаІЛа¶Ха¶Ња¶ђаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞ а¶єаІЛа¶ЃаІЛа¶ЬගථගаІЯа¶Ња¶Є а¶Па¶Х ටа¶∞а¶ња¶Ха¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ – а¶Па¶З а¶єаІЛа¶ЃаІЛа¶ЬගථගаІЯаІЗа¶Яа¶ња¶З а¶Жа¶∞ ඕඌа¶ХටаІЗа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§а¶Па¶З а¶Єа¶Ва¶Ха¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Жබа¶∞аІНපа¶У а¶Ча¶ЊаІЯаІЗа¶ђ, а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х බа¶≤а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶У ථඌа¶За•§ а¶Ђа¶≤аІЗ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІЗа¶∞ ටඌа¶ЧගබаІЗ а¶ХаІЛථа¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Па¶ХඌටаІНථ а¶ђаІЛа¶І а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Жа¶єаІНඐඌථа¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶У ථඌа¶За•§
а¶Ха¶ЃаІНа¶ѓаІБථගа¶ЯගටаІЗ а¶Па¶З а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶≤а¶Ња¶Ча¶Ња¶Ѓа¶єаІАථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞а¶ња¶Хටඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓ බගа¶ЫаІЗа¶Г а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьථ а¶Па¶Цථ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶ЂаІЗа¶≤аІЛ а¶Єа¶ња¶Яа¶ња¶ЬаІЗථ ථඌ а¶≠а¶Ња¶За¶ђа¶Њ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඐග඙а¶∞аІАට඙а¶ХаІНа¶Ја•§ а¶Па¶З вАШа¶Єа¶Ња¶ђаІНа¶ЬаІЗа¶ХаІНа¶Яа¶ња¶≠а¶ња¶Ьа¶ЃвАЩ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Хටඌа¶∞ а¶≠ගටаІНටග а¶Хඌ඙ඌаІЯа¶Њ බගටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Па¶∞аІЗ а¶≠а¶ЩаІНа¶ЧаІБа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤а¶ЫаІЗа•§ а¶Пඁථ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶ХаІЛථ ථа¶Ьа¶ња¶∞ ථඌа¶З а¶ѓаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶∞аІЗа¶Ђа¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶ЄаІЗ а¶ЬаІБටаІЗа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Па¶Ха¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ටඌа¶∞а¶≤аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞аІЗ а¶≤аІБ඙аІНට а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶ЗථаІЗа¶∞ ථගපаІНа¶ЪаІЯටඌ ථඌа¶З, а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞а¶ђа¶ња¶≠а¶Ња¶Ч පටаІНа¶∞аІБа•§ а¶Ђа¶≤аІЗ, а¶ѓаІЗа¶З а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶∞ ථа¶Ьа¶ња¶∞ ථඌа¶З, ටඌа¶∞ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶Й඙ඌаІЯ – ථගа¶ЬаІЗа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗа¶ХаІЛථаІЛ а¶ЃаІВа¶≤аІНа¶ѓаІЗ බаІГපаІНඃඁඌථ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤а¶Ња•§ а¶Па¶З බаІГපаІНඃඁඌථ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶З а¶Па¶Цථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤аІНа¶ѓа¶ђаІЛа¶І, ඪඌඕаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶≠аІЛа¶Ча¶ђа¶Ња¶¶а•§ а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Б, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ха¶Ња¶ЩаІНа¶ХаІНඣගට а¶ђа¶ЄаІНටаІБ а¶≠аІЛа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗ ටаІГ඙аІНට ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Па¶З а¶≠аІЛа¶ЧඐඌබаІЗа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓ ථඌ, а¶Па¶З а¶≠аІЛа¶ЧඐඌබаІЗа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓ а¶Ъа¶Ња¶ЗටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶≠аІЛа¶Ча¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටаІЗа¶З ඙аІБа¶∞ඌථаІЛ ඐඌථඌаІЯа¶Њ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Ња•§ ඁඌථаІБа¶Ја¶Ьථ а¶Па¶Х а¶≠аІЛа¶Ч ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Х а¶≠аІЛа¶ЧаІЗ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓа¶єаІАථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶ња¶Ъа¶∞а¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ѓаІЗථ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ђаІБа¶≤а¶ња¶Ѓа¶њаІЯа¶ЊаІЯ а¶Жа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНටа¶Г ථටаІБථ а¶ЄаІЗа¶≤а¶ЂаІЛථа¶Яа¶Њ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞а¶Яа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ ථඌ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞а¶Яа¶Њ а¶ЂаІЗа¶За¶≤а¶Њ බගටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶≠аІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІБа¶Іа¶Њ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶єаІЛа¶Х а¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ња¶ЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§
а¶Жබа¶∞аІНප а¶Жа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х බа¶≤аІЗа¶∞ ඙ටථа¶Г а¶Па¶Цථ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯа¶Њ ඕඌа¶ХаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х බа¶≤а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶≠аІЛа¶Я а¶ХථаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЛа¶≤а¶ња¶В а¶Ѓа¶ђ а¶≤а¶ња¶°а¶Ња¶∞ а¶Еඕඐඌ а¶Ѓа¶Ња¶Ђа¶њаІЯа¶Њ ඐඪබаІЗа¶∞ а¶≠а¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ¬† а¶ЯаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Єа¶ња¶∞ ඁටаІЛа•§ а¶ХаІЗ а¶ХаІА а¶Еа¶Ђа¶Ња¶∞ බගටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ බаІЗа¶За¶Ца¶Њ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьථ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЬаІБаІЯа¶Ња¶≤а¶њ ඙ඌа¶∞аІНа¶Яа¶њ а¶ђа¶Ња¶Ыа¶Ња¶З а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІАටගඐගබබаІЗа¶∞ බа¶≤ඐබа¶≤ а¶ХаІЛථ а¶ЄаІНа¶ХаІНඃඌථаІНа¶°а¶Ња¶≤ а¶Ча¶£аІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗ ථඌ а¶ХаІЗа¶Йа•§ පаІБа¶ІаІБ ඁඌථаІБа¶Ја¶Ьථ ථඌа¶Г а¶Па¶З а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶њ ථගа¶ЬаІЗа¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථගа¶∞ඌ඙ටаІНටඌයаІАථටඌа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞ බගаІЯаІЗ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶Па¶З බаІНа¶∞а¶ђаІАа¶≠аІВටа¶Ха¶∞а¶£ а¶ХаІА බගаІЯа¶Њ а¶∞ග඙аІНа¶≤аІЗа¶За¶Є а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ? а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Па¶ЦථаІЛ а¶Ьඌථග ථඌ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶З а¶Еа¶∞а¶Ња¶Ьа¶Хටඌ а¶Жа¶∞а¶У а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤а¶ђаІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶Йа¶ЃаІНඃඌථаІЗа¶∞ ඁටаІЗ, а¶Па¶З а¶Еа¶∞а¶Ња¶Ьа¶Хටඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶ђаІИපගඣаІНа¶ЯаІНа¶ѓ а¶єа¶≤аІЛ а¶ѓа¶Цථ а¶Й඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ, а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ, ඐග඙аІНа¶≤а¶ђ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶ЄаІНඕඌ а¶Йа¶Зආඌ а¶ѓа¶ЊаІЯ, ටа¶Цථ а¶ѓа¶Њ ඕඌа¶ХаІЗ ටඌ а¶єа¶За¶≤аІЛ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠а•§ а¶Па¶З а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠ а¶ЬඌථаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ХаІА а¶Ъа¶ЊаІЯ ථඌ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІЗ а¶ЬඌථаІЗ ථඌ а¶ЄаІЗ а¶ХаІА а¶Ъа¶ЊаІЯа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Хඕඌ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞а¶Њ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ – а¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Х а¶ђаІНа¶≤а¶Х ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶Я ථගаІЯаІЗ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Хඁථ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶єа¶За¶≤аІЛ а¶ѓаІЗ, а¶ЕаІНඃඌථඌа¶∞аІНа¶Ха¶ња¶ЄаІНа¶Я, а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶ЄаІНа¶Я а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶∞аІЗа¶° а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЧаІЗа¶°аІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶ПබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶ХаІЛථ а¶≤аІЗа¶ђаІЗа¶≤аІЗ а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶З а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶єаІБа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ ඪඌඁථаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ХаІЗа¶Й а¶ЬඌථаІЗ ථඌ а¶Ха¶Цථ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗ, а¶ХаІЛථබගа¶Х බගаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗа•§ а¶Пඁථ а¶ХаІА а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ ටඌа¶∞а¶Ња¶У а¶Жа¶Ча¶Ња¶Ѓ а¶ХаІЛථ බගපඌ ඙ඌаІЯ а¶®а¶Ња•§
а¶Па¶З බаІНа¶∞а¶ђаІАа¶≠ඐථаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ђаІЛа¶Эඌ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථ а¶Й඙ඌаІЯ а¶ХаІА а¶Жа¶ЫаІЗ? а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶єа¶За¶≤аІЛ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЪаІЗටථ а¶єа¶ЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶ѓаІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≤а¶ња¶ХаІБа¶За¶° а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶ЯගටаІЗ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞ටаІЗа¶Ыа¶њ – а¶ѓа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶ЙаІОа¶∞ඌථаІЛа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ ථටаІБථ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶ЗථаІНа¶Єа¶ЯаІНа¶∞аІБа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Эа¶Ња¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ а¶єа¶За¶≤аІЛ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІАටගඐගබ а¶Жа¶∞ а¶ђаІБබаІНа¶Іа¶ња¶ЬаІАа¶ђаІАබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІЬ а¶Еа¶Вප а¶Па¶ЦථаІЛ а¶Па¶За¶Яа¶Ња¶∞ ටඌаІО඙а¶∞аІНа¶ѓ а¶ђаІБа¶ЭаІЗ а¶ЙආටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ථඌа¶За•§ а¶Па¶З а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶ђа¶Ња¶Йа¶ЃаІНඃඌථ а¶Па¶ЦථаІЛ, вАШථගඣаІН඙аІНа¶∞а¶Ња¶£ ඙аІНа¶∞ඌථаІНටаІЗ а¶ХඌථටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶£аІНආඪаІНа¶ђа¶∞вАЩа•§
а¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶ХаІНඃඌඕа¶≤а¶ња¶Х а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶Ха¶Іа¶Ња¶∞аІНа¶Ѓа¶ња¶Х а¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞а¶ња¶ЄаІНа¶Я (аІ®аІ¶аІ¶аІ¶)
а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьථ а¶ѓа¶Цථ а¶ђа¶ња¶Вප පටඌඐаІНබаІАа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶За¶Я а¶ЄаІН඙ගа¶∞а¶ња¶ЪаІБаІЯа¶Ња¶≤ а¶ЯаІНа¶∞ඌථаІНа¶Єа¶Ђа¶∞аІНа¶ЃаІЗපථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ, ආගа¶Х ඙а¶∞аІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටаІЗа¶З ටඌа¶∞а¶Њ а¶Еа¶ђа¶Іа¶Ња¶∞ගටа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Жබа¶∞аІНපаІЗа¶∞ ඙ටථ ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶≤ඌ඙ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶Па¶З а¶ЄаІН඙ගа¶∞а¶ња¶ЪаІБаІЯа¶Ња¶≤ а¶ЯаІНа¶∞ඌථаІНа¶Єа¶Ђа¶∞аІНа¶ЃаІЗපථа¶ХаІЗа¶З а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ђа¶ња¶Вප පටඌඐаІНබаІАа¶∞ ඪඁඌ඙аІНටගа¶∞ ථගබа¶∞аІНа¶ґа¶®а•§ а¶Па¶∞ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶ЯаІНа¶∞аІНඃඌධගපථඌа¶≤ ධඌථ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞аІНඕа¶ХаІНа¶ѓ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶Еа¶ЄаІН඙ඣаІНа¶Я а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗа¶У ඙аІНа¶∞පаІНථ ඕඌа¶ХаІЗ, а¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶≤ගථ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤ а¶≠а¶Ња¶Ща¶Њ а¶ХаІА а¶Па¶З а¶Жබа¶∞аІНපගа¶Х ඙ටථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ථඌ а¶ХаІА පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ а¶Ђа¶≤а¶Ња¶Ђа¶≤а•§
а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌа¶З а¶Іа¶∞аІЗа¶®а•§ ඁඌථаІБа¶Ја¶Ьථ а¶Ъа¶Ња¶ЗටаІЛ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶єа¶ђаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථගа¶∞඙аІЗа¶ХаІНа¶Ј а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Њ а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ а¶≤а¶ња¶ђа¶∞а¶Ња¶≤ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЛපаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЄаІНа¶Я බаІБа¶З ඙а¶ХаІНа¶Ја¶З ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Цඌටගа¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Зථඌ ථගඐаІЗа¶Г ඙ඌа¶∞аІНඕа¶ХаІНа¶ѓа¶Яа¶Њ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗ පаІБа¶ІаІБ¬† а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶∞аІНඕаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЧаІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶≤ඌථа¶Яа¶Њ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ца¶Ња¶Єа¶Њ аІІаІЃаІ™аІЃ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ вАШа¶Ха¶Ѓа¶ња¶ЙථගඪаІНа¶Я а¶ЃаІНа¶ѓаІЗථග඀аІЗа¶ЄаІНа¶ЯаІЛвАЩа¶∞ а¶ЪගථаІНටඌ, а¶ѓаІЗа¶За¶ЦඌථаІЗ ඙аІБа¶Ба¶ЬගඐඌබаІАබаІЗа¶∞ а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЧаІБа¶£а¶ХаІАа¶∞аІНටථ а¶Ча¶ЊаІЯа¶Њ පаІЗа¶Ја¶ЃаІЗප а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єа¶За¶Ыа¶ња¶≤, вАШа¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а¶У а¶Па¶Цථ а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶Ъа¶Ња¶ЗвАЩа•§ а¶≤а¶ња¶ђа¶∞а¶Ња¶≤ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ђаІБа¶Эටඌඁ а¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ѓаІБа¶ХаІНටගа¶Х а¶ЙаІОа¶Ха¶∞аІНа¶ЈаІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗ, а¶Жа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯඌපаІАа¶≤а¶∞а¶Њ а¶РටගයаІНа¶ѓ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶≤аІБඣටඌඁаІБа¶ХаІНට ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගටаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗа•§ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ ¬†вАШа¶∞а¶ња¶≠аІЛа¶≤аІНа¶ѓаІБපථ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Х а¶ЯаІБ බඌ ඙ඌඪаІНа¶ЯвАЩа•§ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ђа¶£а¶§а¶Њ а¶≤а¶Ња¶°а¶Ња¶За¶ЯබаІЗа¶∞ ඁටаІЛ, а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЃаІЗපගථඌа¶∞а¶њ а¶≠а¶Ња¶Ща¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶У ටඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶ЪගථаІНටගට а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶≤а¶ња¶ђа¶∞а¶Ња¶≤ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЛපаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЄаІНа¶ЯබаІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞аІНඕа¶ХаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶ШаІБа¶Ъа¶ЊаІЯа¶Њ බаІЗаІЯа¶Ња¶∞ а¶єа¶ња¶ЃаІНඁටа¶У ටඌа¶∞а¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ථඌа¶За•§
ටаІЛ, а¶Па¶З а¶Ха¶ња¶Єа¶ња¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠аІЗබа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ а¶Іа¶∞аІЗ ඙аІЬа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ аІІаІѓаІђаІЃ а¶Єа¶Ња¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶Єа¶ЃаІЯа¶Яа¶Њ а¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ගථඐඌබаІАබаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЕථаІБа¶∞а¶Ња¶Ч, а¶ЂаІНа¶≤а¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙ඌа¶УаІЯа¶Ња¶∞, පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Хඐඌබ (а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Еа¶ЯаІЛа¶ЃаІЗපථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶Пඁ඙аІНа¶≤аІЯа¶ЃаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶За¶Ѓа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ) а¶Жа¶∞ ධථ а¶єаІБаІЯඌථаІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶Ча¶ЄаІЗа¶∞ ඕаІНа¶∞аІБටаІЗ а¶ЃаІБа¶ХаІНටගа¶∞ ථඐගබаІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶ња¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗඁගපаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Ђа¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶За¶Я а¶Жа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶∞ а¶≤аІЗа¶Ђа¶Я බаІБа¶Зබගа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗа¶З ටаІГටаІАаІЯ ඐගපаІНа¶ђаІЗа¶∞ ඙඙аІБа¶≤а¶ња¶Ьа¶Ѓ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ша¶Яථඌ а¶єаІЯаІЗ බඌа¶БаІЬа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶Па¶З а¶Ѓа¶ња¶≤ඁගපаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶Яа¶Ња¶У а¶≠а¶Ња¶За¶ЩаІНа¶Ча¶Њ ඙аІЬටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Па¶Цථ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶єаІБа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗа¶Ыа¶њ а¶Єа¶њаІЯа¶Ња¶Яа¶≤ а¶ЃаІБа¶≠а¶ЃаІЗථаІНа¶ЯаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ – а¶ѓаІЗа¶За¶ЦඌථаІЗ ථඐаІНа¶ѓ а¶≤а¶Ња¶°а¶Ња¶За¶Я, а¶∞вАНаІНа¶ѓа¶Ња¶°а¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපඐඌබаІА, ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІНටථ පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶ХඐඌබаІА, а¶≤аІБа¶ЃаІН඙аІЗථපаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Х а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶Па¶ХටаІНа¶∞ а¶єаІЯа¶Њ а¶ХаІНа¶≤аІЛථගа¶В, а¶ђа¶ња¶Ч а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶Х, а¶ЯаІНа¶∞аІНඃඌථаІНа¶Єа¶ЬаІЗථගа¶Х а¶Жа¶∞ ථගа¶Йа¶ХаІНа¶≤а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЯаІЗа¶Хථа¶≤а¶Ьа¶ња¶∞ ඐග඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථ ථගටаІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶∞аІВ඙ඌථаІНටа¶∞ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞ බаІБථගаІЯа¶Ња¶∞ а¶≠ගටа¶∞аІЗа•§ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЗටගයඌඪаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ьа¶Ња¶Зථඌ а¶Жа¶Єа¶Ыа¶њ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶ЄаІЗ а¶ЕඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є, а¶За¶єа¶≤аІМа¶Ха¶ња¶Хටඌ а¶Еа¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞, ඁටඐඌබаІЗа¶∞ а¶ЧаІЛа¶БаІЬа¶Ња¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶Еа¶ђа¶ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗබаІНа¶ѓа•§ а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞ ඐගපаІНа¶ђ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ а¶∞аІВ඙ඌථаІНටа¶∞, ථаІИටගа¶Х а¶Ѓа¶Ња¶®а¶¶а¶£аІНа¶°аІЗа¶∞ ථඁථаІАаІЯටඌ, вАШа¶Е඙а¶∞вАЩ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ а¶Жа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶ЪගථаІНටඌඐа¶≤аІАа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶ЖපඌඐаІНа¶ѓа¶ЮаІНа¶Ьа¶Х බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ ථගаІЯаІЗ ටඌа¶Ха¶ЊаІЯа¶Њ ඕඌа¶ХаІЗ а¶Єа¶ђа¶Єа¶ЃаІЯа•§
а¶ЕඐපаІНа¶ѓа¶З, ටаІЗаІЯа¶Ња¶∞ බаІЗ පඌа¶∞බඌථаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶∞а¶Ња¶У а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ вАШа¶За¶єа¶Ьа¶Ња¶Чටගа¶Х а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐටඌвА٠ථගаІЯаІЗ ඁඌඕඌ а¶Ша¶Ња¶Ѓа¶Ња¶ЗටаІЛ а¶Жа¶∞ а¶Зටගයඌඪ඙ඌආа¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЛ ඙а¶∞ගටаІНа¶∞ඌටඌ යගපඌඐаІЗа•§ а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ, а¶Еа¶ЧаІБථටග а¶Єа¶∞аІНඐථඌපඌ а¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶£а¶ња¶ХаІЗа¶∞ а¶ЪගථаІНටඌа¶У ඁඌඕඌаІЯ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Уа¶∞а¶УаІЯаІЗа¶≤ а¶Жа¶∞ а¶єа¶Ња¶ХаІНа¶Єа¶≤а¶ња¶∞ ථаІЗа¶ЧаІЗа¶Яа¶ња¶≠ а¶За¶Йа¶ЯаІЛ඙ගаІЯа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶ЊаІЯа¶Њ බаІЗаІЯа•§ а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶ЊаІЯа¶Њ බаІЗаІЯ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНඃටаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ, а¶ѓаІЗа¶З а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНඃට а¶єа¶ђаІЗ а¶ђаІАа¶≠аІОа¶Є а¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶Х а¶∞вАНаІНඃඌපථඌа¶≤а¶ња¶Яа¶њ බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ ථගаІЯථаІНටаІНа¶∞а¶ња¶§а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ђаІЗපගа¶∞а¶≠а¶Ња¶Ч а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶Па¶За¶Яа¶Ња¶З а¶ЃаІЛа¶Яа¶Ња¶ЃаІБа¶Яа¶њ ඪටаІНа¶ѓ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓаІЗ, а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ පаІЗа¶Ј а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶°а¶Ња¶Ха¶ђаІЗ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞а¶ња¶Ьа¶Ѓ а¶Ча¶Ња¶ђаІЗ а¶≤аІЛа¶ХаІЛа¶ЃаІЛа¶Яа¶ња¶≠аІЗа¶∞ а¶ЄаІНටаІЛටаІНа¶∞а¶ЧаІАа¶§а•§
а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞ටගа¶Ха¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ЕටаІНа¶ѓаІБаІОа¶Єа¶Ња¶єаІА ටа¶∞аІБа¶£ ඙аІЛ඙а¶≠а¶ХаІНට බа¶≤а¶ђа¶≤аІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶єа¶ња¶Йа¶Ь а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ђаІЗප а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶За¶ЩаІНа¶Чගට බගටаІЗа¶ЫаІЗ ඙аІЛ඙ а¶Ьථ ඙а¶≤ බаІБа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЪаІЗа¶За¶ЮаІНа¶Ь а¶єа¶За¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З а¶ЫаІЛа¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ බа¶≤ а¶ХаІНඃඌඕа¶≤а¶ња¶Х ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІА, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІОа¶Ха¶Ња¶∞ පаІБථаІЗ ඁථаІЗ а¶єа¶За¶≤аІЛ ඐඌටගа¶Ха¶ЧаІНа¶∞а¶ЄаІНට а¶ЃаІМа¶≤ඐඌබග а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶ѓа¶Њ а¶ђаІБа¶Эа¶ЊаІЯ, а¶Па¶∞а¶Њ ටඌ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶З а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶З බа¶≤ ඐගඐඌය඙аІВа¶∞аІНа¶ђ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х, а¶Ча¶∞аІНа¶≠ථගа¶∞аІЛа¶Іа¶Х, а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђа¶ња¶В а¶Пඁථ а¶ХаІА а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶Ча¶Є ථගаІЯаІЗа¶У ථටаІБථ а¶ђаІЛа¶Эඌ඙аІЬа¶ЊаІЯ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯа•§ а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ, а¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞ බаІБථගаІЯа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Хඌථ – а¶Па¶∞а¶Њ а¶ШаІНඃඌථඌа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ පඐаІНබබаІВа¶Ја¶£ а¶Жа¶∞ ථගа¶Й а¶Па¶За¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЄаІН඙ගа¶∞а¶ња¶Я ථගаІЯаІЗа•§ а¶Па¶З а¶ЄаІН඙ගа¶∞а¶ња¶Я а¶Па¶Х а¶Хඌටඌа¶∞аІЗ බඌаІЬа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ЊаІЯа¶Њ බගටаІЗа¶ЫаІЗ ථඐаІНа¶ѓ-ඐග඙аІНа¶≤а¶ђаІА, ඁථඪගථගа¶Уа¶∞ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶∞ а¶Ђа¶≤аІЛаІЯа¶Ња¶∞ а¶Па¶ђа¶В а¶≠аІЛа¶Ча¶ђа¶ња¶≤а¶Ња¶ЄаІЗ а¶°аІБа¶За¶ђа¶Њ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶≤аІЛа¶Ха¶ЬථබаІЗа¶∞, а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Уа¶∞а¶њаІЯаІЗථаІНа¶Яа¶Ња¶≤ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶Ња¶Ь ථගටаІЗ а¶ЬаІАඐථ а¶ЙаІОа¶Єа¶∞аІНа¶Ч а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶Па¶Яа¶Њ ටаІЛ ඁඌටаІНа¶∞ පаІБа¶∞аІБаІЯа¶Ња¶¶а•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ЬаІБබаІЗ а¶Жа¶∞а¶У а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З බаІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ а¶Жа¶ЫаІЗа•§
а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ පаІЗа¶ХаІЬаІЗа¶∞ а¶ЦаІЛа¶Ба¶ЬаІЗ (аІ®аІ¶аІ¶аІ©)¬†
а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ පаІЗа¶ХаІЬаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІАаІЯ а¶Єа¶Вඐග඲ඌථаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶Яඌථඌ а¶єа¶ђаІЗ а¶ХаІА ථඌ вАУа¶Па¶З а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶ѓаІЛа¶ЧаІНඃටඌа¶∞ ඐගටа¶∞аІНа¶Х ථගаІЯаІЗ а¶Па¶З а¶ЧаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶ЃаІЗ ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Єа¶∞а¶ђ а¶єаІЯаІЗ а¶Йආа¶ЫаІЗа•§ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьථ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶∞аІЛඁඌථ а¶Єа¶Ња¶ЃаІНа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ ඙ටථаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ යඌට а¶Іа¶∞аІЗа¶З а¶єа¶За¶ЫаІЗ; ටඌ ථඌ а¶єа¶За¶≤аІЗа¶У аІ©аІІаІ© а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Єа¶ЃаІНа¶∞а¶Ња¶Я а¶ХථаІНа¶Єа¶ЯඌථаІНа¶ЯගථаІЗа¶∞ а¶Ђа¶∞ඁඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ටаІЛ а¶ЕඐපаІНа¶ѓа¶За•§ а¶ђаІМබаІНа¶І а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶ѓаІЗඁථ ඙аІВа¶ђаІЗа¶∞ а¶Ьа¶Чට а¶Ха¶≤аІН඙ථඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ථඌ, ටаІЗඁථග а¶ХаІНඃඌඕа¶≤а¶ња¶Х а¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶Ъ, а¶Іа¶∞аІНඁ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ, а¶ЄаІНа¶Ха¶≤а¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶Х а¶Іа¶∞аІНඁටටаІНටаІНа¶ђ а¶Жа¶∞ ඁයඌථ ඪථаІНටබаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ѓа¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶∞ а¶Йබඌයа¶∞а¶£а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶ХаІЗ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ ථඌ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶®а¶Ња•§
ඐග඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьථ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶Ча¶£а¶§а¶®аІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІБථගаІЯඌබаІЗ а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞ ථаІАටගа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶ѓаІБа¶ХаІНටගа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Па¶∞а¶Њ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗථ, а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞а¶ња¶Ьа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Ња¶Яа¶Ња¶З а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞ටගа¶Х а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞, а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЂаІНа¶∞аІЗа¶ЮаІНа¶Ъ ඐග඙аІНа¶≤а¶ђаІЗа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶Ња¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶З а¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞а¶ња¶Ьа¶Ѓа•§ а¶Па¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ ඪථаІНථаІНඃඌඪඐඌබ а¶Еඕඐඌ а¶ЂаІНа¶∞ඌථаІНඪගථа¶Хඌථ а¶РටගයаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶≤аІЗථඌබаІЗථඌ ථඌа¶За•§ ටඌа¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶∞ а¶Ка¶∞аІНа¶ІаІНа¶ђаІЗ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНඃටаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Ха¶ЊаІЯа¶Њ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙а¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶єаІБа¶Ьඌටගа¶Х ඁයඌබаІЗප යගපඌඐаІЗ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආගට а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶®а•§ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ ථටаІБථ а¶ЖඪටаІЗа¶ЫаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗ, ටඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶Ѓа¶ња¶≤ථаІАа¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථа¶Яа¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Іа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ЄаІНට а¶єа¶ђаІЗ ඃබග а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙а¶ХаІЗ а¶Єа¶∞а¶Ња¶Єа¶∞а¶њ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Ха¶ѓаІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶ЕථඌථаІНа¶ѓ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Жа¶∞ а¶РටගයаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ја¶ЬථаІЗа¶∞а¶Ња¶У а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ШаІБ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶Жа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤аІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Хඌටඌа¶∞аІЗ ඙а¶∞аІНඃඐඪගට а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ вАШа¶Па¶Х ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶∞බඌඪаІНට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶За¶≤аІЛ а¶Жа¶∞ а¶ХаІАвА٠ඁථаІЛа¶≠а¶Ња¶ђа¶Яа¶Њ а¶ЦаІБа¶ђа¶З ඙а¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞а•§
а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶З а¶Па¶Яа¶Њ පаІБа¶ІаІБ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶ѓаІБබаІНа¶І ථඌ; а¶Па¶Яа¶Њ а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х ඙аІНа¶∞а¶Ха¶≤аІН඙, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථаІГටඌටаІНටаІНа¶ђа¶ња¶Х බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶≠а¶ЩаІНа¶Ча¶ња•§ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞¬† а¶Жබа¶≤а¶Яа¶Њ а¶ХаІА ටඌа¶∞ а¶Ьථඪа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЕටаІАටаІЗа¶∞ පа¶ХаІНටගа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶≠ගටаІНටග а¶Ха¶∞аІЗ а¶Яඌථඌ а¶єа¶ђаІЗ ථඌ а¶ХаІА а¶Па¶∞ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНඃටаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ පа¶ХаІНටගа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶≠ගටаІНටග а¶Ха¶∞аІЗ а¶Яඌථඌ а¶єа¶ђаІЗ – а¶ЄаІЗа¶З ඪගබаІН඲ඌථаІНටа¶У а¶Па¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ЬаІЬа¶ња¶§а•§
඙аІЗа¶ЫථаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶Ха•§ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶Ха¶њ පаІБа¶ІаІБа¶З а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶Й඙а¶∞ බඌа¶БаІЬа¶ЊаІЯа¶Њ а¶ђа¶ња¶Хපගට а¶єа¶За¶ЫаІЗ? а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶Ча¶£а¶ња¶§а¶ґа¶Ња¶ЄаІНටаІНа¶∞, а¶Жа¶∞а¶ђаІЗа¶∞ а¶Уа¶ЈаІБа¶І а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Ха¶У ඙аІЛа¶≤аІЛа¶∞а¶У а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Жа¶≤аІЗа¶ХаІНඪඌථаІНа¶°а¶Ња¶∞ බаІНа¶ѓа¶Њ а¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶За¶ЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ ඙аІВа¶ђаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶ѓаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶≤а¶Ња¶≠ඐඌථ а¶єа¶За¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶≤а¶Ња¶ЧаІЗ а¶®а¶Ња•§ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶Х а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶З а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶Ьගථගප඙ටаІНа¶∞ а¶Жබඌථ඙аІНа¶∞බඌථ а¶Ха¶∞аІЗ ටඌа¶∞ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞ බඌа¶БаІЬа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ЊаІЯа•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ а¶Па¶Яа¶Њ а¶ђа¶≤а¶Ња¶З ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Я ථඌ а¶ѓаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶∞ට а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶Жа¶∞ඐබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ХаІГටа¶ЬаІНа¶Ю ඕඌа¶ХටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞аІЗа¶Хබගа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІЗа¶Ца¶Ња¶За¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටග а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶Ча¶Ња¶£а¶ња¶§а¶ња¶Х а¶ЄаІНа¶ђа¶∞а¶≤ග඙ගටаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња•§ а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶ХаІЛ-а¶∞аІЛඁඌථ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶Хඕඌ а¶≠аІБа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶Ыа¶ња•§
а¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶ХаІЛ-а¶∞аІЛඁඌථ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶Жа¶Зථ, බඌа¶∞аІНපථගа¶Х а¶ЪගථаІНටඌ а¶Пඁථ а¶ХаІА а¶≤аІЛа¶ХඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶У а¶ЖටаІНа¶Ѓа¶ЄаІНඕ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ඲а¶∞аІНа¶Ѓ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶Чඌථ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ ඁගඕаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З ථගа¶ЫаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ, а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶ЦаІЗаІЯа¶Ња¶≤ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶З а¶ђа¶єаІБ а¶ИපаІНа¶ђа¶∞ඐඌබаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Й඙ඌබඌථ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶Па¶∞ а¶≠ගටа¶∞аІЗа•§ а¶Жа¶∞ а¶∞аІЗථаІЗа¶Єа¶Ња¶Б а¶ѓаІБа¶Ча¶З¬† а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶ѓаІБа¶Ч ථඌ а¶ѓаІЗ а¶ХаІА ථඌ а¶≠аІЗථඌඪ а¶Жа¶∞ а¶ЕаІНඃඌ඙аІЛа¶≤аІЛ බගаІЯаІЗ ආඌඪඌ¬† а¶ХаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶Ха¶Ња¶≤ а¶Ьа¶ЧටаІЗа¶∞ а¶ІаІНа¶ђа¶ВඪඌඐපаІЗа¶Ј а¶Жа¶∞ а¶™а¶Ња¶£аІНа¶°аІБа¶≤ග඙ග а¶ЦаІЛа¶Ба¶ЬаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єа¶За¶ЫаІЗа•§ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶ѓаІБа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Іа¶∞аІНඁටටаІНටаІНа¶ђ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶ња¶ЄаІНа¶Яа¶Яа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЪගථаІНටඌа¶∞ а¶Й඙а¶∞ බඌаІЬа¶ЊаІЯа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞ඐබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ බගаІЯаІЗ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶ЃаІЗ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗа•§ ඙аІНа¶≤аІЗа¶ЯаІЛа¶ХаІЗ ඙ඌටаІНටඌ ථඌ බගа¶≤аІЗа¶У а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІЯ ථඐаІНа¶ѓ-඙аІНа¶≤аІЗа¶ЯаІЛඐඌබа¶ХаІЗ а¶ПаІЬа¶ЊаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ථඌа¶За•§ а¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІЗа¶∞ ඀ඌබඌа¶∞а¶∞а¶Њ ථඐаІНа¶ѓ-඙аІНа¶≤аІЗа¶ЯаІЛඐඌබ බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞а¶≠ඌඐගට а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶ЪගථаІНටඌඐගබබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓ පаІНа¶∞аІЗа¶ЈаІНආ а¶ЪගථаІНටඌඐගබ а¶Еа¶Ча¶Ња¶ЄаІНа¶Яගථа¶ХаІЗ ඙аІНа¶≤аІЗа¶ЯаІЛථගа¶Х а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ха¶≤аІН඙ථඌа¶З а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶Єа¶Ња¶ЃаІНа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Ња¶Яа¶Њ, а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ ඐගඐඌබ а¶Ъа¶≤а¶ЫаІЗ, ඐගඐඌබ а¶Ъа¶≤а¶ЫаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІЗа¶∞- а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЙаІО඙ටаІНටගа¶У а¶∞аІЛа¶Ѓа¶Ња¶®а•§ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЄаІНа¶Яඌථ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶∞аІЛа¶ЃаІЗа¶∞ а¶≤аІНඃඌටගථа¶ХаІЗа¶З ටඌа¶∞ පඌඪаІНටаІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞, а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶ЪගථаІНටඌа¶∞, а¶Жа¶Зථ а¶Жа¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ ඐගටа¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ ඐඌථඌа¶За¶ЫаІЗа•§
а¶За¶єаІБබගබаІЗа¶∞ а¶Па¶ХаІЗපаІНа¶ђа¶∞ඐඌබ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶ХаІЛථ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶РටගයаІНа¶ѓ а¶Ха¶≤аІН඙ථඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶≠ගට а¶ѓаІЗа¶З ඙ඌආаІНа¶ѓ, ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Ыඌ඙а¶Цඌථඌ а¶ѓаІЗа¶З ඙ඌආаІНа¶ѓ а¶Ыඌ඙ඌථаІЛа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ, а¶ѓаІЗа¶З ඙ඌආаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЕථаІБඐඌබ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶Ьа¶Ња¶∞аІНඁඌථ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓ බගа¶ЫаІЗ, а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶ЯаІНඃඌථаІНа¶Я බаІБථගаІЯа¶Ња¶∞ ථаІАටග඙ඌආаІНа¶ѓ – а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶єа¶≤аІЛ а¶ђа¶Ња¶За¶ђаІЗа¶≤а•§ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ බаІБථගаІЯа¶Њ а¶ђаІЬа¶З а¶єа¶За¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ѓ а¶Ча¶ЊаІЯа¶Њ, ථඐаІАබаІЗа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ІаІГටග බගаІЯаІЗ, а¶Ьа¶ђ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶єа¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ІаІНඃඌථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶За¶єаІБබග а¶Па¶ХаІЗපаІНа¶ђа¶∞ඐඌබа¶З а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶Па¶ХаІЗපаІНа¶ђа¶∞ඐඌබ а¶Жа¶∞ а¶За¶Єа¶≤а¶Ња¶Ѓа¶ња¶Х а¶Па¶ХаІЗපаІНа¶ђа¶∞ඐඌබаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ђ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ а¶ЄаІЗටаІБ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ බගа¶ЫаІЗа•§
а¶Па¶ЦඌථаІЗа¶З පаІЗа¶Ј а¶®а¶Ња•§ ඙ගඕඌа¶ЧаІЛа¶∞а¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ඁගපа¶∞аІАаІЯ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶ХаІЛථ а¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶≠а¶Ња¶ђа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ගаІЯ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Ша¶Яථඌа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶єа¶За¶≤аІЛ а¶∞аІЗථаІЗа¶Єа¶Ња¶Б, а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ ඁගපа¶∞аІАаІЯ а¶Жа¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶°а¶њаІЯඌථබаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ බඌаІЬа¶Њ а¶ђаІНඃඌ඙а¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶§а•§ а¶Еа¶ђаІЗа¶≤а¶ња¶ЄаІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶∞а¶єа¶ЄаІНа¶ѓа¶≠аІЗබ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ පаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙а¶≤а¶ња¶Б ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ѓаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඁඌඕඌаІЯ а¶≠а¶Ња¶ЄаІЗ, а¶Єа¶Ња¶ЃаІНа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶Па¶ђа¶В а¶ЦаІБа¶ђа¶З ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶Њ ථටаІБථ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶ЪගථаІНටඌа¶Ха¶≤аІН඙- а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ටаІЛ ථаІЗа¶Ђа¶Ња¶∞ටගටග, ඙ගа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶°аІЗа¶∞ а¶∞а¶єа¶ЄаІНа¶ѓ, а¶Ђа¶Ња¶∞а¶Ња¶УаІЯаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠ගපඌ඙, ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ ඁගපа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЧаІБа¶ђа¶∞аІЗ ඙аІЛа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЦаІЛබඌа¶З ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗа•§
ටаІЛ, а¶Жа¶Ѓа¶њ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶њ а¶Па¶З а¶Єа¶Вඐග඲ඌථаІЗ а¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶ХаІЛ-а¶∞аІЛඁඌථ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶ђа¶Њ а¶За¶єаІБබග-а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Па¶З ඁයඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶Яඌථඌа¶У ඙аІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶ЩаІНа¶Ча¶ња¶Х а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ටඌа¶За•§ а¶∞аІЛа¶Ѓ а¶ѓаІЗඁථ ටඌа¶∞ ඙аІНඃඌථаІНඕගаІЯථ а¶Єа¶ђ а¶ђа¶∞аІНа¶£аІЗа¶∞ а¶ЦаІЛබඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ බගа¶Ыа¶ња¶≤, а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶Ъа¶Ња¶ЃаІЬа¶Ња¶∞ ඁඌථаІБа¶Ја¶ХаІЗа¶У ටඌа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ЃаІНа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЧබගටаІЗ а¶ђа¶Єа¶Ња¶За¶Ыа¶ња¶≤ – а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶≠аІБа¶≤а¶Њ а¶Йа¶Ъගට ථඌ а¶ЄаІЗа¶ЗථаІНа¶Я а¶Еа¶Ча¶Ња¶ЄаІНа¶ЯගථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓ а¶Жа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶ЊаІЯ – а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓ පаІЗа¶ХаІЬаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ а¶Йа¶Ъගට а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ а¶Єа¶ђ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Па¶ђа¶В а¶ЬඌටаІАඪටаІНටඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටаІБට යගපඌඐаІЗ а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња•§ а¶ХаІЗථථඌ, а¶ЙථаІНа¶ЃаІБа¶ХаІНට ඕඌа¶Ха¶Ња¶З а¶Па¶З ඁයඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНඃටඁ ඐගපගඣаІНа¶Я а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶ђаІИපගඣаІНа¶ЯаІНа¶ѓа•§
а¶°аІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓа¶° а¶Ђа¶ња¶≤аІЛа¶Єа¶Ђа¶њ (аІ®аІ¶аІІаІІ)
а¶Ха¶ња¶ЫаІБබගථ а¶Жа¶ЧаІЗ вАШа¶≤а¶Њ а¶∞ග඙ඌඐаІНа¶≤а¶ња¶Ха¶ЊвАЩ а¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶ЂаІЗථ а¶єа¶Ха¶ња¶В а¶Жа¶∞ а¶≤аІЗථඌа¶∞аІНа¶° а¶ЃаІНа¶≤ධගථаІЛа¶∞ вАШබаІНа¶ѓа¶Њ¬† а¶ЧаІНа¶∞аІНඃඌථаІНа¶° а¶°а¶ња¶Ьа¶Ња¶ЗථвАЩ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ча¶Ња¶Ѓ а¶ЕථаІБඐඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶Вප ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶ВපаІЗ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶ЬаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЙබаІНа¶ІаІГට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶Ња¶ђа¶Яа¶Ња¶За¶ЯаІЗа¶≤ а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗ, вАШබа¶∞аІНපථ а¶ЃаІГට, ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Па¶Ха¶Ња¶З ඁයඌඐගපаІНа¶ђ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Єа¶ХаІНа¶Ја¶ЃвАЩа•§ බа¶∞аІНපථаІЗа¶∞ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБ а¶Па¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶У ථඌථඌ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶ђаІЗප а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶За¶ЫаІЗ, а¶ПටаІЗ а¶ђа¶ња¶ЄаІНඁගට а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ථඌа¶За•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶Вපа¶Яа¶Њ ඙аІЬа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඁථаІЗ а¶єа¶За¶Ыа¶ња¶≤ а¶єа¶Ха¶ња¶В а¶ђаІБа¶≤පගа¶Я а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗа•§ вАШа¶≤а¶Њ а¶∞ග඙ඌඐаІНа¶≤а¶ња¶Ха¶ЊвАЩ а¶ѓаІЗ а¶≠аІБа¶≤а¶≠а¶Ња¶≤ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗ ථඌа¶З,¬† а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ЕථаІБඁඌථ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗа¶У ථගපаІНа¶Ъගට а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶ђа¶За¶Яа¶Њ а¶Хගථа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ а¶≠аІБа¶≤ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§
а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≠а¶Ња¶∞аІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶ЃаІНа¶≤ධගථаІЛ а¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Ђа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІНа¶Я-а¶∞аІЗа¶За¶Я ඙඙аІБа¶≤а¶Ња¶∞а¶Ња¶За¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Па¶ђа¶В а¶ђаІЗප а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶П඙ගඪаІЛа¶°аІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ХаІНа¶∞ගථа¶∞а¶Ња¶За¶Яа¶Ња¶∞а¶Уа•§ а¶Па¶Яа¶Њ а¶ђа¶За¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ьа¶Ња¶Ба¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶За¶≤а¶Ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗපථ බаІЗа¶ЦаІЗа¶З а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ыа¶ња•§ ඁථаІЗ а¶єа¶За¶ЫаІЗ а¶За¶≤а¶Ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗපථа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ђа¶Ња¶ЪаІНа¶ЪඌබаІЗа¶∞ а¶ЗаІЯаІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞а¶ЗаІЯа¶Ња¶∞ а¶ПථаІНа¶Єа¶Ња¶За¶ХаІНа¶≤аІЛ඙аІЗа¶°а¶њаІЯа¶Њ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓаІЗ а¶Ха¶∞а¶Њ, а¶ѓаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Ђа¶ња¶Ьа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤-а¶ЃаІНඃඌඕඁаІЗа¶Яа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤-а¶Ха¶Єа¶ЃаІЛа¶≤а¶Ьа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶Й඙඙ඌබаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х ථඌа¶За•§ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට а¶ЄаІВа¶Ъа¶Ња¶≤аІЛ а¶ХඌථаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶ХබаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ බа¶∞аІНපථаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ЧаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶Ча¶Ыа¶ЊаІЯа¶Њ බаІЗаІЯа¶Ња¶Яа¶Њ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§
а¶ђа¶За¶Яа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶За¶ЫаІЗ а¶ЄаІБබаІГаІЭа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Па¶Яа¶Њ බඌඐග а¶Ха¶За¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗ, බа¶∞аІНපථаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІЗපග а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ ථඌа¶З а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶Юඌථа¶З а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ (аІІ) а¶ѓаІЗ බаІБථගаІЯඌටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞а¶њ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ (аІ®) а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටග а¶ХаІА (аІ©) බаІБථගаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ха¶њ а¶ХаІЛථ а¶ЄаІНа¶∞а¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶∞ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ХаІА ථඌ (аІ™) а¶ХаІЛථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ථඌ ඕඌа¶Ха¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ХаІНඃඌථ а¶Жа¶ЫаІЗ¬† (аІЂ) а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ (аІђ) а¶ХаІЗථ а¶ЄаІБථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶Па¶З а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶≤ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ථඌа¶За•§ а¶ѓаІЗඁථ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Єа¶ђа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶З а¶Жබа¶∞аІНප බඌа¶∞аІНපථගа¶Х ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Па¶ђа¶В පаІЗа¶Ј а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞පаІНථаІЗа¶∞ (а¶ѓаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ බа¶∞аІНපථа¶Чට) а¶ЙටаІНටа¶∞ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, а¶ђа¶За¶Яа¶Ња¶∞ а¶Й඙а¶ЬаІАа¶ђаІНа¶ѓ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶За•§
а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Цගට පаІЗа¶Ј а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞පаІНථаІЗа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞ බගටаІЗ а¶єа¶За¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁ බаІБа¶За¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞පаІНථаІЗа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶Ьඌථඌ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а•§ а¶ЕථаІНа¶ѓа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗ, а¶ХаІЛථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ХаІА а¶ђаІБа¶Эа¶ЊаІЯ а¶Па¶ђа¶В බаІБථගаІЯа¶Њ а¶ѓаІЗඁථ- а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ХаІА а¶ЄаІЗа¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З බаІБථගаІЯа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЬඌථටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ? а¶Зටඌа¶≤а¶ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶Ха¶Ња¶ЪаІНа¶ЪඌබаІЗа¶∞ а¶ѓа¶Цථ බа¶∞аІНපථ ඙аІЬඌථаІЛ а¶єаІЯ, ටа¶Цථ ටඌа¶∞а¶Њ පаІБа¶∞аІБа¶З а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶Яа¶Њ බගаІЯаІЗ- а¶ђа¶ЄаІНටаІБа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶≠а¶Ња¶ђа¶ХаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶ЊаІЯа¶Ња¶З а¶Ха¶њ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ පගа¶Ца¶њ? а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶У а¶Ха¶њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Жа¶ЫаІЗ? ථඌ а¶ХаІА а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶ХаІНа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ЄаІЗа¶З ඪටаІНටඌ, а¶Еඕඐඌ ඙ඌа¶ЯථඌඁаІЗа¶∞ вАШа¶ђаІНа¶∞аІЗа¶Зථ а¶Зථ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Њ а¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶Я?вАЩ
а¶Па¶З а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ බаІЗаІЯа¶Њ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ЄаІБථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Яа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ බඌа¶∞аІНපථගа¶Ха•§ ඃබග ටඌ ථඌ а¶єа¶ЗටаІЛ ටඌයа¶≤аІЗ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶Юඌථа¶У а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЛ ථඌ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ХаІЗථ а¶ЬඌථаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶ХаІА а¶ЬඌථаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГට඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ, а¶≤аІЗа¶Ца¶ХබаІНа¶ђаІЯ а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ вАШа¶Ѓа¶°аІЗа¶≤ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐටඌвАЩ а¶Па¶∞ а¶Хඕඌа¶З а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗථ а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ а¶ђа¶≤аІЗ-¬† вАШа¶Ыа¶ђа¶њ-а¶Еඕඐඌ ටටаІНටаІНа¶ђ-а¶єаІАථ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐටඌа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ ඕඌа¶ХටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ථඌвАЩа•§ а¶Па¶ђа¶В вАШа¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Ња¶Чට а¶ХඌආඌඁаІЛ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶єа¶За¶≤аІЗа¶У а¶≠ගථаІНථ а¶≠ගථ ටටаІНටаІНа¶ђ බගаІЯаІЗ а¶Па¶Ха¶З а¶Ша¶Яථඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х ඪථаІНටаІЛа¶Ја¶Ьථа¶Х а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђвАЩа•§ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐටඌ ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Њ а¶ђаІБа¶Эа¶њ, а¶Ьඌථග а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶≤а¶њ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶°аІЗа¶≤ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ѓа¶Њ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථ а¶Ха¶∞аІЗ ටඌа¶∞ а¶Й඙а¶∞а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Њ а¶Ьඌථග а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЗථаІНබаІНа¶∞а¶њаІЯ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶Ја¶Ьඌට а¶Жа¶∞ а¶ђаІНа¶∞аІЗа¶ЗථаІЗа¶∞ а¶Ђа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶¶а¶Ња¶®а•§
а¶Єа¶Ьа¶Ња¶Ч ඙ඌආа¶Х¬† а¶Зටගඁ඲аІНа¶ѓаІЗа¶З а¶ХඌථаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶≠аІВටаІЗа¶∞ බаІЗа¶Ца¶Њ ඙ඌа¶За¶ЫаІЗථ а¶Па¶З а¶Жа¶≤ඌ඙аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶З බаІБа¶З а¶≤аІЗа¶Ца¶ХаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐථඌ, බа¶∞аІНපථаІЗ ටඌа¶∞ ථඌඁ а¶єа¶≤а¶ња¶Ьа¶Ѓа•§ а¶ХаІЗа¶Й а¶Па¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Еа¶≠аІНඃථаІНටа¶∞аІАа¶£ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐඐඌබ, а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Ча¶†а¶®а¶ђа¶Ња¶¶а•§
а¶Пටа¶ХаІНа¶Ја¶£аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ђаІБа¶ЭаІЗ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶њ, а¶Па¶З а¶ђа¶З а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ХаІЛථ ඙බඌа¶∞аІНඕඐаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶Х а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ ථගаІЯаІЗ ථඌ, а¶ђа¶∞а¶В а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ බඌа¶∞аІНපථගа¶Х ඙аІНа¶∞ටаІАටග ථගаІЯаІЗ а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ а¶Йа¶ХаІНට ඙බඌа¶∞аІНඕඐගබаІЗа¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶ХаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕථ а¶Жа¶∞ ථаІНа¶ѓа¶Ња¶ѓаІНඃටඌ බаІЗаІЯа•§ ඪථаІНබаІЗа¶є ථඌа¶З, а¶≤а¶ЊаІЯаІЗа¶Х ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶ЮඌථаІАа¶∞а¶Њ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞ බඌа¶∞аІНපථගа¶Х а¶≠ගටаІНටග ථගаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ ඙ඌඐаІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶Еа¶ђа¶Чට, а¶Жа¶∞ а¶ЃаІНа¶≤ධගථаІЛ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶ХаІЗа¶∞ ඐබаІМа¶≤ටаІЗ а¶ѓаІЗඁථ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ьඌථග, вАШ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьථ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶≠аІЯа¶Ва¶Ха¶∞ а¶Ша¶Яථඌа¶∞ බඌаІЯ а¶Еа¶≤а¶ња¶ЃаІН඙ඌඪаІЗа¶∞ а¶єа¶ња¶Ва¶Єа¶Х а¶Жа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගපаІЛ඲඙а¶∞а¶ЊаІЯа¶£ බаІЗඐටඌබаІЗа¶∞ а¶Ъඌ඙ඌаІЯа¶Њ බගටаІЛвАЩа•§ а¶ђа¶Ња¶З а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶≠аІЗථ а¶ЕаІНඃඌථаІНа¶° а¶ђа¶Ња¶З а¶ЬаІЛа¶≠!
а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶Ѓ а¶Ха¶З а¶ЦаІБа¶Ба¶За¶Ьа¶Њ ඙ඌа¶У? (аІ®аІ¶аІ¶аІ©)
පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ ඪථаІНටаІНа¶∞а¶Ња¶ЄаІА а¶єа¶Ња¶Ѓа¶≤а¶Њ ථඌ, а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞ටගа¶Х а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ ඁටඌඁට а¶Ьа¶∞ග඙ඪය ඙а¶∞඙а¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ша¶Яථඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶Ча¶Яа¶Њ а¶єаІЗа¶°а¶≤а¶Ња¶ЗථаІЗ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ථගа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗа¶≤ පаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ථаІЗа¶∞ ඙а¶≤а¶ња¶Єа¶ња¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІЛа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Єа¶єа¶ЬаІЗ а¶Ъа¶ња¶єаІНථගට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶За¶єаІБබගа¶У а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶За¶Єа¶∞а¶ЊаІЯаІЗа¶≤а¶ђа¶ња¶∞аІЛа¶ІаІА ඁථаІЛа¶≠а¶Ња¶ђ ඙аІЛа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞аІЗ, ඐග඙а¶∞аІАටаІЗ а¶Па¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІН඲ඐඌබаІАබаІЗа¶∞а¶У а¶Па¶Ха¶З а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඁථаІЛа¶≠а¶Ња¶ђ а¶ПබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶§а¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ьථඁට а¶Жа¶∞ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶Є а¶Ѓа¶ња¶°а¶њаІЯа¶Њ а¶ђа¶ња¶ЪගටаІНа¶∞ а¶∞а¶Ха¶ЃаІЗа¶∞ ඐගබаІНа¶ђаІЗа¶Ја¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶З а¶Хඌටඌа¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗа•§ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ,඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Ьථඁට а¶Па¶ЦථаІЛ а¶ЄаІЗа¶З а¶Жа¶∞ඌඁබඌаІЯа¶Х බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶Ча¶∞ගටаІЗ а¶Жа¶Яа¶ХඌථаІЛ- а¶Па¶Х ථඌඁаІНа¶ђа¶Ња¶∞- а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶Ѓ а¶Жа¶∞ඐබаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞, බаІБа¶З-а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ха¶Ѓ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Х а¶ЄаІНа¶ХගථයаІЗа¶°аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶Ѓ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§
а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶Ха¶ЦථаІЛа¶З а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ටඕඌ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ, ඙඙аІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ вАШа¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶ХвАЩ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ђа¶Ња¶∞а¶Ња¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІБа¶За¶Эа¶Њ а¶ЙආටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ථඌа¶За•§ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶Ѓ а¶ЃаІВа¶≤ට ඙඙аІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ බඌаІЯаІА а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶За¶єаІБබаІАа¶∞а¶Њ а¶ИපаІНа¶ђа¶∞-ඐගබаІНа¶ђаІЗа¶ЈаІАа¶Г ¬†а¶Па¶З а¶Еа¶ЬаІБයඌටаІЗ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЃаІЯ а¶ђаІНඃඌ඙а¶Х а¶Ха¶ЪаІБа¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ а¶Ъа¶≤а¶ЫаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞а•§ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ыа¶ња¶≤, ථගа¶∞аІНඐඌඪගට а¶За¶єаІБබගа¶∞а¶Њ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶РටගයаІНа¶ѓ а¶Іа¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ ඐබаІН඲඙а¶∞а¶ња¶Ха¶∞, а¶Єа¶єа¶ЬаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤ටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤аІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶ЕථаІБа¶Єа¶Ња¶∞аІА а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ ටඌබаІЗа¶∞ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ха¶ња¶∞а¶Њ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЛ, а¶Па¶∞а¶Њ а¶≠ගථаІНථ ටа¶∞а¶ња¶Ха¶ЊаІЯ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶≠аІЯа¶Ва¶Ха¶∞ а¶ЗථаІНа¶ЯаІЗа¶≤аІЗа¶Ха¶ЪаІБаІЯа¶Ња¶≤а•§ вАШа¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶ХвАЩ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶Ѓ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђаІБа¶Эа¶Ња¶ЗටаІЗа¶Ыа¶њ а¶Рටගයඌඪගа¶Х а¶Па¶ђа¶В ථаІГටඌටаІНටаІНа¶ђа¶ња¶Х а¶≠а¶Ња¶ђа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶ХаІЗ, а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ а¶За¶єаІБබගа¶ЬඌටаІАа¶∞ ඐග඙а¶∞аІАටаІЗ а¶Жа¶∞аІНа¶ѓа¶Ьඌටගа¶∞ පаІНа¶∞аІЗа¶ЈаІНආටаІНа¶ђ а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ ථаІНа¶ѓа¶Ња¶ѓаІНඃටඌ ඙аІНа¶∞බඌථ а¶Ха¶∞ටаІЛа•§ а¶Па¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ вАШа¶За¶єаІБබගа¶∞а¶Њ а¶ЈаІЬඃථаІНටаІНа¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ බаІБථගаІЯа¶Њ බа¶Ца¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ ථаІЗаІЯа¶Ња¶∞вАЩ – а¶Па¶З а¶∞а¶Ха¶ЃаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа•§а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЂаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶Йආа¶ЫаІЗ вАШබаІНа¶ѓа¶Њ ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЯаІЛа¶Ха¶≤а¶Є а¶Еа¶Ђ බඌ а¶Па¶≤аІНа¶°а¶Ња¶∞а¶Є а¶Еа¶Ђ а¶Ьа¶ЊаІЯථвАЩ а¶ђа¶ЗටаІЗа•§ а¶ђа¶≤ටаІЗ බаІНа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ ථඌа¶З, а¶ђа¶За¶Яа¶Њ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђаІБබаІНа¶Іа¶ња¶ђаІГටаІНටගа¶∞а¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞аІЛа¶°а¶Ња¶ХаІНа¶Яа•§
а¶Жа¶∞а¶ђ ඐගපаІНа¶ђаІЗ а¶Іа¶∞аІНඁටඌටаІНටаІНа¶ђа¶ња¶Х а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶ЃаІЗа¶∞ යබගඪ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ථඌ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ХаІЛа¶∞ඌථ පа¶∞а¶ња¶Ђ а¶Жа¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶єа¶Ња¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ьа¶ња¶Єа¶Ња¶Є ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗа¶З ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶Чට බගа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЕථаІБа¶ЃаІЛබථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶За¶Єа¶≤а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶Жа¶∞ а¶За¶єаІБබගබаІЗа¶∞ බаІНඐගටаІАаІЯ පаІНа¶∞аІЗа¶£аІАа¶∞ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х යගපඌඐаІЗ а¶ЧаІБа¶£а¶≤аІЗа¶У а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓа¶∞ඌටඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶ђаІЗප ඪයථපаІАа¶≤а¶З а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶≤аІЗ а¶За¶єаІБබග-а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථа¶∞а¶Њ а¶ЯаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Є බගаІЯаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඐඪඌ඙ඌටග а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ха¶∞аІНа¶Ѓ ථගа¶∞аІНа¶ђа¶ња¶ШаІНථаІЗ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶ЊаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЛа•§ а¶За¶Єа¶≤а¶Ња¶Ѓа¶ња¶Х а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶Ѓ ටඌа¶З а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶Ча¶∞а¶ња¶∞ ථඌ, а¶Па¶Яа¶Њ ඙аІБа¶∞ඌ඙аІБа¶∞а¶ња¶З а¶Ьඌටග а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Ха•§ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ ඙аІНа¶∞а¶£аІЛබථඌ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶У а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ьа¶Ња¶ЄаІНа¶Я а¶Па¶Х඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඪඌ඙аІЛа¶∞аІНа¶Я බаІЗаІЯ а¶Ьа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа•§ а¶Йථඐගа¶Вප පටඌඐаІНබаІАටаІЗ а¶За¶єаІБබගа¶∞а¶Њ ඃබග а¶За¶Єа¶∞а¶ЊаІЯаІЗа¶≤ а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Яа¶Њ а¶За¶Йа¶ЯඌටаІЗ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌ а¶Ха¶∞ටаІЛ, ටඌයа¶≤аІЗ а¶Жа¶∞а¶ђа¶∞а¶Њ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Х а¶єа¶ЗටаІЛ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ඃඌටаІЗ а¶≠аІБа¶≤ ථඌ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶єаІЯа¶Г а¶Рටගයඌඪගа¶Х а¶Па¶ђа¶В а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶За¶єаІБබගබаІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶ЗථаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ ඐඪටග а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞а•§ а¶Па¶ХපаІЛ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Іа¶∞аІЗ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ පඌථаІНටග඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඐඪටග а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ а¶Па¶ђа¶В ටඌබаІЗа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ ඕඌа¶Ха¶Ња¶∞а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶∞а¶ђ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶Ѓ а¶Жа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶ња¶Х, а¶ХаІЛථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶Іа¶∞аІНඁටඌටаІНටаІНа¶ђа¶ња¶Х а¶®а¶Ња•§
а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛа¶Х, а¶Па¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶У а¶Єа¶ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶Є а¶Жа¶≤ඌ඙ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІЗа¶∞ බඌаІЯа¶Г ඙඙аІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶Ѓ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞а¶Њ ඙ඌаІЯа¶Њ а¶Ча¶£а¶єа¶§аІНа¶ѓа¶Њ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶Ња¶За¶ЫаІЗа•§ ඃබගа¶У а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ња¶≤а¶Ња¶За¶Ьа¶° а¶Па¶ђа¶В а¶ЃаІЛа¶Яа¶Ња¶ЃаІБа¶Яа¶њ ඙а¶∞а¶ња¶Ха¶≤аІН඙ථඌයаІАа¶®а•§ а¶Жа¶Єа¶≤ вАШа¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶ХвАЩ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶Ѓ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶≤аІН඙ а¶Ъа¶Ња¶≤аІБ а¶єаІЯ а¶Жආඌа¶∞аІЛපаІЛ පටඌඐаІНබаІАа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶Йථගප පටඌඐаІНබаІАටаІЗа•§ а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ьа¶Ња¶∞аІНඁඌථගටаІЗ ථඌ, පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶За¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЂаІНа¶∞ඌථаІНа¶Є а¶Па¶ђа¶В а¶Зටඌа¶≤а¶ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Еа¶ВපаІЗа•§ а¶Єа¶≠аІНඃටඌа¶∞ а¶Ьඌටගа¶Чට පаІЗа¶ХаІЬ ථඌඁаІЗ а¶ЂаІНа¶∞ඌථаІНа¶ЄаІЗ а¶Єа¶∞аІНඐ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶ђа¶Ња¶¶аІА ටටаІНටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Хඌප а¶єаІЯ а¶Па¶ђа¶В а¶ЂаІНа¶∞ඌථаІНа¶Є а¶Жа¶∞ а¶Зටඌа¶≤а¶ња¶∞ а¶≠ගටа¶∞аІЗа¶З а¶За¶єаІБබග-а¶ЈаІЬඃථаІНටаІНа¶∞ ටටаІНටаІНа¶ђ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌ а¶≤а¶Ња¶≠ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Па¶З а¶ЈаІЬඃථаІНටаІНа¶∞ ටටаІНටаІНඐඁටаІЗ, а¶Ђа¶∞а¶Ња¶Єа¶њ ඐග඙аІНа¶≤а¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶За¶єаІБබගබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶Яа¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶Єа¶≠аІНඃටඌа¶ХаІЗ а¶Ха¶ђаІНа¶Ьа¶ЊаІЯ а¶Жථඌа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Іа¶Ња¶™а•§ а¶Зටගයඌඪ බаІЗа¶Ца¶Ња¶За¶ЫаІЗ, вАШබаІНа¶ѓа¶Њ ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЯаІЛа¶Ха¶≤а¶Є а¶Еа¶Ђ බаІНа¶ѓа¶Њ а¶Па¶≤аІНа¶°а¶Ња¶∞а¶Є а¶Еа¶Ђ а¶Ьа¶ЊаІЯථвАЩ а¶ЬаІЗа¶ЬаІНа¶ѓаІБаІЯаІЗа¶Я а¶≤аІЗа¶Ьа¶ња¶Яа¶ња¶Ѓа¶ња¶ЄаІНа¶Я, а¶ЂаІНа¶∞аІЗа¶ЮаІНа¶Ъ а¶Жа¶∞ а¶∞ඌපගаІЯඌථ а¶Єа¶ња¶ХаІНа¶∞аІЗа¶Я а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶≠а¶ња¶ЄаІЗа¶∞а¶З а¶Ха¶Ња¶Ь, ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ьа¶Ња¶∞ඐඌබаІА ඙аІНа¶∞ටගа¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯඌපаІАа¶≤ а¶Жа¶∞ ථඌаІОа¶Єа¶ња¶∞а¶Њ බаІНа¶ђа¶ња¶Іа¶Ња¶єаІАථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶ЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ථаІЗа¶ЯаІЗ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Єа¶ња¶Ѓа¶Ња¶Ѓ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Х а¶Жа¶∞а¶ђ а¶УаІЯаІЗа¶ђа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶У а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІАаІЯ вАШа¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶ХвАЩ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Жබа¶∞аІНපаІЗ ඐඌථඌථаІЛа•§
а¶За¶Яа¶Ња¶≤ගටаІЗ а¶∞а¶Ња¶За¶Я а¶Йа¶За¶В а¶≤а¶ња¶°а¶Ња¶∞ а¶Ьඌථ඀аІНа¶∞а¶Ња¶ЩаІНа¶ХаІЛ ඀ගථග а¶Єа¶∞аІНа¶ђаІЛа¶ЪаІНа¶Ъ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ ටඌа¶∞ ඙ඌа¶∞аІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЕටаІАටаІЗа¶∞ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Х а¶Ха¶≤а¶ЩаІНа¶Х а¶ЃаІБа¶За¶Ыа¶Њ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗа•§ а¶Па¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ ටඌа¶ХаІЗ ඁථаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶Йа¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථ а¶ЄаІН඙аІЗපඌа¶≤а¶Яа¶њ а¶ђаІБа¶Хප඙аІЗ ඃඌථ, බаІЗа¶Ца¶ђаІЗථ а¶єа¶≤а¶њ а¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶За¶≤аІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶Еа¶Ха¶Ња¶≤аІНа¶Я а¶ђаІБа¶ХаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ а¶ЃаІБа¶ЄаІЛа¶≤ගථගа¶∞ а¶ђа¶ХаІНටаІГටඌ а¶Жа¶∞ вАШබаІНа¶ѓа¶Њ ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЯаІЛа¶Ха¶≤а¶Є а¶Еа¶Ђ බаІНа¶ѓа¶Њ а¶Па¶≤аІНа¶°а¶Ња¶∞а¶Є а¶Еа¶Ђ а¶Ьа¶ЊаІЯථвАЩ а¶ЦаІБа¶За¶Ьа¶Њ ඙ඌඐаІЗථ а¶Жа¶™а¶®а¶ња•§ а¶Па¶За¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶ђаІНа¶≤аІЗථаІНа¶° а¶ЬаІБа¶≤а¶ња¶Йа¶Є а¶Па¶≠аІЛа¶≤а¶Ња¶∞ ඁටаІЛ බаІЗපаІА а¶∞а¶Ња¶За¶Я а¶Йа¶За¶В а¶Жа¶За¶°а¶ња¶Уа¶≤а¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶ЦаІБа¶ђа¶З බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а•§ а¶ЦаІБа¶Ба¶Ьа¶≤аІЗ а¶Ж඙ථග а¶Уа¶За¶ЦඌථаІЗ а¶Па¶≠аІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶З-а¶У ඙ඌඐаІЗа¶®а•§
а¶ЃаІВа¶≤а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІАටග а¶Еа¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЕථаІЗа¶Х ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබаІА а¶Єа¶Ва¶Чආථ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ вАШа¶Ха¶ЃаІНа¶ѓаІБථගඪаІНа¶ЯвАЩ а¶ђа¶≤аІЗ බඌඐග а¶Ха¶∞аІЗа•§ ¬†а¶За¶Яа¶Ња¶≤а¶њаІЯඌථ ඐඌඁබаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ЃаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶ХаІЗа¶З а¶Ѓа¶Ња¶За¶∞а¶Њ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Њ а¶єа¶За¶ЫаІЗ, а¶Ђа¶≤аІЗ ටඌබаІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Па¶З вАШа¶Ха¶ЃаІНа¶ѓаІБථගඪаІНа¶ЯвАЩබаІЗа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤ඌබඌ බඌඐග а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞а•§ ටඌа¶∞а¶Њ а¶Зටගඁග඲аІНа¶ѓаІЗ ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබаІАබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶Жа¶За¶Єа¶Њ බඌаІЬа¶Ња¶За¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶ђаІЗа¶∞а¶≤аІБа¶ЄаІНа¶Хථගа¶ХаІЗа¶З а¶Па¶За¶Єа¶ђ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ ඁඌඕඌ а¶Ша¶Ња¶Ѓа¶Ња¶ЗටаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЄаІЗ ඃටа¶З а¶Ха¶Ња¶ЃаІЗа¶≤ а¶Жබඁග а¶єаІЛа¶Х ථඌ а¶ХаІЗථ, ටඌа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЄаІНඕඌ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶Ха¶†а¶ња¶®а•§ а¶За¶Яа¶Ња¶≤а¶њаІЯඌථ а¶∞а¶Ња¶За¶Я а¶Йа¶За¶В а¶Ха¶њ а¶Па¶За¶Єа¶ђ ථගаІЯа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ? а¶Па¶∞а¶Њ а¶Ха¶њ а¶Ѓа¶Ња¶Зථඌ ථගටаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶њ а¶ѓаІЗ а¶Па¶≠аІЛа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶Цථ а¶≠а¶ња¶Ьа¶Њ а¶ђа¶њаІЬа¶Ња¶≤ а¶єаІЯа¶Њ а¶ЙආаІЗ ථඌа¶З, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Жа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Ха¶За¶∞а¶Њ ඙аІЬа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶У а¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ъа¶∞а¶Ѓ а¶≠аІБа¶≤, а¶ЄаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶Ха¶Ьථ ඙ඌаІЬ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶Ња¶За¶Я? බаІНඐගටаІАаІЯ ඐගපаІНа¶ђа¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗа¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶У а¶ЄаІЗ ටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶ЊаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶За¶Яа¶Ња¶≤а¶њаІЯඌථ а¶∞а¶Ња¶За¶Я а¶Йа¶За¶ЩаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞а¶ЊаІЯ вАШබаІНа¶ѓа¶Њ а¶°а¶ња¶ЂаІЗථаІНа¶Є а¶Еа¶Ђ බаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞аІЗа¶ЄвА٠ඁටаІЛ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶Ча¶Ња¶ЬගථаІЗ вАШа¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶ХвАЩ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶∞аІЗа¶Яа¶∞а¶ња¶Х¬† а¶Па¶ЦථаІЛ а¶Ъа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ а¶Жа¶∞ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶°а¶Ња¶≤аІНа¶Я а¶Па¶ЬаІБа¶ХаІЗපථаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ХаІЗ බඌаІЯ ථගඐаІЗ а¶Па¶∞ а¶Еа¶ѓаІМа¶ХаІНටගа¶Хටඌ а¶ЬඌථඌථаІЛа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ?
ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞а¶ђ ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ බඌаІЯගටаІНа¶ђ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а¶За•§ а¶Па¶Ха¶ЗඪඌඕаІЗ, а¶ѓаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶єаІЛа¶Х ථඌ а¶ХаІЗථ, පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶ХаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ පටаІНа¶∞аІБබаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶≤аІЬа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ – а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶Чට а¶Жа¶∞а¶ђ а¶ПථаІНа¶Яа¶ња¶ЄаІЗа¶Ѓа¶ња¶Яа¶ња¶Ьа¶Ѓ а¶ЂаІЗථඌаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶°а¶ња¶Ьа¶ња¶Яа¶Ња¶≤ а¶Ѓа¶ња¶°а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≤аІЛ඙ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶£а¶§а¶Њ ථගаІЯаІЗ (аІ®аІ¶аІ¶аІѓ)
а¶Чට а¶∞а¶ђа¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶≠аІЗථගඪаІЗ а¶Па¶Х а¶Хථ඀ඌа¶∞аІЗථаІНа¶ЄаІЗ а¶°а¶ња¶Ьа¶ња¶Яа¶Ња¶≤ а¶Ѓа¶ња¶°а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶Ја¶£а¶ЄаІНඕඌаІЯаІАටаІНа¶ђ ථගаІЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Жа¶≤ඌ඙ ටаІЛа¶≤а¶Њ а¶єа¶За¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඁගපа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ца¶ЊаІЬа¶Њ ඙ඌඕа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ђа¶≤а¶Х, а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Хටග, ඙аІНඃඌ඙ගа¶∞а¶Ња¶Є, ඙පаІБа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶ЃаІЬа¶Њ а¶Па¶ђа¶В а¶Еටග а¶ЕඐපаІНа¶ѓа¶З а¶Ыඌ඙ඌථаІЛ а¶ђа¶З – а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ЗටගයඌඪаІЗ ටඕаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶Ѓ යගපඌඐаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗа•§¬† а¶ПබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶ђа¶За¶ХаІЗа¶З ඙ඌа¶Ба¶ЪපаІЛ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХඌථаІЛ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶ѓа¶Цථ а¶∞вАНаІНа¶ѓа¶Ња¶Ч ඙аІЗ඙ඌа¶∞ බගаІЯаІЗ ඐඌථඌථаІЛ а¶єа¶За¶ЫаІЗ පаІБа¶ІаІБ ටа¶Цථа¶За•§ а¶Йථඐගа¶Вප පටඌඐаІНබаІАа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶Цඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХඌආаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶£аІНа¶° ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶З а¶Ыඌ඙ඌථаІЛ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶За¶≤аІЗ ටඌа¶∞ а¶ЄаІНඕඌаІЯගටаІНа¶ђ а¶Ча¶њаІЯа¶Њ බඌаІЬа¶ЊаІЯ ඪටаІНටа¶∞ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа•§ බаІНඐගටаІАаІЯ ඐගපаІНа¶ђа¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗа¶∞ ඙а¶∞඙а¶∞ а¶Ыඌ඙ඌ а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶ХаІЛථ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ ඙ඌටඌ а¶Йа¶≤аІНа¶Яа¶ЊаІЯа¶Њ බаІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ බаІЗа¶Ца¶ђаІЗථ ඙аІГа¶ЈаІНආඌа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Єа¶ђ а¶ЦаІБа¶За¶≤а¶Њ ඙аІЬටаІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶З а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Ха¶Ња¶≤ а¶Іа¶∞аІЗа¶З а¶Хථ඀ඌа¶∞аІЗථаІНа¶Є а¶Жа¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶≤а¶Ња¶За¶ђаІНа¶∞аІЗа¶∞а¶ња¶ЧаІБа¶≤ඌටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶єа¶Ња¶∞ а¶Яа¶ња¶Ха¶ЊаІЯа¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶ЊаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ЃаІЛа¶Яа¶Ња¶ЃаІБа¶Яа¶њ а¶Еа¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ ඁථаІЗ а¶єа¶За¶≤аІЗа¶У, а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Й඙ඌаІЯ а¶єа¶За¶≤аІЛ ඃට а¶ђа¶З а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Єа¶ђа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶ХаІЗ а¶ЄаІНа¶ХаІНඃඌථ а¶Ха¶За¶∞а¶Њ а¶За¶≤аІЗа¶ХаІНа¶ЯаІНа¶∞ථගа¶Х а¶Ѓа¶ња¶°а¶њаІЯඌටаІЗ ඥаІБа¶Ха¶ЊаІЯа¶Њ බаІЗаІЯа¶Ња•§
а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Яа¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Эа¶Ња¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶ѓаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ЯаІНа¶∞ඌථаІНа¶Єа¶Ђа¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶Ва¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ђаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞а¶Њ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ, බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІБа¶Ха¶Ња¶≤ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶У а¶Ха¶Ѓ- а¶єаІЛа¶Х а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ђа¶ња¶≤аІНа¶Ѓ а¶∞а¶ња¶≤, а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶Х, а¶Еඕඐඌ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶За¶Йа¶Па¶Єа¶ђа¶њ а¶ЃаІЗа¶ЃаІЛа¶∞а¶њ а¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶Ха•§ а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶ѓа¶Х а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ-а¶Жа¶ЧаІЗа¶Ха¶Ња¶∞ බගථаІЗ а¶Еа¶°а¶ња¶У а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶Яа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБබගථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶З а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ЊаІЯа¶Њ බගටаІЛа•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЂаІБа¶Яа¶Ња¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞ බගаІЯаІЗ ඙аІЗථаІНа¶Єа¶ња¶≤ ඥаІБа¶Ха¶ЊаІЯа¶Њ а¶∞а¶ња¶УаІЯа¶Ња¶ЗථаІНа¶° а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Ъа¶Ња¶≤ඌථаІЛа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Єа¶ђа¶Єа¶ЃаІЯ а¶Па¶З ඙බаІН඲ටග а¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ බගටаІЛ, ටඌа¶У а¶®а¶Ња•§ а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ, а¶≠а¶ња¶°а¶ња¶У а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ а¶°аІЗ඀ගථаІЗපථаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБබගථ ඙а¶∞аІЗа¶З а¶Эа¶Ња¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЛ, а¶Жа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ ඙ගа¶ЫаІЗ а¶Яа¶Ња¶Зථඌ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶Ња¶За¶≤аІЗ ථඣаІНа¶Я а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶УаІЯඌථаІНа¶ЯаІБа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а•§ а¶ЄаІНа¶ХаІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶Ъ ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ч ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶≠а¶Ња¶Зථа¶≤ а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶Ъа¶Ња¶≤ඌථаІЛ а¶ѓа¶ЊаІЯ, а¶Па¶З а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ ථගаІЯаІЗа¶У а¶ЕථаІЗа¶Х а¶≠а¶Ња¶ђа¶Ыа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња•§ ටඐаІЗ а¶Єа¶ња¶°а¶њ а¶Ьගථගපа¶Яа¶Њ а¶ХටаІЛබගථ а¶Яа¶ња¶Ха¶ђаІЗ а¶Па¶Яа¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙ඌа¶З ථඌа¶За•§ а¶Єа¶ња¶°а¶њ а¶Жа¶За¶Єа¶Њ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђа¶ХаІЗ а¶ЃаІЛа¶Яа¶Ња¶ЃаІБа¶Яа¶њ а¶єа¶Яа¶ЊаІЯа¶Њ බගටаІЗ ථගа¶Ыа¶ња¶≤, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Еථа¶≤а¶Ња¶ЗථаІЗ а¶Єа¶ња¶°а¶ња¶∞ а¶ЄаІЗа¶За¶Ѓ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЯаІЗа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶≤ а¶Жа¶∞а¶У පඪаІНටඌаІЯ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶За¶≤аІЗ а¶Єа¶ња¶°а¶њ ථගа¶ЬаІЗа¶З а¶Ча¶ЊаІЯаІЗа¶ђ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЛа•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Па¶Яа¶Ња¶У ථඌ а¶°а¶ња¶≠ගධගටаІЗ а¶Хටබගථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЃаІБа¶≠а¶њ¬† а¶Яа¶ња¶ХаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІЗපග а¶За¶Йа¶Ь а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа¶З а¶Па¶Яа¶Њ а¶ЄаІНа¶Хග඙ а¶Ха¶∞а¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Пඁථග а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Ња¶∞а¶З а¶Яа¶Ња¶За¶Ѓ ඙ඌа¶З ථඌа¶З а¶ЂаІНа¶≤඙ගධගඪаІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ьඁඌථඌ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗ а¶ХаІЯа¶¶а¶ња¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶≠а¶Ња¶За¶ђа¶Њ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶ХаІЗа¶Я බගаІЯаІЗ а¶ЂаІНа¶≤඙ග а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶Х, а¶∞а¶ња¶∞а¶Ња¶За¶ЯаІЗа¶ђа¶≤ а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶Х බගаІЯаІЗ а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶ХаІЗа¶Я а¶Жа¶∞ а¶За¶Йа¶Па¶Єа¶ђа¶њ а¶ЃаІЗа¶ЃаІЛа¶∞а¶њ а¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶Х බගаІЯаІЗ а¶∞а¶ња¶∞а¶Ња¶За¶ЯаІЗа¶ђа¶≤ а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶Х ටඌа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ බа¶Ца¶≤ а¶Ха¶За¶∞а¶Њ ථගа¶ЫаІЗ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗа•§ а¶ѓаІЗа¶З а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶∞а¶ња¶° а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЛ, ¬†а¶Па¶З а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Ча¶ЊаІЯаІЗа¶ђ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶У а¶Ча¶ЊаІЯаІЗа¶ђ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЃаІЛа¶Яа¶Ња¶ЃаІБа¶Яа¶њ ථගපаІНа¶Ъගට а¶Па¶Цථ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ а¶ЂаІНа¶≤඙ග а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶Х а¶ЄаІНа¶≤а¶Яа¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶Њ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ ථඌа¶За•§ ඙аІБа¶∞ඌථаІЛ а¶Ђа¶Ња¶За¶≤а¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ඃබග а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶≠а¶Ња¶За¶Єа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථටаІБථ а¶°а¶ња¶≠а¶Ња¶За¶ЄаІЗ බаІБа¶З ටගථ а¶ђа¶Ыа¶∞ ඙а¶∞඙а¶∞ а¶ЯаІНа¶∞ඌථаІНа¶Єа¶Ђа¶Ња¶∞ ථඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ (а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Њ а¶ЕථථаІНටа¶Ха¶Ња¶≤ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶Ња¶ЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට), ටඌයа¶≤аІЗ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ථගа¶ГඪථаІНබаІЗа¶єаІЗ а¶єа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З а¶Эа¶Ња¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙а¶∞ගටаІНа¶∞а¶Ња¶£аІЗа¶∞ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶Й඙ඌаІЯ- а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЯаІЛа¶∞а¶∞аІБа¶ЃаІЗ ථඌථඌ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶°а¶Ьථ а¶ђа¶Њ ටඌа¶∞а¶У а¶ђаІЗපග а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶За¶Ца¶Њ බаІЗаІЯа¶Њ-а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶Ха¶Яа¶Ња¶З ඕඌа¶Ха¶ђаІЗ а¶ХаІЛථ ථඌ а¶ХаІЛථ ඐඌටගа¶≤ а¶Ђа¶Ња¶За¶≤-а¶ЄаІНа¶ЯаІЛа¶∞аІЗа¶Ь а¶ЃаІЗඕධаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Ха¶ња¶§а•§
ටඌа¶∞ ඁඌථаІЗ බඌаІЬа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗа¶Г а¶Єа¶ђ а¶ЃаІЗа¶ХаІНඃඌථගа¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤, а¶За¶≤аІЗа¶ХаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶Па¶ђа¶В а¶За¶≤аІЗа¶ХаІНа¶ЯаІНа¶∞ථගа¶Х а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶Ѓ ථඌ а¶єаІЯ а¶ЦаІБа¶ђ බаІНа¶∞аІБට ථඣаІНа¶Я а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ,¬† а¶Еඕඐඌ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ХаІЛථ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Ња¶З а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ ථඌ а¶ѓаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶Ѓа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ьඁඌථඌ а¶ХаІЯබගථ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗа•§
а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Іа¶∞аІЗථ, ඙ඌа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶Ь, ඐගබаІНа¶ѓаІБаІО а¶Ъа¶Ѓа¶Хඌථග а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථ ටаІБа¶ЪаІНа¶Ы а¶Ша¶Яථඌа¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЃаІЗа¶ЃаІЛа¶∞а¶њ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°а¶ХаІЗ а¶°а¶ња¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНථаІЗа¶Яа¶Ња¶За¶Ь а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Яа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІЬа¶ЄаІЬ а¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Х а¶Жа¶Йа¶ЯаІЗа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞аІЗ ඙аІЬа¶≤аІЗа¶З а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶За¶≤аІЗа¶Ха¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶ЃаІЗа¶ЃаІЛа¶∞а¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЬаІЛ ඕඌа¶ХаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶За¶≤аІЗа¶ХаІНа¶Яථගа¶Х а¶ЃаІЗа¶ЃаІЛа¶∞ගටаІЗ ¬†а¶ѓа¶§а¶З вАШධථ а¶Ха¶ња¶єаІЛටаІЗвАЩ¬† ඕඌа¶ХаІБа¶Х, ¬†а¶Жа¶Ѓа¶њ ¬†а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЃаІЛඁඐඌටගа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛටаІЗ, а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓа¶ХаІЗ, ථаІМа¶Ха¶ЊаІЯ, а¶ЧаІЛа¶Єа¶≤аІЗ, බаІЛа¶≤ථඌаІЯ ටඌ ඙аІЬටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЛ а¶®а¶Ња•§ а¶Еඕа¶Ъ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞ටගа¶ХаІВа¶≤ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌටаІЗа¶У а¶ђа¶З ඙аІЬа¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђа•§ ඙ඌа¶Ба¶Ъටа¶≤а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Њ а¶З-а¶ђаІБа¶Х а¶ЫаІБаІЬа¶≤аІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ЧаІБаІЬа¶Ња¶ЧаІБаІЬа¶Њ а¶єаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶З ඥගа¶≤ බගа¶≤аІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЕථаІНටට а¶ЙබаІНа¶Іа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђа•§
а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ටඕаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£аІЗа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђаІЗපග а¶ЬаІЛа¶∞ බගаІЯаІЗ а¶ЖඪටаІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗа¶У, а¶ђа¶З පаІБа¶ІаІБ ටඕаІНа¶ѓ а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ ථඌ, а¶Па¶∞ а¶Єа¶Ва¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£а¶У а¶Ха¶∞аІЗа•§ ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶ЯаІНඃඌථаІНа¶Я а¶∞а¶ња¶Ђа¶∞аІНа¶ЃаІЗපථаІЗ а¶Ыඌ඙ඌ а¶ђа¶Ња¶За¶ђаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ а¶Ха¶≤аІН඙ථඌ а¶Ха¶∞аІЗ බаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІЗа¶®а•§ а¶Пඁථа¶У а¶єа¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Х පටඌඐаІНබаІАа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶ђ а¶За¶≤аІЗа¶Ха¶ЯаІНа¶∞ථගа¶Х а¶Ѓа¶ња¶°а¶њаІЯа¶Њ а¶°а¶ња¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНථаІЗа¶Яа¶Ња¶За¶Ьа¶° а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ, ටа¶Цථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶Зථа¶ХаІБථаІНа¶ѓа¶Ња¶ђаІБа¶≤аІБа¶Ѓ а¶єа¶ђаІЗ а¶ЕටаІАට а¶Ьඌථඌа¶∞ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶Ѓа•§ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ѓаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Яа¶ња¶Ха¶ђаІЗ, а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶єа¶ЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ පаІНа¶∞аІЗа¶ЈаІНආ ඁඌථඪඁаІН඙ථаІНථ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶°а¶єаІАථ а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞а•§
а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶РටගයаІНඃඐඌබаІА а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ බаІБа¶ЗපаІЛ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌප а¶Ча¶ња¶Ча¶Ња¶ђа¶Ња¶За¶ЯаІЗа¶∞ а¶єа¶Ња¶∞аІНа¶°а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඐගපаІНඐඪඌයගටаІНа¶ѓ а¶Жа¶∞ බа¶∞аІНපථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞඙ගඪа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Ха¶За¶∞а¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ыа¶ња•§ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶Йа¶Ъа¶Њ පаІЗа¶≤а¶ЂаІЗа¶∞ а¶ЗаІЯа¶Њ а¶ЃаІЛа¶Яа¶Њ а¶ЃаІЛа¶Яа¶Њ а¶ђа¶З ථඌඁඌථаІЛа¶∞ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ ථаІЗаІЯа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶З а¶єа¶Ња¶∞аІНа¶°а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶Х а¶За¶Йа¶Ь а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Єа¶єа¶Ьа•§ а¶Жа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶З බඌථаІНටаІЗ а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ вАШа¶ЄаІБа¶Ѓа¶Њ ඕගа¶Уа¶≤а¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞вАЩ а¶ХаІЛථ а¶ЙබаІНа¶ІаІГටග а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа¶∞ ඙а¶≤а¶ХаІЗ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ХаІЛථ а¶Ша¶Яථඌа¶З а¶®а¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗа¶У а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶ЧаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Уа¶З а¶ђа¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Њ පаІЗа¶≤а¶ЂаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶За¶≤аІЗа¶ХаІНа¶ЯаІНа¶∞ථගа¶Х а¶ЗථаІНа¶Єа¶ЯаІНа¶∞аІБа¶ЃаІЗථаІНа¶Я а¶ѓа¶Цථ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ ථඌ ටа¶Цථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Хඌ඙ යගපඌඐаІЗа•§
ථඌ ඙аІЬа¶Њ а¶ђа¶З ථගаІЯаІЗ (аІ®аІ¶аІ¶аІ≠)
ඃටබаІВа¶∞ ඁථаІЗ ඙аІЬаІЗ, а¶Ьа¶∞аІНа¶ЬаІЛ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЩаІНа¶ЧඌථаІЗа¶≤аІНа¶≤а¶ња¶∞ ටඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞аІНа¶Яа¶ња¶ХаІЗа¶≤аІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤аІЛ а¶ѓаІЗ- а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ЭඌථаІБ ඙ඌආа¶Х ථටаІБථ а¶ХаІЛථ а¶ђа¶З а¶ЦаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶Жа¶Ба¶Ъ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ђа¶За¶Яа¶Њ ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶Ђа¶ЊаІЯබඌ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ХаІА а¶®а¶Ња•§¬† ටඌа¶∞ а¶Па¶З බඌඐаІА¬† а¶ХаІЛථ ඙аІЗපඌබඌа¶∞, а¶ЙаІОа¶Єа¶Ња¶єаІА а¶ђа¶Њ а¶Єа¶Ѓа¶Эබඌа¶∞ ඙ඌආа¶ХаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶∞аІНඕаІНа¶ѓаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЛ ථඌ; а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ХаІА ථඌ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶≤а¶Ња¶Зථ ඙аІЬаІЗ, බаІБа¶З а¶Па¶Х ඙ඌටඌ а¶Йа¶≤аІНа¶Яа¶ЊаІЯа¶Њ-඙ඌа¶≤аІНа¶Яа¶ЊаІЯа¶Њ බаІЗа¶За¶Ца¶Њ а¶ђа¶Њ а¶ЄаІВа¶Ъග඙ටаІНа¶∞, а¶∞аІЗа¶Ђа¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶Є а¶Ша¶Ња¶За¶Яа¶Ња¶З а¶ђаІБа¶За¶Эа¶Њ а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗ а¶Па¶Яа¶Њ ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶ХаІА а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶ђаІБа¶≤а¶ЊаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, ටඌа¶∞а¶Њ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Ю а¶≤аІЛа¶Ха•§ а¶ХගථаІНටаІБ, а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЩаІНа¶ЧඌථаІЛа¶≤аІНа¶≤а¶њ а¶За¶ЩаІНа¶Чගට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІН඙ඣаІНа¶Яටа¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶Ња¶°а¶ХаІНа¶Єа¶ња¶Ха¶Ња¶≤ а¶ЪаІЗа¶∞а¶Ња¶ЧаІА඙ථඌа¶∞ බගа¶ХаІЗа•§
а¶Єа¶Ња¶За¶ХаІЛа¶ЕаІНඃඌථඌа¶≤а¶ња¶ЄаІНа¶Я а¶Па¶ђа¶В ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х ඙ගаІЯаІЗа¶∞аІЗ а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶З а¶Жа¶ЫаІЗ вАШа¶єа¶Ња¶Й а¶ЯаІБ а¶Яа¶Х а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶ђа¶Ња¶Йа¶Я а¶ђаІБа¶ХаІНа¶Є а¶За¶Й а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶≠аІЗථаІНа¶Я а¶∞аІЗа¶°вА٠ථඌඁаІЗа¶∞а•§ а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶ђа¶З ඙аІЬа¶Ња¶∞ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ ථඌа¶З а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ђа¶За¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶ђа¶ЄаІНටаІБ ථඌ, а¶ђа¶∞а¶В а¶ЦаІБа¶ђ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶З ථඌ ඙аІЬаІЗа¶У а¶Ж඙ථග а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ ඪඌඕаІЗ (а¶Пඁථ а¶ХаІА а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞බаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗа¶У) а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶ЦаІБපගඁථаІЗ а¶Жа¶≤ඌ඙ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶ЊаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗථ – а¶Па¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗа¶З а¶ЄаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථඪඁаІНඁට а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ ටаІБа¶≤а¶ЫаІЗа•§ а¶Іа¶∞аІЗථ, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶≤а¶Ња¶За¶ђаІНа¶∞аІЗа¶∞ගටаІЗ а¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶Ѓа¶ња¶≤а¶ња¶Уථ а¶ђа¶З ඕඌа¶ХаІЗ; а¶Ж඙ථග ඃබග ඙аІНа¶∞ටගබගථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶У ඙аІЬаІЗථ ටඌයа¶≤аІЗ а¶Па¶Х а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗ аІ©аІђаІЂ а¶Яа¶Њ а¶ђа¶З ඙аІЬටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗථ, බප а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ча¶њаІЯаІЗ බඌа¶БаІЬа¶Ња¶ђаІЗ аІ©аІђаІ¶аІ¶, а¶Па¶ђа¶В බප а¶Па¶ђа¶В а¶Жපග а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ж඙ථග а¶Єа¶∞аІНа¶ђаІЛа¶ЪаІНа¶Ъ ඙аІЬටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗථ аІ®аІЂ,аІ®аІ¶аІ¶ а¶Яа¶Њ а¶ђа¶За•§ а¶ЦаІБа¶ђа¶З ථа¶Ча¶£аІНа¶ѓа¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ха•§ а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ, а¶ЃаІЛа¶Яа¶Ња¶ЃаІБа¶Яа¶њ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶ЄаІЗа¶ХаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶∞а¶њ а¶Па¶ЬаІБа¶ХаІЗපථ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Пඁථ а¶ѓаІЗа¶ХаІЛථаІЛ а¶За¶Яа¶Ња¶≤а¶њаІЯඌථ а¶ЦаІБа¶ђ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЬඌථаІЗ, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞а¶У ථඌ ඙аІЬаІЗ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶У а¶ђаІНඃඌථаІНа¶°аІЗа¶≤аІЛ, а¶ЂаІНа¶∞а¶Ња¶ЮаІНа¶Ъа¶ња¶Єа¶ХаІЛ а¶ЧаІБа¶За¶Ъа¶Ња¶∞аІНබගථග, а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶У а¶ђа¶ЗаІЯа¶Ња¶∞аІНබаІЛ а¶Еඕඐඌ а¶≠ගටаІНටа¶∞а¶ња¶У а¶Жа¶≤а¶Ђа¶њаІЯаІЗа¶∞а¶њ а¶ЯаІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶°а¶њ а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ ථගаІЯаІЗа¶≠аІЛа¶∞ вАШа¶Хථ඀аІЗපථ а¶Еа¶Ђ а¶ЕаІНඃඌථ а¶За¶Яа¶Ња¶≤а¶њаІЯඌථвАЩ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Х а¶ѓаІЗа¶ХаІЛථ а¶Жа¶≤ඌ඙аІЗ а¶ЬаІБа¶ЗаІЬа¶Њ ඐඪටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ – පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ ථඌඁ а¶Жа¶∞ ටඌබаІЗа¶∞ а¶єа¶Ња¶≤аІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶Эඌ඙ඪඌ а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶Яа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶Хථа¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Я а¶Ьඌථඌа¶∞ ඕаІНа¶∞аІБටаІЗа•§
а¶Жа¶∞ а¶Па¶З а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶Яа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶Хථа¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶З а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶∞аІБපа¶≤ ඙аІЯаІЗථаІНа¶Яа•§ а¶ХаІЛථ а¶Єа¶Ва¶ХаІЛа¶Ъ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶З а¶ЄаІЗ а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Њ බගа¶ЫаІЗ, а¶ЬаІЗа¶Ѓа¶Є а¶ЬаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶∞ вАШа¶За¶Йа¶≤а¶ња¶Єа¶ња¶ЄвА٠ථඌ ඙аІЬа¶Ња¶∞ ඙аІЬаІЗа¶У а¶ЄаІЗ а¶Па¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶≤ඌ඙ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Па¶Яа¶Њ вАШа¶Уа¶°а¶ња¶Єа¶њвАЩа¶∞а¶З ඙аІБථа¶∞аІНа¶ђаІЯඌථ ( а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබ а¶Па¶Яа¶Ња¶У а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ ඙аІБа¶∞а¶Њ вАШа¶Уа¶°а¶ња¶Єа¶њвАЩа¶У ටඌа¶∞ ඙аІЬа¶Њ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗ ථඌа¶З)а•§ а¶ЄаІЗ а¶Па¶Яа¶Ња¶У а¶ЬඌථаІЗ ඙аІБа¶∞а¶Њ а¶Ша¶Яථඌа¶Яа¶Њ а¶°а¶Ња¶ђа¶≤ගථаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ බගථаІЗ а¶ЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ථаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ ඁථаІЛа¶≤а¶ЧаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶≠ගටаІНටග а¶Ха¶∞аІЗ а¶Єа¶Ња¶ЬඌථаІЛа•§ вАШа¶Ђа¶≤аІЗвАЩ, а¶ЄаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗ, вАШа¶ХаІЛථ බаІБපаІНа¶ЪගථаІНටඌ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶З а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶З а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ ථඌථඌ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њвАЩа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶Ьඌථඌ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ ථඌ ඙аІЬа¶Њ а¶ђа¶За¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗа¶У а¶Ж඙ථග а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ьа¶Ња¶Зථඌ ඕඌа¶ХටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ, а¶За¶≠аІЗථ а¶ЪඌථаІНа¶Є а¶Жа¶ЫаІЗ- а¶ђа¶За¶Яа¶Њ ඙аІЬаІЗа¶У а¶єаІЯටаІЛ ටටаІЛа¶Яа¶Њ а¶ЬඌථටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗථ ථඌ ඃටаІЛа¶Яа¶Њ ථඌ ඙аІЬаІЗ а¶ЬඌථටаІЗа¶®а•§
а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබ බаІЗа¶Ца¶Ња¶За¶ЫаІЗ-¬† ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я¬† а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶З ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ж඙ථග а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Й඙а¶≤а¶ђаІНа¶Іа¶њ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ђа¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶ђа¶ЄаІНටаІБ а¶Ж඙ථඌа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶єаІЯටаІЛ а¶ђа¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЗа¶Й ඙аІЬаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗ, а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЙබаІНа¶ІаІГටග බගа¶ЫаІЗ, а¶Еඕඐඌ а¶ЄаІЗа¶За¶Ѓ а¶ЪගථаІНටඌа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶≠ගටа¶∞ බගаІЯаІЗ а¶ЖපаІЗ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ХаІЗа¶Й а¶єаІЯටаІЛ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබ ටඌа¶∞ ථඌ ඙аІЬа¶Њ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶≤а¶ња¶ЯаІЗа¶∞аІЗа¶∞а¶њ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Я ථගаІЯаІЗ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶Ъа¶Ѓа¶Х඙аІНа¶∞බ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ђаІЗа¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶∞а¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶Я а¶ЃаІБа¶Єа¶ња¶≤, а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶єа¶Ња¶Ѓ а¶ЧаІНа¶∞ගථ, а¶ЖථඌටаІЛа¶≤ а¶Ђа¶Ба¶Є, ඙а¶≤ а¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶∞а¶њ а¶Жа¶∞ а¶°аІЗа¶≠а¶ња¶° а¶≤а¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђа¶За¶У а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබ а¶ђа¶За¶Яа¶ЊаІЯ вАШබаІНа¶ѓа¶Њ ථаІЗа¶За¶Ѓ а¶Еа¶Ђ බаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞аІЛа¶ЬвА٠ථගаІЯаІЗ а¶Па¶Х а¶ЪаІНඃඌ඙аІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ඲ථаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§вАШබаІНа¶ѓа¶Њ ථаІЗа¶За¶Ѓ а¶Еа¶Ђ බаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞аІЛа¶ЬвАЩ-а¶Па¶∞ а¶Йа¶За¶≤а¶њаІЯа¶Ња¶Ѓ බаІНа¶ѓа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞а¶≠а¶ња¶≤ а¶ѓа¶Цථ ඙аІНа¶∞ඕඁඐඌа¶∞аІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶ња¶ЄаІНа¶Яа¶Яа¶≤аІЗа¶∞ вАШ඙аІЛаІЯаІЗа¶Яа¶ња¶ХаІНа¶ЄвАЩ-а¶Па¶∞ а¶єа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ බаІНඐගටаІАаІЯ а¶Ца¶£аІНа¶° යඌටаІЗ ඙ඌаІЯ, ටа¶Цථа¶З а¶ЄаІЗ පථඌа¶ХаІНට а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ыа¶ња¶≤аІЛ а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶ХаІЛථ а¶ђа¶За•§ а¶Па¶∞а¶ња¶ЄаІНа¶Яа¶Яа¶≤ ටඌа¶∞ а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗ а¶ХаІА а¶≤а¶ња¶Ца¶ЫаІЗ, а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶≠ගටаІНටග а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞а¶≠а¶ња¶≤ а¶Єа¶єа¶ЬаІЗа¶З а¶Па¶З а¶Хථа¶ХаІНа¶≤аІБපථаІЗ а¶Жа¶Єа¶Ыа¶ња¶≤аІЛа•§ а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛа¶Х, ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඥаІЛа¶≤ ඙ගа¶ЯඌථаІЛа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶З ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶Ьа¶Яа¶Њ а¶≤а¶ња¶ЦටаІЗа¶Ыа¶њ ථඌ, а¶Па¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞аІНа¶Яа¶ња¶ХаІЗа¶≤аІЗа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗа¶З а¶Ж඙ථඌа¶∞а¶Њ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§
а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබаІЗа¶∞ а¶ђа¶За¶Яа¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶ХаІМටаІВа¶єа¶≤аІЛබаІНබаІА඙а¶Х ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐථඌ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ѓаІЗ а¶ђа¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ඙аІЬа¶Њ а¶єаІЯ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞, ටඌа¶∞ а¶≠ගටа¶∞аІЗа¶∞ ඐගපඌа¶≤ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Еа¶Вපа¶З а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶≠аІБа¶За¶≤а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶За•§ ¬†а¶™аІНа¶∞а¶ХаІГට඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐаІЗ, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඁථаІЗ а¶ђа¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ХаІЗඁථаІЗ а¶Іа¶∞а¶Њ බගа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶≠ගටаІНටග а¶Ха¶∞аІЗа¶За¶Ж඙ථඁථаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІБаІЯа¶Ња¶≤ а¶Ыа¶ђа¶њ ඐඌථඌа¶ЗටаІЗ ඕඌа¶Ха¶њ а¶ђа¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ථගаІЯаІЗ, а¶ѓа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Хඕඌа¶∞¬† а¶Ѓа¶ња¶≤ ථඌа¶У ඕඌа¶ХටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶Ђа¶≤аІЗ, а¶ХаІЗа¶Й ඃබග а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶З ථඌ ඙аІЬаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඁථа¶ЧаІЬа¶Њ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶Ь а¶Еඕඐඌ а¶Єа¶ња¶ЪаІБаІЯаІЗපථ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶®а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Єа¶єа¶ЬаІЗа¶З ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶њ а¶ѓаІЗ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗа¶З а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗа•§
а¶ђа¶З ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබ а¶ЕථаІНа¶ѓ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Жа¶За¶°а¶њаІЯа¶Њ ඙аІЬа¶Њ යගපඌඐаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗ ථඌа¶∞а¶Ња¶Ьа•§ а¶Па¶З а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶Жа¶За¶Єа¶Ња¶З а¶ЄаІЗ ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЂаІЗа¶Єа¶∞аІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶ЪගථаІНටඌ ථඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Єа¶Ња¶За¶ХаІЛа¶ЕаІНඃඌථඌа¶≤а¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶∞ ඁටаІЛа•§ ටඌа¶∞ ඁටаІЗа¶Г а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඙аІЬа¶Њ, ථඌ ඙аІЬа¶Њ, а¶Еа¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯаІЗа¶Яа¶ња¶≠ а¶ЕаІНඃඌඪ඙аІЗа¶ХаІНа¶Я а¶Жа¶ЫаІЗа•§¬† а¶Па¶З а¶Ьගථගපа¶Яа¶Њ ඙ඌආа¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗ а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ѓа¶Ња¶∞ ඁටаІЛ а¶Ха¶∞аІЗ ඐඌථඌаІЯа¶Њ ථаІЗаІЯа•§ а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබ а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඌඐථඌа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Жа¶ЧаІНа¶∞а¶єаІА, а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶∞а¶Њ вАШа¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞вАЩ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶ђа¶З ටඌබаІЗа¶∞ ඙аІЬа¶Њ а¶≤а¶Ња¶Ча¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ථඌ ඙аІЬа¶Њ а¶ђа¶З ථගаІЯаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶Па¶Х а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶ЖටаІНථඪа¶ЪаІЗа¶§а¶®а¶§а¶Ња•§
а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබ а¶Па¶Яа¶Ња¶У බаІЗа¶Ца¶Ња¶За¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ, а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶З ථඌ ඙аІЬаІЗа¶У а¶ЄаІЗа¶З а¶ђа¶За¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Жа¶≤ඌ඙ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ХаІА ථඌ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗа¶З а¶ђа¶За¶Яа¶Њ ඙аІЬа¶ЫаІЗа•§ а¶Еඕа¶Ъ а¶ѓаІЗ а¶ђа¶За¶Яа¶Њ ඙аІЬа¶ЫаІЗ, а¶ЄаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶≠аІБа¶≤а¶≠а¶Ња¶≤ а¶Іа¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶З а¶ђа¶За¶Яа¶Ња¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Х а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ, вАШබаІНа¶ѓа¶Њ ථаІЗа¶За¶Ѓ а¶Еа¶Ђ බаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞аІЛа¶ЬвАЩ, а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶єа¶Ња¶Ѓ а¶ЧаІНа¶∞ගථаІЗа¶∞ вАШබаІНа¶ѓа¶Њ ඕඌа¶∞аІНа¶° а¶ЃаІНඃඌථвАЩ а¶Жа¶∞ а¶°аІЗа¶≠а¶ња¶° а¶≤а¶ЬаІЗа¶∞ вАШа¶ЪаІЗа¶За¶ЮаІНа¶Ьа¶ња¶В ඙аІНа¶≤аІЗа¶За¶ЄаІЗа¶ЄвАЩ-а¶Па¶∞¬† а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶∞ගටаІЗ а¶ЄаІЗ а¶За¶ЪаІНа¶Ыа¶Ња¶ХаІГට ටගථа¶Яа¶Њ а¶≠аІБа¶≤ ටඕаІНа¶ѓ ඥаІБа¶Ха¶Ња¶За¶ЫаІЗа•§ а¶ЖපаІНа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞ а¶єа¶За¶≤аІЛ, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓа¶Цථ а¶ђа¶За¶Яа¶Њ ඙аІЬа¶Ыа¶њ ටа¶Цථ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶єа¶Ња¶Ѓ а¶ЧаІНа¶∞ගථаІЗа¶∞ а¶≠аІБа¶≤а¶Яа¶Њ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗа¶З а¶Іа¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ыа¶њ, а¶°аІЗа¶≠а¶ња¶° а¶≤а¶ЬаІЗа¶∞а¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗ ඪථаІНබаІЗа¶єаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶З ථගаІЯаІЗ а¶≠аІБа¶≤ ටඕаІНа¶ѓа¶Яа¶Њ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа¶З ඙аІЬаІЗ ථඌа¶За•§ а¶Па¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබаІЗа¶∞ а¶ђа¶За¶Яа¶Њ ආගа¶ХඁටаІЛ ඙аІЬа¶њ ථඌа¶З, а¶Еඕඐඌ, а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶Ха¶З ඪඌඕаІЗ а¶ЄаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙ඌආа¶Ха¶∞а¶Њ¬† ඪථаІНබаІЗа¶є а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶За¶Яа¶ЊаІЯ а¶Ьа¶Ња¶ЄаІНа¶Я а¶ЪаІЛа¶Ц а¶ђаІБа¶≤а¶ЊаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ЗථаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶В а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞ а¶єа¶За¶≤аІЛ, ටගථа¶Яа¶Њ а¶За¶ЪаІНа¶Ыа¶Ња¶ХаІГට а¶≠аІБа¶≤ ඥаІБа¶ХඌථаІЛа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЄаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶З а¶Ѓа¶Ња¶Зථඌ ථගа¶≤аІЛ а¶ѓаІЗ а¶Па¶Х а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඙аІЬа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Х а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඙аІЬа¶Њ ඪආගа¶Хටа¶∞а•§ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗ а¶ђа¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබ ටඌа¶∞ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ, ටඌа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞а¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЭඌථаІБ ඙ඌආ ටඌа¶∞ ථගටаІЗ а¶єа¶За¶ЫаІЗ- පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ඙аІЬටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ ථඌ а¶Па¶З ටටаІНටаІНа¶ђ ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗа•§ а¶Па¶З а¶ХථаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶°а¶ња¶Хපථа¶Яа¶Њ а¶Пටа¶Яа¶Њ а¶ЄаІН඙ඣаІНа¶Я а¶ѓаІЗ, а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Еа¶ђа¶Ња¶Х а¶єаІЯаІЗ а¶≠ඌඐටаІЗа¶З ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІНබ а¶ХаІА а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђа¶За¶Яа¶Њ ඙аІЬаІЗ බаІЗа¶Ца¶ЫаІЗа•§
а¶Жа¶≤аІНа¶≤а¶Њ а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІА а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђаІЗа¶ХаІБа¶ђ (аІ®аІ¶аІІаІ¶)
а¶ЄаІЗබගථ а¶Па¶Х а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶≤а¶Ња¶ЮаІНа¶ЪаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶≠аІБа¶≤ а¶ђаІБа¶За¶ЭаІЗථ ථඌа¶Г а¶∞ග඙ඌඐаІНа¶≤а¶ња¶ХඌථබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ පа¶ХаІНට а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕථ ඕඌа¶Ха¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶У බаІБа¶З а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶∞аІЗබаІЛථаІНබඌ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Йа¶Х යගපඌඐаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶Ја¶ња¶ХаІНට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Яа¶Ња¶За¶ЯаІЗа¶≤ а¶Ыа¶ња¶≤а¶Г බаІБа¶ХаІНа¶ѓаІЗ බаІЗ а¶≤а¶Њ а¶ЖаІЯа¶≤а¶Њ බаІЗа¶≤ බගаІЯа¶Њ බаІЗ а¶ЖථаІНටаІЗа¶Єа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Па¶З а¶ЦаІЗටඌඐаІЗ а¶Жа¶∞а¶У а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНඁඌථගට а¶єа¶За¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඙аІЗබаІНа¶∞аІЛ а¶Жа¶≤ඁබаІЛа¶≠а¶Ња¶∞, а¶П а¶Па¶Є а¶ђа¶ЊаІЯаІЗට, а¶ЂаІНа¶∞а¶Ња¶ЩаІНа¶Ха¶ња¶Є а¶ЂаІЛа¶∞аІНа¶° а¶Х඙аІЛа¶≤а¶Њ, а¶Жа¶∞аІНටаІБа¶∞аІЛ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶Є а¶∞аІЗа¶≠аІЗа¶∞аІНටаІЗ, а¶Ьථ а¶ЕаІНඃඌපඐаІЗа¶∞а¶њ, а¶Уа¶∞යඌථ ඙ඌඁаІБа¶Х, а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶Йබගа¶У а¶Ѓа¶Ња¶Ча¶∞а¶ња¶Є, а¶∞аІЗ а¶ђаІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶°а¶ђаІЗа¶∞а¶њ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶∞а¶У а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Ьа¶®а•§ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶Яа¶Њ а¶єа¶За¶≤аІЛ- а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Цගට а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ЊаІЯ ඙а¶ЫථаІНබ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§
а¶УаІЯаІЗа¶ЄаІНа¶Я а¶ЗථаІНа¶°а¶ња¶ЬаІЗ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕගට а¶∞аІЗබаІЛථаІНබඌ බаІНа¶ђаІА඙аІЗа¶∞ а¶ЖаІЯටථ ටаІНа¶∞ගප а¶ђа¶∞аІНа¶Ча¶Ха¶ња¶≤аІЛа¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ња¶∞, а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞аІБа¶Ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶®а•§ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶З ඐඪටаІАа¶єаІАථ බаІНа¶ђаІА඙, බаІЗа¶За¶Ца¶Њ ඁථаІЗ а¶єаІЯ ථඌ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶ХаІЛථ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶Па¶З බаІНа¶ђаІА඙аІЗ ඙ඌ а¶ЂаІЗа¶≤а¶ЫаІЗа•§ аІІаІЃаІђаІЂ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЃаІНඃඌඕගа¶У а¶°а¶Ња¶Йа¶°а¶њ පඌаІЯа¶≤ ථඌඁаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶З බаІНа¶ђаІА඙ а¶Еа¶Іа¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶£аІАа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶Жа¶∞аІНа¶Ьа¶њ а¶ЬඌථඌаІЯ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶Яа¶ЊаІЯ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ а¶∞а¶Ња¶ЬටаІНа¶ђ а¶Ха¶ЊаІЯаІЗа¶ЃаІЗа¶∞а•§ а¶∞а¶Ња¶£аІА а¶ЦаІБපග а¶єаІЯаІЗа¶З ටඌ а¶Ѓа¶Ња¶Зථඌ ථаІЗаІЯ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඁථаІЗ а¶єа¶За¶Ыа¶ња¶≤аІЛ а¶Па¶З ඙аІБа¶Ъа¶Ха¶Њ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Яගප а¶Й඙ථගඐаІЗපගа¶Х а¶Єа¶Ња¶ЃаІНа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶єаІБа¶Ѓа¶Ха¶њ а¶°а¶Ња¶За¶Ха¶Њ а¶ЖථඐаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ а¶Па¶З බаІНа¶ђаІА඙аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Хඌථඌ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ යඌටඐබа¶≤ а¶єа¶За¶ЫаІЗа•§ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ХаІЗа¶Й а¶ХаІЗа¶Й а¶Па¶Ха¶З а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ ථඌථඌа¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ, а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Жа¶Зථа¶Чට а¶ЂаІНඃඌඪඌබа¶У а¶Ыа¶ња¶≤аІЛ බаІНа¶ђаІА඙а¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗа•§ а¶Ж඙ථග ඃබග а¶∞аІЗබаІЛථаІНබаІЛ බаІНа¶ђаІА඙аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Хඌථඌа¶∞ а¶ђа¶Вප ථගаІЯаІЗ а¶ЬඌථටаІЗ а¶Жа¶ЧаІНа¶∞а¶єаІА යථ, ටඌයа¶≤аІЗ а¶Йа¶За¶Хග඙ගධගаІЯඌටаІЗ а¶Па¶∞ а¶Жа¶∞аІНа¶Яа¶ња¶Ха¶≤а¶Яа¶Њ а¶ЪаІЗа¶Х а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а•§ аІІаІѓаІѓаІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ බаІНа¶ђаІА඙аІЗа¶∞ පаІЗа¶Ј а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶ЄаІН඙аІНඃඌථගප а¶≤аІЗа¶Ца¶Х а¶єа¶Ња¶≠а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶Єа¶ХаІЗ බаІНа¶ђаІА඙а¶Яа¶Ња¶∞ а¶Е඲ග඙ටග а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶∞а¶Ња¶ЬටаІНа¶ђ а¶єа¶ЄаІНටඌථаІНටа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶≤аІЗа¶Ца¶Х-а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶єа¶Ња¶≠а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶Є а¶Еටග а¶ЙаІОа¶Єа¶Ња¶єаІЗ බаІНа¶ђаІА඙аІЗа¶∞ ධඌථаІЗ, а¶ђа¶Ња¶ЃаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶ЦඌථаІЗ ථඌථඌ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶°а¶ња¶Йа¶Х а¶Еа¶≠а¶ња¶Ја¶ња¶ХаІНට а¶Ха¶∞а¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа•§
а¶Па¶За¶Яа¶Ња¶З а¶єа¶≤аІЛ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶°а¶ња¶Йа¶Х а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ша¶Яа¶®а¶Ња•§ ඃබගа¶У а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶Ђа¶ња¶Ьа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶ЃаІВаІЭටඌа¶∞ а¶ЧථаІНа¶І а¶Жа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗа¶У… ඙аІНа¶∞ටගබගථ ථගපаІНа¶Ъа¶З а¶ХаІЗа¶Й а¶°а¶ња¶Йа¶Х а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч ඙ඌаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛа¶Х, а¶Пටа¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓ а¶ЕථаІНа¶ѓа•§ а¶ЄаІЗබගථ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶Є а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ටඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ¬†а¶ЗථаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶В ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ђаІЗа¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Ьඌථඌа¶За¶Ыа¶ња¶≤аІЛа•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ѓаІЗ, а¶Жа¶Ьа¶Ха¶Ња¶≤а¶Ха¶Ња¶∞ ඁඌථаІБа¶Ја¶Ьථ а¶Яа¶ња¶≠ගටаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶ХаІА ථඌ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶Пඁථ а¶ХаІА а¶Яа¶ња¶≠ගටаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІОа¶Ха¶Ња¶∞ ථаІЗаІЯа¶Њ а¶єа¶За¶≤аІЗ ටඌа¶∞ ඙ගа¶ЫථаІЗа¶∞ а¶≠а¶њаІЬаІЗ а¶ђа¶За¶Єа¶Њ යඌට ථඌаІЬඌථаІЛа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶єа¶За¶≤аІЗа¶У а¶ЄаІЗ а¶ЯаІЗа¶≤а¶ња¶≠ගපථаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ња•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБබගථ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶За¶Яа¶Ња¶≤ගටаІЗ а¶ЦаІБථ а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶ђаІЛථаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶≠а¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶ХඌයගථаІА ¬†а¶ХඌථаІЗ а¶Жа¶Єа¶≤аІЛа•§ а¶Па¶Х ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶∞а¶Ња¶За¶Ѓ а¶Ха¶≤а¶Ња¶ЃаІЗ а¶≠а¶Ња¶За¶Яа¶Ња¶∞ ථඌඁ а¶ЃаІЗථපථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶За¶Ыа¶ња¶≤аІЛа•§ а¶Па¶З а¶Ша¶Яථඌа¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶ЄаІЗ а¶Па¶Х а¶ЯаІЗа¶≤а¶ња¶≠ගපථ а¶ЄаІЗа¶≤аІЗа¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Яа¶ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Ча¶њаІЯа¶Њ а¶Жа¶∞аІНа¶Ьа¶њ а¶ЬඌථඌаІЯ ටඌа¶ХаІЗ ඃඌටаІЗ а¶Яа¶ња¶≠а¶ња¶∞ ඙а¶∞аІНබඌаІЯ а¶°а¶Ња¶Ха¶Њ а¶єаІЯ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ЄаІЗ ටඌа¶∞ а¶ђаІЛථаІЗа¶∞ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶єаІГබаІЯඐගබඌа¶∞а¶Х а¶Ша¶Яථඌ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Пඁථ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ХаІЗа¶З а¶Ъගථග а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶≤а¶Ња¶За¶Ѓа¶≤а¶Ња¶За¶Я ඙ඌа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶њ- ඙а¶∞а¶ХаІАаІЯа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶Ња¶Ьа¶ђаІНඃඌථаІНа¶° ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶За¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞ටඌа¶∞а¶Х, а¶Зඁ඙аІЛа¶ЯаІЗථаІНа¶Я а¶ХаІЛථ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯаІЗа¶З ටඌа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ ථඌа¶З, а¶ХගථаІНටаІБ а¶≤а¶Ња¶За¶Ѓа¶≤а¶Ња¶За¶Яа¶Њ ටඌа¶∞ ඙ඌа¶ЗටаІЗа¶З а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶ХаІНа¶∞а¶Ња¶За¶Ѓ а¶Єа¶Ња¶За¶ХаІЛа¶≤а¶Ьа¶ња¶ЄаІНа¶ЯබаІЗа¶∞а¶У а¶Па¶Яа¶Њ а¶Еа¶Ьඌථඌ ථඌ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶≤ а¶Ха¶ња¶≤а¶Ња¶∞а¶∞а¶Њ а¶ЦаІБථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ђаІЗа¶Єа¶ња¶Х а¶Ха¶Ња¶∞а¶£а¶З¬† а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ХаІЗа¶Й ඃඌටаІЗ ටඌа¶ХаІЗ а¶ЦаІБа¶За¶Ьа¶Њ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ЦаІБа¶За¶Ьа¶Њ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤аІЗа¶З а¶ЄаІЗ а¶ђа¶ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶§а•§
а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶≠ඌඐටаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶Па¶З а¶ЃаІВаІЭටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ХаІА? а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ, а¶Па¶∞ ඪඌඕаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ИපаІНа¶ђа¶∞аІЗ ථඌ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ч а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓа¶Цථ ඁඌථаІБа¶Ј а¶≠ඌඐටаІЛ а¶Па¶Я а¶≤а¶ња¶ЄаІНа¶Я а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ЕථаІНටට а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ЬඌථаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ХаІА а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ХаІА а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Па¶Ха¶Ьථ ටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග බаІЯඌපаІАа¶≤, а¶Пඁථ а¶ХаІА а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ ටඌа¶∞ а¶≠аІБа¶≤ටаІНа¶∞аІБа¶Яа¶њ ථගаІЯаІЗ ථගථаІНබඌа¶У а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶З ඁඌථаІБа¶Ја¶Яа¶Њ а¶ЃаІЗа¶ђа¶њ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ЪаІНа¶ѓаІБට, а¶Еа¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња•§ а¶Ъа¶Ња¶∞඙ඌපаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ а¶єаІЯටаІЛ а¶ЄаІЗ а¶≤аІБа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З ථඌ, а¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ ටඌа¶ХаІЗ ඁථаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња¶∞ а¶ХаІЗа¶Йа¶З ථඌа¶З – а¶ХගථаІНටаІБ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ЕථаІНටට а¶Па¶З ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶Яа¶Њ а¶≤а¶Ња¶≤ථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ, а¶ХаІЗа¶Й а¶Па¶Ха¶Ьථ ටඌа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶Єа¶ђ а¶ЬඌථаІЗа•§
а¶Еа¶ЄаІБа¶ЄаІНඕ බඌබаІА, а¶ѓа¶Ња¶∞ ථඌටග඙аІБටගа¶∞а¶Њ ටඌа¶ХаІЗ а¶Ыа¶Ња¶ЗаІЬа¶Њ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, а¶єаІЯටаІЛ а¶ђа¶≤ටаІЛ, вАШа¶Жа¶≤аІНа¶≤а¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶≤аІБа¶Ѓ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Хට а¶≠аІБа¶Ча¶Ыа¶њвАЩа•§
ඐගථඌ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Єа¶Ња¶Ьඌ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНට ඁඌථаІБа¶Ј ඪඌථаІНටаІНඐථඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЛ, вАШа¶Жа¶≤аІНа¶≤а¶Њ а¶ЬඌථаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථගа¶∞аІНබаІЛа¶ЈвАЩа•§
а¶Еа¶ХаІГටа¶ЬаІНа¶Ю ඙аІЛа¶≤ඌ඙ඌථа¶∞аІЗ ටඌа¶∞ а¶Ѓа¶Њ а¶ђа¶≤ටаІЛ, вАШа¶Жа¶≤аІНа¶≤а¶Њ а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІА а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІЛඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶Хටа¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶њвАЩа•§
а¶ЫаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Њ а¶Ца¶ЊаІЯа¶Њ ඙аІНа¶∞аІЗа¶Ѓа¶ња¶Х а¶Ъа¶ња¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶ЗටаІЛ, вАШа¶Жа¶≤аІНа¶≤а¶Њ а¶ЬඌථаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Хට а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа¶ђа¶Ња¶Єа¶њвАЩа•§
а¶Ъа¶Ња¶∞බගа¶ХаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ යටа¶≠а¶Ња¶Ча¶Њ ඁඌථаІБа¶Ја¶Яа¶Њ, а¶ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ХаІЗа¶Й ඙ඌටаІНටඌ බаІЗаІЯ ථඌ,¬† ටඌа¶∞ а¶ЕථаІНටට а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤, вАШа¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶Жа¶≤аІНа¶≤а¶Њ а¶ЬඌථаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІАа¶ЄаІЗа¶∞ а¶≠ගටа¶∞ බගаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗ а¶єа¶За¶ЫаІЗвАЩа•§
а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶Па¶З а¶Єа¶∞аІНඐබа¶∞аІНපаІА а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІАа¶ХаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЫගථඌаІЯа¶Њ ථаІЗаІЯа¶Њ а¶єа¶За¶ЫаІЗ, ටඌа¶∞ а¶ЕථаІБ඙ඪаІНඕගටගටаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ХаІА? а¶Па¶Цථ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶∞඙ඌපаІЗ පаІБа¶ІаІБ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЪаІЛа¶Ц, вАШа¶ЕථаІНа¶ѓаІЗа¶∞вАЩ а¶ЪаІЛа¶Ц – ඃඌබаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞ටаІЗа¶З а¶єа¶ђаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප ථඌ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶З ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶єаІЛа¶≤аІЗа¶∞ ථඌඁයаІАථටඌаІЯ а¶єа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђа¶Њ, а¶єа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђа¶Њ а¶ђа¶ња¶ЄаІНа¶ЃаІГටගа¶∞ а¶ШаІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶§аІЗа•§ а¶Па¶З а¶≠аІЯаІЗ а¶ХаІЗа¶Й а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З ථаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶Яа¶Њ ඙ඌа¶Ча¶≤а¶єа¶ЗටаІЗа¶У а¶Ж඙ටаІНටග а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§
а¶ЯаІЗа¶≤а¶ња¶≠ගපථаІЗ а¶°а¶Ња¶Х ඙ඌа¶УаІЯа¶Ња¶Яа¶Њ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ЄаІЗа¶З вАШа¶Єа¶∞аІНඐබа¶∞аІНපаІА а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶Ха¶∞аІНටඌвАЩ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞ටගඪаІНඕඌ඙ථ ඁඌටаІНа¶∞а•§ а¶Яа¶ња¶≠ගටаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶Яа¶Њ а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЯаІНа¶∞аІНඃඌථа¶ЫаІЗථධаІЗථаІНа¶Є, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗ а¶ЄаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Ьඌථඌа¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьථ а¶Яа¶ња¶≠ග඙а¶∞аІНබඌ ථඌඁаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶Ха¶Ња¶≤аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞аІЗ බаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ ඪඌඁථаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶∞ ඐග඙а¶∞аІАටаІЗ, а¶ЄаІЗа¶З а¶Яа¶ња¶≠ග඙а¶∞аІНබඌа¶∞ ඙а¶∞а¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ,ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ъа¶≤а¶Ња¶Ъа¶≤ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶Яа¶ња¶≠ග඙а¶∞аІНබඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ බа¶∞аІНපа¶ХබаІЗа¶∞ а¶За¶єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶За•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞, а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ බа¶∞аІНපа¶Х а¶Жа¶∞ а¶Яа¶ња¶≠ගටаІЗ а¶ѓа¶Ња¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶ЊаІЯ а¶ЄаІЗа¶За¶Єа¶ђ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶ЊаІЯа¶Ња¶З а¶Па¶З а¶За¶єа¶Ха¶Ња¶≤а•§ а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ха¶∞аІЗ බаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІЗථ, а¶Па¶З а¶За¶єа¶Ха¶Ња¶≤-඙а¶∞а¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ඃඌටඌаІЯඌට а¶ХаІНа¶Ја¶£а¶ЄаІНඕඌаІЯаІА а¶Па¶ђа¶В ටаІНа¶ђа¶∞ගට а¶єа¶За¶≤аІЗа¶У а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶Еа¶Ѓа¶∞ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶ЗඪඌඕаІЗ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ ඙аІГඕගඐаІА а¶Жа¶∞ а¶Ха¶≤аІН඙ගට а¶Ка¶∞аІНа¶ІаІНа¶ђа¶≤аІЛа¶Х, බаІБа¶З а¶Ьа¶ЊаІЯа¶ЧඌටаІЗа¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІАа¶∞аІНටථ а¶Ча¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶З ඙аІБа¶∞а¶Њ а¶Ша¶ЯථඌаІЯа•§
а¶Эа¶Ња¶ЃаІЗа¶≤а¶Ња¶Яа¶Њ а¶єа¶За¶≤аІЛ, а¶Па¶З вАШа¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටගвАЩа¶Яа¶Њ බаІНа¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІНඕඐаІЛа¶Іа¶Ха•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶Ъа¶Ња¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ පаІНа¶∞а¶Ѓ, а¶ЃаІЗа¶Іа¶Њ, ටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ч а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶ѓаІЗа¶ХаІЛථ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛටаІНа¶ђа¶З ඃඌටаІЗ вАШа¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටвАЩ а¶єаІЯа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЯаІЗа¶≤а¶ња¶≠ගපථаІЗ а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞а¶Њ බаІЗаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ ඁඌථаІБа¶Ја¶Ьථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ѓа¶Цථ බаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІЗ ටа¶Цථ а¶ђа¶≤аІЗ, вАШටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ъගථа¶Ыа¶њ, а¶Чටа¶∞ඌටаІНа¶∞аІЗ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЯаІЗа¶≤а¶ња¶≠ගපථаІЗ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶ЃвАЩа•§ а¶Па¶З вАШа¶ЃаІБа¶Ца¶ЪаІЗථඌа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටගвАЩ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටග ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶З а¶Жа¶≤ඌබඌ බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶Ьа¶ња¶®а¶ња¶ґа•§
ප඀ගа¶Йа¶≤ а¶ЬаІЯ
Latest posts by ප඀ගа¶Йа¶≤ а¶ЬаІЯ (see all)
- а¶ХаІНа¶∞ථගа¶Ха¶≤а¶Є а¶Еа¶Ђ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Њ а¶≤а¶ња¶ХаІБа¶За¶° а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶ња•§а•§ а¶Йа¶Ѓа¶ђаІЗа¶∞аІНටаІЛ а¶Па¶ХаІЛ а•§а•§ - а¶ЂаІЗа¶ђаІНа¶∞аІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ 25, 2019