а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ පගа¶≤аІН඙аІА а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ вАУ а¶Жа¶ђаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶ЙබаІНබаІАථ а¶Жයඁබ (а¶Єа¶ња¶≤аІЗа¶ХаІНа¶ЯаІЗа¶° ඙ඌа¶∞аІНа¶Я аІ™)
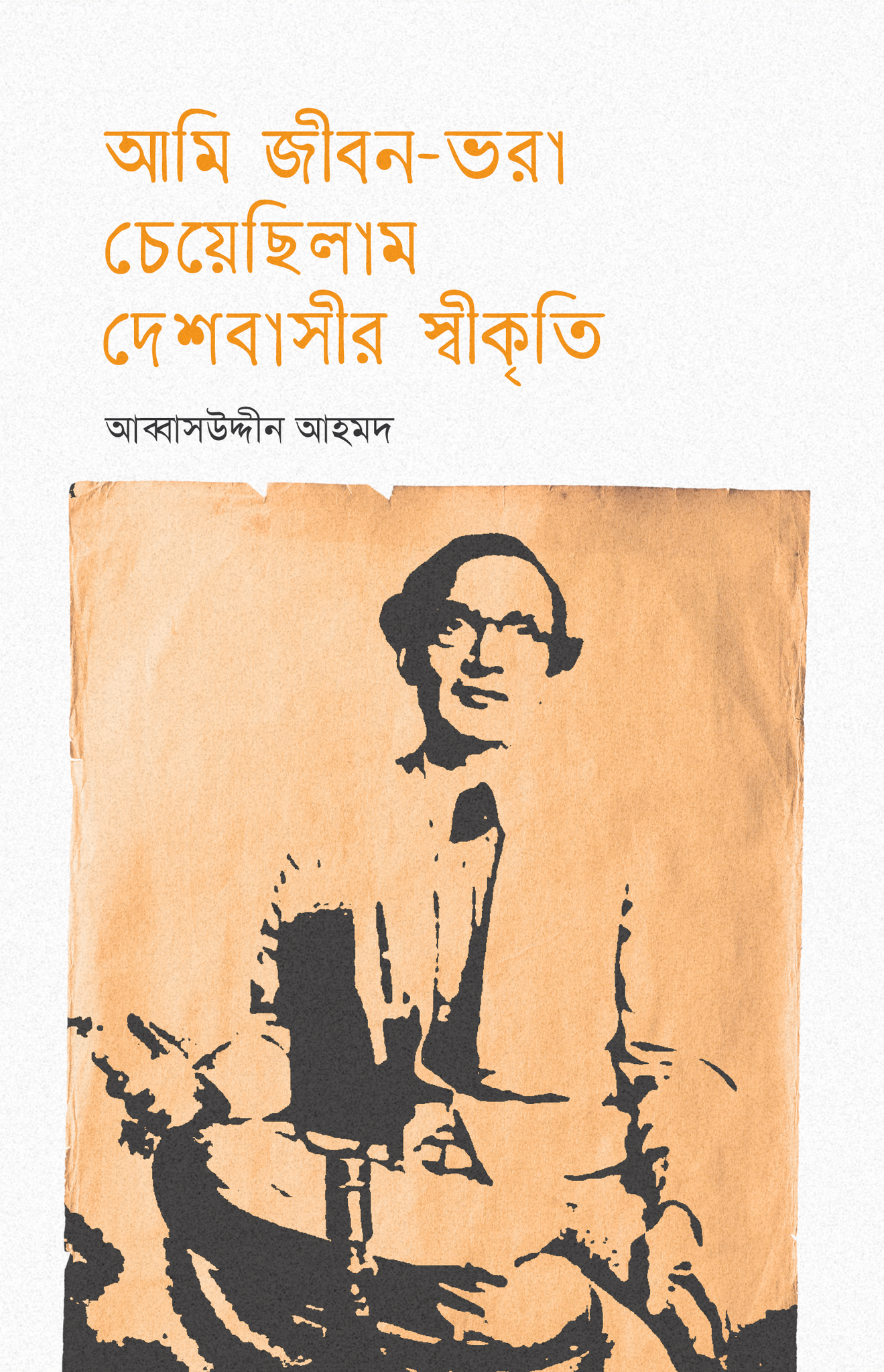
඙ඌа¶∞аІНа¶Я аІІ а•§а•§ ඙ඌа¶∞аІНа¶Я аІ® а•§а•§ ඙ඌа¶∞аІНа¶Я аІ© а•§а•§
…
а•§а•§ а¶Ъа¶Ња¶ХаІБа¶∞аІА а¶У а¶ђа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а••
බаІБ’а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌ а¶Еа¶∞аІНа¶Ьථ а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІГа¶Ја¶њ බ඀ටа¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶Ха¶Њ а¶Ъа¶Ња¶ХаІБа¶∞аІА а¶Ца¶Ња¶≤а¶њ а¶єа¶≤, බа¶∞а¶Ца¶Ња¶ЄаІНට а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Ъа¶Ња¶ХаІБа¶∞аІАа¶Яа¶Њ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶°а¶њ. ඙ග. а¶Жа¶З а¶Еа¶Ђа¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЄаІНඕඌඃඊаІА а¶Ъа¶Ња¶ХаІБа¶∞аІАටаІЗ а¶За¶ЄаІНට඀ඌ බගඃඊаІЗ ඙ඌа¶Ха¶Њ а¶Ъа¶Ња¶ХаІБа¶∞аІАටаІЗ ඥаІБа¶Ха¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Йа¶∞аІНа¶ІаІНඐටථ, а¶ХаІГа¶Ја¶њ а¶ђа¶ња¶≠а¶Ња¶ЧаІЗа¶∞ а¶°аІЗ඙аІБа¶Яа¶њ а¶°а¶ња¶∞аІЗа¶ХаІНа¶Яа¶∞ а¶Уа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІНථ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶ХаІЗа¶≤, ටගථග а¶Па¶Хබගථ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶Жа¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ, а¶Ж඙ථඌа¶∞ ථඌඁ а¶Ха¶њ а¶ЄаІЗа¶З, а¶Жа¶Ьа¶Ха¶Ња¶≤ а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶°аІЗ а¶ЦаІБа¶ђ ථඌඁ පаІБථගвА¶ а¶ЄаІЗа¶За¶З?вАЭ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Еටග ඐගථඃඊаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬа¶Жа¶ЬаІНа¶ЮаІЗ а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Ба•§вАЭ а¶§а¶Ња¶∞ ථඌඁ ඃබаІБථඌඕ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а•§ ටගථග а¶єаІЗа¶° а¶Па¶Єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІЗථаІНа¶Яа¶ХаІЗ а¶°аІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬබаІЗа¶ЦаІБථ, а¶Па¶ХаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤ а¶Ха¶Ња¶Ь බаІЗа¶ђаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Еа¶Ђа¶ња¶ЄаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ ථඌඁ බඪаІНටа¶Цට а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ЦаІБපаІА а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗථ, ඐගපаІЗа¶Ј а¶Ха¶∞аІЗ බаІБ඙аІБа¶∞аІЗ ඃබග а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶∞а¶ња¶єа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶Ъඌථ а¶Ха¶ХаІНа¶Ја¶£аІЛ а¶ђа¶Ња¶Іа¶Њ බаІЗа¶ђаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠а¶Ња¶ЧаІЗ а¶Пඁථ а¶≤аІЛа¶Х ඙аІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶њ а¶ПටаІЗа¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЄаІМа¶≠а¶Ња¶ЧаІНа¶ѓа•§вАЭ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ђа¶Ња¶єаІБа¶≤аІНа¶ѓ а¶ђаІГබаІНа¶І а¶єаІЗа¶° а¶ПаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯඌථаІНа¶Я а¶Іа¶∞аІНඁබඌඪ-а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶П ථගඃඊඁаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶ђаІНඃටගа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶®а¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶З а¶Па¶З බаІБа¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶З а¶ХаІГටа¶ЬаІНа¶Юа•§ а¶Па¶БබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Іа¶Ња¶Іа¶∞а¶Њ ථගඃඊඁаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ХаІБа¶∞аІА а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ ඪටаІНа¶ѓа¶ња¶З а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЧаІАටඪඌ඲ථඌа¶∞ ඙ඕаІЗ ථගа¶∞аІНඐගඐඌබаІЗ а¶Па¶ЧаІБටаІЗ ඙ඌа¶∞ටඌඁ а¶®а¶Ња•§
а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЛа¶ЂаІЛථ а¶ХаІЗа¶ЃаІН඙ඌථаІАටаІЗ а¶Па¶Хබගථ а¶Ха¶Ња¶Ьගබඌа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ а¶єа¶∞ගබඌඪ, а¶ЃаІБа¶£а¶Ња¶≤ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЗ а¶ХаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶Ча¶≤аІН඙ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Пඁථ а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЧаІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Ьඌථග ථඌ а¶Ха¶њ. а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞, යආඌаІО а¶Ха¶Ња¶Ьගබඌ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Йආа¶≤аІЗථ ටඌබаІЗа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗප а¶Ха¶∞аІЗ, вАЬබаІЗа¶Ц ටаІЛඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа•§ а¶Хඕ а¶ђа¶≤а¶ња•§ а¶Жа¶ђаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЫаІЛа¶Я а¶≠а¶Ња¶За•§ බගථ බගථ а¶ЧඌථаІЗ а¶Ъа¶ЃаІОа¶Ха¶Ња¶∞ ථඌඁ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ ඃබග ටаІЛа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ХаІЗа¶Й а¶Па¶ХаІЗ а¶ХаІЛථබගථ а¶Ца¶Ња¶∞ඌ඙ ඙ඕаІЗ ථගඃඊаІЗ а¶ѓа¶Ња¶У ටඌයа¶≤аІЗ ටаІЛඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЬаІНඃඌථаІНට а¶∞а¶Ња¶Ца¶ђ а¶®а¶Ња•§вАЭ а¶ђа¶≤а¶Ња¶З а¶ђа¶Ња¶єаІБа¶≤аІНа¶ѓ а¶Ха¶Ња¶Ьගබඌа¶∞ а¶Па¶Хඕඌ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞аІЗ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞аІЗ ඙ඌа¶≤ථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§
а¶Па¶Хබගථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Я а¶Ша¶Яථඌ а¶ђа¶≤а¶ња•§ а¶Ха¶ђа¶њ පаІИа¶≤аІЗථ а¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶≤аІНඃඐථаІНа¶ІаІБа•§ а¶Еа¶≠ගථаІЗටඌ බаІБа¶∞аІНа¶ЧඌබඌඪඐඌඐаІБ а¶≠а¶Ња¶∞аІА а¶∞а¶Єа¶ња¶Х а¶≤аІЛа¶Х, පаІИа¶≤аІЗථ а¶У а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶ЄаІНථаІЗа¶є а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Ља¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බаІБа¶Ьථа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗථ, вАЬа¶Па¶Хබගථ а¶єаІЛа¶Х ථඌ а¶Па¶Х඙ඌටаІНа¶∞! බаІЛа¶Ј а¶Ха¶њ?вАЭ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶Хබගථ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬа¶Ж඙ථඌа¶∞ යඌටаІЗ යඌටа¶Ца¶°а¶Ља¶њ а¶єа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ ඁඌථаІЗ ටаІЗаІЈ а¶Еа¶≤ а¶ЗථаІНа¶°а¶њаІЯа¶Њ а¶∞аІЗа¶°а¶ња¶УටаІЗ а¶Ца¶ђа¶∞ а¶ђа¶≤а¶Ња•§ ටගථග а¶єаІЗа¶ЄаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗථ, вАЬа¶Жа¶∞аІЗ ථඌ ථඌ, а¶Ха¶Ња¶Х඙а¶ХаІНа¶ЈаІАа¶У а¶ЬඌථටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§вАЭ а¶ґаІИа¶≤аІЗථ а¶ђа¶≤ට, вАЬටඌ බаІБа¶∞аІНа¶ЧඌබඌвАЩ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЬаІАа¶ђ а¶≤а¶ња¶≠а¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶Пට а¶єа¶ња¶Ва¶Єа¶Њ а¶ХаІЗථ?вАЭ а¶®а¶Ња¶Г а¶°а¶Ња¶≤ а¶Жа¶∞ а¶Ча¶≤аІЗ а¶®а¶Ња•§ බаІБа¶∞аІНа¶ЧඌබඌඪඐඌඐаІБа¶ХаІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗ පаІБථаІЗа¶Ыа¶њ, вАЬа¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ, а¶Па¶∞а¶Њ а¶Хඌබඌඃඊ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Хඌබඌ а¶Ча¶Ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЦаІЗ а¶®а¶Ња•§вАЭ
а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶Ња¶ЂаІЛථ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථаІАа¶∞ а¶∞а¶ња¶єа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶≤ а¶∞аІБа¶Ѓа¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ ටа¶Цථ а¶Еටග а¶Ьа¶ШථаІНа¶ѓ а¶Ьа¶Ња¶ѓа¶Ља¶Ча¶Ња¶ѓа¶Љ а•§ ಲಐಶථа¶В а¶Ж඙ඌа¶∞ а¶Ъа¶њаІО඙аІБа¶∞ а¶∞аІЛа¶°, а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶£аІБа¶≠а¶ђа¶®а•§ ටඌа¶∞ а¶ЖපаІЗ-඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ђа¶єаІБබаІВа¶∞аІЗ а¶≠බаІНа¶∞а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶П බаІБඣගට а¶Жа¶ђа¶єа¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶ѓа¶Љ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІАа¶Ъа¶ња¶ЈаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶Хටබගථ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐ඙а¶∞ а¶єа¶ђаІЗ а¶Па¶З ථගඃඊаІЗ බඪаІНටаІБа¶∞ඁට а¶ЪගථаІНටගට а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ ඙ධඊа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Еа¶Ха¶ЄаІНа¶Ѓа¶ЊаІО а¶Па¶Хබගථ ඁථඪаІНඕගа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Ња¶ХаІЗ ‘а¶ЬඌථගඃඊаІЗ බගа¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЬаІАа•§
а¶єа¶≤аІНබගඐඌධඊаІАටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බаІЛа¶ЄаІНට ඁපඌа¶∞а¶Ђ а¶єаІЛа¶ЄаІЗථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ а¶Ъගආග බගа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞а¶Ва¶Чටඁ а¶ђа¶Ња¶≤аІНඃඐථаІНа¶ІаІБ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බаІЛа¶ЄаІНට ඁපඌа¶∞а¶Ђ а¶єаІЛа¶ЄаІЗа¶®а•§ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶ЬаІЗථаІНа¶ХගථаІНа¶Є а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Цථ а¶Єа¶ња¶ЄаІНа¶Хඕ а¶ХаІНа¶≤ඌපаІЗ а¶≠а¶∞аІНටග а¶єа¶З, ටа¶Цථа¶З ටඌа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඐථаІНа¶ІаІБටаІНа¶ђ а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶ЙආаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶З а¶єаІЛа¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶≤аІЗ ඕඌа¶Ха¶ња•§ ටඌа¶∞а¶Њ ටගථа¶≠а¶Ња¶З а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я а¶Єа¶ЃаІН඙ටаІНටගа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Х вАУ а¶ЖපаІИපඐ ඙ගටаІГа¶єаІАа¶®а•§ а¶Єа¶ЃаІН඙ටаІНටග ටඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІЛа¶∞аІНа¶Я а¶Еа¶ђ а¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞аІНа¶°а¶ЄаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІАථаІЗа•§ а¶Па¶∞ а¶ђа¶°а¶Љ а¶≠а¶Ња¶За¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶°а¶Љ а¶≠а¶Ња¶За¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБටаІНа¶ђвАУටඌа¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බаІБ’а¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа¶У а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶УආаІЗ ඐථаІНа¶ІаІБටаІНа¶ђа•§ а¶єаІЛа¶ЈаІНа¶ЯаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ђа¶≤а¶≤аІЗ, а¶ђа¶Ња¶Г а¶Па¶∞а¶Њ බаІБа¶ЯගටаІЗ а¶ђаІЗප а¶Ѓа¶ња¶≤а•§ බаІЛа¶ЄаІНටඌа¶≤а¶њ ඙ඌටඌа¶Уа•§ ටඌа¶З බаІБ’а¶Ьථ බаІБ’а¶Ьථа¶ХаІЗ බаІЛа¶ЄаІНට а¶ђа¶≤аІЗ а¶°а¶Ња¶Ха¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බаІЛа¶ЄаІНට а¶Па¶Цථ а¶∞а¶В඙аІБа¶∞ ඲ඌ඙аІЗ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа¶®а•§
බаІЛа¶ЄаІНට а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Ъගආග බගа¶≤, ටඌа¶∞ а¶Уа¶ЦඌථаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶∞а¶В඙аІБа¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶°аІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ බප а¶ђа¶Ња¶∞ බගථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶ђа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§
ටа¶Цථ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Ха¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ђа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ බගථаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ша¶Яථඌ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶З а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶ѓаІЗබගථ а¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ЄаІЗබගථ а¶єа¶ђаІБ පаІНඐපаІБа¶∞а¶ђа¶Ња¶°а¶ЉаІАටаІЗ а¶ХаІА а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶Ша¶Яа¶Ња•§ а¶єа¶Ња¶∞а¶ЃаІЛථගඃඊඌඁ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Хට а¶Чඌථа¶З а¶ЧаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ඙ඌධඊඌа¶∞ а¶≤аІЛа¶Х а¶ЄаІЗබගථ а¶Жа¶Єа¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§
а¶ђа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ බගථ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඐථаІНа¶ІаІБඐඌථаІНа¶Іа¶ђ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶∞ඌටаІЗ ටа¶Ха¶∞аІАа¶Ѓ а¶Жයඁබ а¶ѓаІЗа¶З а¶ЄаІЗටඌа¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶ЯаІБа¶Ва¶Яа¶Ња¶В පඐаІНබ ටаІБа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ а¶Еඁථග а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞а¶§а¶ња¶ђа¶Ња¶¶а•§ ථඌ, а¶Па¶Ха¶њ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ-а¶ђа¶Ња¶°а¶ЉаІА. а¶Чඌථ-а¶ђа¶Ња¶Ьථඌ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථ ථаІЗа¶З а¶ЗටаІНඃඌබග! ඐථаІНа¶ІаІБබаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶Еඐඁඌථථඌඃඊ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ча¶£аІНа¶°а¶ЧаІЛа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶ХаІЗ а¶Жа¶Ба¶Іа¶Ња¶∞ а¶∞ඌටаІЗ පаІНඐපаІБа¶∞а¶ђа¶Ња¶°а¶ЉаІА ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶∞ඌට а¶Ха¶Ња¶Яа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶њ බаІВа¶∞аІЗ а¶Па¶Х а¶єа¶Ња¶З а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ђа¶ња¶≤аІЗа•§ а¶∞ඌටаІЗ а¶≠аІАа¶Ја¶£ а¶Эа¶°а¶Љ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶∞аІВඥඊ а¶Жа¶Ъа¶∞а¶£аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІБа¶ХаІЗ а¶У а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗබගථ ඪඌට-а¶Єа¶Ња¶Ча¶∞аІЗа¶∞ ඥаІЗа¶Й!
а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶∞ඌට а¶ђа¶∞ а¶ХаІЛඕඌඃඊ а¶ђа¶∞ а¶ХаІЛඕඌඃඊ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶™а¶Ња¶ѓа¶Ља¶®а¶ња•§ а¶ђа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ-а¶ђа¶Ња¶°а¶ЉаІАටаІЗ а¶П ථගඃඊаІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ѓа¶єа¶Њ а¶Жа¶≤аІЛа¶°а¶Ља¶®а•§ а¶≠а¶Ња¶ЧаІНа¶ѓа¶ња¶Є а¶ђа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ ඙ධඊඌථаІЛ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ вАУ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶З а¶Єа¶ђа¶Ња¶З ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤, ඙ඌа¶ЦаІАа¶ХаІЗ පගа¶Ха¶≤ ඙а¶∞ඌථаІЛ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Жа¶∞ටаІЛ а¶ЙධඊටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ ථඌ, а¶Ца¶Ња¶Ба¶Ъа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ЖඪටаІЗа¶З а¶єа¶ђаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗа•§
а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ඌට а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ а¶Эа¶°а¶Љ а¶Жа¶∞ ඁථаІЗа¶∞ а¶Эа¶°а¶ЉаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ѓаІБබаІНа¶І а¶Ха¶∞аІЗ а¶≠аІЛа¶∞аІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶ЯаІЗа¶ђа¶ња¶≤аІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶ШаІБа¶Ѓа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ ඙ධඊаІЗа¶Ыа¶ња•§ ඙аІНа¶∞ඌටа¶Га¶≠аІНа¶∞а¶Ѓа¶£а¶∞ට බаІБ’а¶Па¶Ха¶Ьථ පаІНඐපаІБа¶∞а¶ђа¶Ња¶°а¶ЉаІАа¶∞ а¶≤аІЛа¶Х а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶П а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌඃඊ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ පаІЗа¶Ј ඙а¶∞аІНඃථаІНට ථගඃඊаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗථ ඁඌථа¶≠а¶ЮаІНа¶ЬථаІЗа¶∞ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ බаІГපаІНа¶ѓаІЗ а¶ЕඐටаІАа¶∞аІНа¶£ а¶єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а•§
඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ЕඐපаІНа¶ѓа¶њ පаІНඐපаІБа¶∞а¶ђа¶Ња¶°а¶ЉаІАටаІЗ ඃටඐඌа¶∞а¶З а¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶њ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђа¶Ња¶Іа¶Њ ටаІЗ බаІВа¶∞аІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ЈаІЗ а¶Х’බගථ ඕඌа¶Хටඌඁ а¶Ча¶≤а¶Ња¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Пඁථ ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ ආаІЗа¶Хට а¶ѓаІЗ බඪаІНටа¶∞ඁට ඙ථаІЗа¶∞-ඐගප බගථ а¶Ча¶≤а¶Ња¶ХаІЗ ඐගපаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ බගටаІЗ а¶єа¶§а•§
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඙аІБටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶Вඐඌබ ඙ඌа¶З а¶Ха¶≤а¶Ха¶Ња¶§а¶Ња¶ѓа¶Ља•§ а¶Ха¶Ња¶Ьගබඌа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬа¶Ха¶Ња¶Ьගබඌ а¶Жа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Еа¶ЄаІАа¶Ѓ а¶ЕථаІБа¶Ха¶ЃаІН඙ඌඃඊ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶Х а¶ЦаІЛа¶Ха¶Њ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ша¶∞аІЗ, а¶Ж඙ථග ඃබග а¶ЦаІЛа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථඌඁа¶Ха¶∞а¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§вАЭ а¶Ѓа¶єа¶Њ а¶Йа¶≤аІНа¶≤ඌඪගට а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ බаІБ’බථаІНа¶° а¶ЪаІЛа¶Ц а¶ђаІБа¶Ба¶ЬаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Йආа¶≤аІЗථ, вАЬа¶ЦаІЛа¶Ха¶Ња¶∞ ථඌඁ а¶∞а¶За¶≤ а¶ЃаІЛа¶ЄаІНට඀ඌ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶Ња¶≤а•§ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ .ඁටаІЛа¶З а¶ѓаІЗථ а¶Па¶Хබගථ බаІЗප а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ вАУ а¶¶аІЗපаІЗа¶∞ а¶Еථඌа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Еа¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞а¶ХаІЗ බа¶≤ගට ඁඕගට а¶Ха¶∞аІЗ ථаІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ – а¶Жа¶∞ а¶°а¶Ња¶Х ථඌඁ а¶∞а¶За¶≤ බаІЛබаІБа¶≤а•§вАЭ а¶Па¶З බаІЛබаІБа¶≤а¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ ඙ඌа¶≤а¶ЯаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓа•§
а¶Уа¶∞ а¶ђа¶ѓа¶Ља¶Є а¶ѓа¶Цථ ටගථ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ ටа¶Цථ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌඃඊ а¶Ха¶°а¶ЉаІЗаІЯа¶Њ а¶∞аІЛа¶°аІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶ђа¶Ња¶Єа¶Ња¶ѓа¶Љ ථගඃඊаІЗ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Уа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ඪඌඕаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ටගථ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ පගපаІБ а¶ХаІА а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶ЄаІБа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ча¶Ња¶Зට,-
ටаІНа¶∞а¶ња¶≠аІБඐථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Љ а¶ЃаІЛа¶єа¶ЃаІНඁබ а¶Па¶≤аІЛ а¶∞аІЗ බаІБථගඃඊඌඃඊ
а¶Жа¶ѓа¶Ља¶∞аІЗ а¶Ыа¶Ња¶Ча¶≤ а¶Жа¶Хඌප ඐඌටඌඪ බаІЗа¶Ца¶ђа¶њ ඃබග а¶Жа¶ѓа¶Ља•§
а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶єаІЗа¶ЄаІЗ а¶≤аІБа¶ЯаІЛ඙аІБа¶Яа¶њ!
ටගථ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ පගපаІБ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Чඌබඌ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Єа¶ђа¶ЧаІБа¶≤аІЗа¶Њ а¶Уа¶≤а¶Я ඙ඌа¶≤а¶Я а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤аІЗа¶У а¶ђа¶≤аІЗ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞ට а¶ХаІЛථа¶Яа¶Њ а¶Ха¶њ а¶Чඌථ а¶Па¶ђа¶В а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶Жа¶∞аІЛ а¶Еа¶ђа¶Ња¶Х а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶П а¶ђа¶ѓа¶Ља¶ЄаІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶ѓаІЗඁථ “а¶Еа¶∞аІБа¶£ а¶∞а¶ђа¶њ а¶Йආа¶≤, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ШаІБа¶Ѓ а¶ЫаІБа¶Яа¶≤” а¶ЗටаІНඃඌබග а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЃаІБа¶Ца¶ЄаІНඕ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞ට а¶ЄаІЗа•§
а•§а•§ ඙а¶≤аІНа¶≤аІА а¶Єа¶Ва¶ЧаІАටаІЗ а••
а¶Ха¶Ња¶Ьගබඌ ටа¶Цථ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЛа¶ЂаІЛථ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථаІАа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Чඌථ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶ЩаІБа¶∞а¶ђа¶Ња¶≤а¶Њ, а¶ЗථаІНබаІБа¶ђа¶Ња¶≤а¶Њ, а¶єа¶∞ගඁටаІА, а¶Хඌථථ බаІЗа¶ђаІА, а¶Ха¶Ѓа¶≤ а¶Эа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ, а¶ІаІАа¶∞аІЗථ බඌඪ, а¶Ха¶Ѓа¶≤ බඌපа¶ЧаІБ඙аІНට, а¶ЃаІБа¶£а¶Ња¶≤а¶ХඌථаІНටග а¶ШаІЛа¶Ј а¶Єа¶ђа¶Ња¶З ටඌа¶∞ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ вАЬа¶Ха¶ња¶Й’ а¶≤а¶Ња¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Уබගа¶ХаІЗ а¶За¶Єа¶≤а¶Ња¶ЃаІА а¶Чඌථ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Њ а¶Хට а¶≤а¶ња¶Ца¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶ња¶У බаІБ’බගථ а¶Ъа¶Ња¶∞බගථ බපබගථ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶У а¶Чඌථ ඙ඌа¶З а¶®а¶Ња•§
а¶ЗටаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶∞аІЗ а¶Ха¶ђа¶њ а¶ЧаІЛа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ЃаІЛа¶ЄаІНට඀ඌа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЧаІЗа¶У а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ѓа¶Љ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶Ѓа¶Ња¶За¶ХаІЗа¶≤ а¶єаІЛа¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶≤аІЗ ටගථග ඕඌа¶ХටаІЗа¶®а•§ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓ ටගථගа¶У а¶Єа¶Ва¶ЧаІАටа¶ЬаІНа¶Юа•§ а¶Чඌථ а¶ЬඌථаІЗа¶®а•§ а¶Чඌථ а¶≤аІЗа¶ЦаІЗථа¶Уа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЧаІЗ ටගථග а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЛа¶ЂаІЗථ а¶ЄаІНа¶ЯаІБа¶°а¶ња¶УටаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Чඌථа¶У а¶Жа¶Я බа¶∞පа¶Цඌථඌ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ බගඃඊаІЗа¶У а¶Ха¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ха¶Цඌථඌ а¶Чඌථ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Ха¶∞а¶Ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ටගථගа¶У а¶ЙаІОඪඌයගට а¶єа¶≤аІЗа¶®а•§
а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЛа¶ЂаІЛථ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶°аІЗа¶∞ ඙ඌа¶За¶Ха¶Ња¶∞аІА ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපа¶Х а¶Ѓа¶ња¶Г а¶ЬаІЗ, а¶Пථ, බඌඪ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථаІА а¶ЦаІБа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§ ථඌඁ බගа¶≤аІЗථ ටඌа¶∞ а¶ЃаІЗа¶Ча¶Ња¶ЂаІЛථ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථаІА а•§ а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ගඪථ а¶∞аІЛа¶°аІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ බаІЛа¶Хඌථ а¶У а¶∞а¶ња¶єа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶≤ а¶∞аІБа¶Ѓ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶єа¶ња¶Ь а¶Ѓа¶Ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶≠а¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЕථаІБඁටග ථගඃඊаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ѓа¶Ља¶Цඌථඌ а¶Чඌථ ටගථග а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶Ьගබඌа¶∞ ඙аІНа¶∞ඪගබаІНа¶І а¶Чඌථ вАЬටаІЛа¶∞а¶Њ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ѓа¶Њ а¶Жඁගථඌ а¶Ѓа¶Ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ а¶ХаІЛа¶≤аІЗвАЭ вАУ а¶ЃаІЗа¶Ча¶Ња¶ЂаІЛථаІЗ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Чඌථ а¶Ха¶Ња¶Ьගබඌ а¶ЦаІБа¶ђа¶З ඙а¶ЫථаІНබ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ ටඌа¶З вАЬථබаІАа¶∞ ථඌඁ а¶Єа¶З а¶Ха¶ЪаІБа¶ѓа¶Ља¶Њ, а¶Ѓа¶Ња¶Ы а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЫаІБа¶ѓа¶Ља¶ЊвАЭ а¶Жа¶∞ вАЬටаІЛа¶∞а¶Ја¶Њ ථබаІАа¶∞ ඙ඌа¶∞аІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶≤аІЗ බගබගа¶≤аІЛ ඁඌථඪඌа¶З ථබаІАа¶∞ ඙ඌа¶∞аІЗвАЭ а¶Па¶З බаІБ’а¶Цඌථඌ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶∞аІЗ ටගථග а¶ЃаІЗа¶Ча¶Ња¶ЂаІЛථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶≤а¶ња¶Ца¶≤аІЗථ, вАЬථබаІАа¶∞ ථඌඁ а¶Єа¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ьථඌ ථඌа¶ЪаІЗ ටаІАа¶∞аІЗ а¶Ца¶ЮаІНа¶ЬථඌвАЭ, а¶Жа¶∞ вАЬ඙බаІНඁබаІАа¶Ша¶ња¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞аІЗ а¶Іа¶Ња¶∞аІЗвАЭ а¶Па¶З බаІБ’а¶Цඌථඌ а¶Ча¶Ња¶®а•§
а¶Зටගඁ඲аІНа¶ѓаІЗ а¶≠а¶Ња¶Яа¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤аІА а¶ЄаІБа¶∞аІЗ вАЬа¶Р а¶ѓаІЗ а¶≠а¶∞а¶Њ ථබаІАа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ба¶ХаІЗ а¶ХඌපаІЗа¶∞ ඐථаІЗа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶ХаІЗ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶ХаІЗвАЭ а¶Чඌථа¶ЦඌථගටаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЫаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶≠а¶Ња¶Яа¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤аІАа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶Ьගබඌа¶∞ а¶∞а¶Ъථඌ а¶У а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІНа¶ѓ а¶ЄаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඙аІНа¶∞ඕඁ ථඌඁ а¶Ха¶∞а¶ња•§ ඙а¶≤аІНа¶≤аІАа¶ЧаІАටගа¶∞ а¶Ча¶Ња¶ѓа¶Ља¶Х а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථඌඁ а¶ѓа¶Цථ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ а¶Ыа¶°а¶Ља¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ ඙ධඊаІЗа¶ЫаІЗ ටа¶Цථ ඙а¶≤аІНа¶≤аІАа¶Ха¶ђа¶њ а¶Ьа¶Єа¶ња¶Ѓа¶ЙබаІНබගථ ථගа¶ЬаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Па¶Хබගථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Па¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ вАЬථබаІАа¶∞ ථඌඁ а¶Єа¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ьථඌ ථඌа¶ЪаІЗ ටаІАа¶∞аІЗ а¶Ца¶ЮаІНа¶ЬථඌвАЭ а¶ґаІБථаІЗ ටගථග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓаІЗ а¶Хඐගටඌ а¶∞а¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ вАЬа¶ХаІЛථ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ьථඌ, ටаІАа¶∞аІЗ а¶Ца¶ЮаІНа¶Ьථඌ ඙ඌа¶ЦаІАа•§вАЭ а¶Ьа¶Єа¶ња¶Ѓ ටඌа¶∞ а¶ЃаІНа¶ђа¶≠ඌඐඪගබаІНа¶І а¶ЧаІЗа¶Ба¶ѓа¶ЉаІЛ а¶Хඕඌа¶∞ а¶Ьа¶Ња¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђаІЗа¶Ба¶ІаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶≤а•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ ටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Чඌථ а¶Ча¶Ња¶За¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬа¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ча¶єаІАථ а¶Ча¶Ња¶ЩаІЗа¶∞ ථඌа¶За¶ѓа¶Ља¶ЊвАЭ а¶§а¶Ња¶∞඙а¶∞ а¶Ча¶Ња¶За¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬа¶У а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බа¶∞බаІА а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Ьඌථа¶≤аІЗ ටаІЛа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ща¶Њ ථаІМа¶Ха¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Ъධඊටඌඁ а¶®а¶Ња•§вАЭ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Єа¶Ња¶°а¶Ља¶Њ ඙ධඊаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§
а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶∞ а¶Ьа¶Єа¶ња¶Ѓ බаІБа¶За¶ЬථаІЗ ටа¶Цථ а¶Па¶Х а¶Еа¶≠ගඃඌථ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶За¶Йථගа¶≠а¶Ња¶∞аІНа¶Єа¶ња¶Яа¶њ а¶ЗථඣаІНа¶Яа¶ња¶Яа¶ња¶Йа¶ЯаІЗ, а¶ЄаІНа¶Ха¶Яගපа¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶Ъ а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗ а¶Єа¶≠а¶Њ а¶≠аІЗа¶ХаІЗ а¶≠а¶Ња¶Яа¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤аІА а¶Чඌථ පаІЛа¶®а¶Ња¶§а¶Ња¶Ѓа•§ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Єа¶Ња¶°а¶Ља¶Њ ඙ඌа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶®а¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බа¶≤аІЗ а¶ѓаІЛа¶Ч බගа¶≤аІЗථ а¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ ඐඌයඌබаІБа¶∞ а¶Ца¶ЧаІЗථ ඁගටаІНටගа¶∞, а¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ ඐඌයඌබаІБа¶∞ බаІАථаІЗප а¶ЄаІЗථ, а¶ЧаІБа¶∞аІБඪබඃඊ බටаІНට, а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶З බගථ බගථ ඙а¶≤аІНа¶≤аІАа¶ЧаІАටගа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ පаІНа¶∞බаІНа¶Іа¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶ђ а¶ЬаІЗа¶ЧаІЗ а¶Йආа¶≤а•§
а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌඃඊа¶З а¶Па¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єа¶≤ а¶Єа¶ђа¶Ъа¶Ња¶ЗටаІЗ а¶ђаІЗපаІА а•§ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ පටа¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЖපаІА а¶≠а¶Ња¶Ч а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞а¶З а¶ђа¶Ња¶°а¶ЉаІА ඙а¶≤аІНа¶≤аІА а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа•§ ටඌа¶∞а¶Њ а¶∞аІБа¶Ьа¶њ- а¶∞аІЛа¶Ьа¶Ча¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌඃඊ а•§ ඁථ ඙ධඊаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ බаІЗපаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ЯගටаІЗа•§ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶°, а¶∞аІЗа¶°а¶ња¶Уа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶ѓа¶Цථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶£аІНආаІЗ а¶ІаІНඐථගට а¶єа¶≤ ඙а¶≤аІНа¶≤аІАа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЃаІЗආаІЛ а¶ЄаІБа¶∞ ඙ඕа¶Ъа¶Ња¶∞аІА බඌа¶Ба¶°а¶Ља¶Ња¶≤ ඕඁа¶ХаІЗ! а¶Па¶Ха¶њвА¶ а¶П а¶ЄаІБа¶∞аІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථඌධඊаІАа¶∞ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶ЧвА¶ а¶Па¶Ха¶њ а¶ђа¶Ња¶£аІА, а¶П а¶ѓаІЗ බаІЗа¶Ца¶њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£аІЗа¶∞а¶З ඙аІНа¶∞ටග඲аІНඐථග а•§
඙а¶≤аІНа¶≤аІА а¶Єа¶Ва¶ЧаІАටаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶Хඌප ඐඌටඌඪ ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶єа¶≤ а¶ЄаІБа¶∞පаІНа¶∞аІАа¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶І а•§
඙а¶≤аІНа¶≤аІАа¶ЧаІАටගа¶∞ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶°а¶У а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗ а¶Па¶Х ථටаІБථ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶°аІЗа¶∞ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Ха¶∞а¶≤а•§ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶Ьඌට а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶У а¶П а¶Чඌථ ඐගපаІЗа¶Ј а¶ЖබаІГට යටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤а•§ а¶ЫඌටаІНа¶∞බаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶єа¶≤аІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶°а¶Ња¶Х а¶™а¶°а¶Ља¶§а•§ а¶ЖඪටаІЗ а¶Жа¶∞а¶ЃаІНа¶≠ а¶Ха¶∞а¶≤ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶Яа¶ња¶Йа¶ґа¶®а¶ња•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ а¶Ъа¶≤аІНа¶≤ගප ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌප а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња•§ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶Яа¶ња¶Йපථග а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ а¶ђаІЈ ඪ඙аІНටඌයаІЗ බаІБ’බගථ а¶Па¶Х а¶Ша¶£аІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа•§ බаІБ’а¶ЯаІЛ ටගථа¶ЯаІЗ а¶Яа¶ња¶Йපථග ථගа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Є ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ѓаІЗа¶З ඁථаІЗ යට а¶Жа¶Ь а¶П а¶Яа¶ња¶ЙපථගටаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, ඁඌඕඌඃඊ а¶ѓаІЗථ а¶ђа¶Ња¶Ь а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ а¶™а¶°а¶Ља¶§а•§ ඁථаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ, ආගа¶Х а¶Па¶Х а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶Яа¶ња¶Йපථග а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЫඌටаІНа¶∞аІАа¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ ථගඃඊаІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶њ, вАЬа¶Ѓа¶Ња¶Ђ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗථ, а¶Яа¶ња¶Йපථග а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ, ටඐаІЗ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ ථගඃඊаІЗ ථඃඊ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ ථගа¶≤аІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ආගа¶Х බගථ а¶У ඪඁඃඊඁට а¶ЖඪටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶Па¶З а¶ђа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ђа¶Ња¶Іа¶Хටඌа¶∞ а¶∞аІЗа¶≤-а¶≤а¶Ња¶ЗථаІЗа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞ බගඃඊаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶ЃаІВа¶≤аІНඃඐඌථ බගථа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶ХаІЗ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђ а¶®а¶Ња•§ ටඐаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶Єа¶ђ, а¶Чඌථ පගа¶Ца¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђ а¶ѓаІЗබගථ а¶ѓа¶Цථ ඁථ а¶Ъа¶Ња¶ѓа¶Љ, а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђ а¶®а¶Ња•§вАЭ
а¶≠а¶Ња¶Яа¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤аІА а¶Чඌථ ටа¶Цථ а¶ђаІЗප а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Љ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁථаІЗ а¶Па¶≤ а¶Па¶Х ථටаІБථ а¶Ха¶≤аІН඙ථඌ а•§ а¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶єа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ ඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХඌථаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ЄаІБа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Эа¶Ва¶Ха¶Ња¶∞ ටаІБа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗ а¶єа¶≤ а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Ња•§ а¶Па¶З а¶ЄаІБа¶∞аІЗ а¶Чඌථ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Ѓа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Йආа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЛа¶ЂаІЛථ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථаІАа¶∞ а¶Ха¶∞аІНටඌ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Чඌථ? а¶Уа¶Єа¶ђ а¶Жа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶ња¶Х а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ а¶Ъа¶≤а¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§вАЭ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° ටа¶Цථ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗ а¶ПථаІЗа¶ЫаІЗ ථඐඐගඪаІНа¶Ѓа¶ѓа¶Љ, а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථаІА а¶≤аІБа¶Яа¶ЫаІЗ а¶ЃаІЛа¶Яа¶Њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ, а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Жඐබඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶Па¶Хබඁ а¶Йа¶°а¶Ља¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶У බගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗа¶У а¶Па¶Х а¶°а¶ња¶ЧаІНа¶∞аІА ථаІАа¶ЪаІЗ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶ЖඪටаІЗ а¶єа¶≤а•§ а¶ѓаІЗ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶£аІА а¶Ыа¶ња¶≤:
ටаІЛа¶∞а¶Ја¶Њ ථබаІАа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞аІЗ а¶Іа¶Ња¶∞аІЗ а¶У
බගබගа¶≤аІЛ ඁඌථඪඌа¶З ථබаІАа¶∞ ඙ඌа¶∞аІЗ
а¶Уа¶Ха¶њ а¶ЄаІЛථඌа¶∞ а¶ђа¶Ба¶ІаІБ а¶Чඌථ а¶Ха¶∞а¶њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶У
බගබග ටаІЛа¶∞аІЗ а¶Ха¶њ а¶Ѓа¶∞аІЗ
а¶Ха¶њ පаІЛථаІЗа¶∞ බගබග а¶Уа••
а¶ЄаІЗ а¶Чඌථ බඌа¶Ба¶°а¶Ља¶Ња¶≤ а¶Па¶З а¶∞а¶Ха¶Ѓ:
ටаІЛа¶∞а¶Ја¶Њ ථබаІАа¶∞ ඙ඌа¶∞аІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶У
බගබගа¶≤аІЛ ඁඌථඪඌа¶З ථබаІАа¶∞ ඙ඌа¶∞аІЗ
а¶Жа¶Ьа¶њ а¶ЄаІЛථඌа¶∞ а¶ђа¶Ба¶ІаІБ а¶Чඌථ а¶ЧаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶У
බගබග ටаІЛа¶∞ ටа¶∞аІЗ а¶Ха¶њ а¶ЃаІЛа¶∞ ටа¶∞аІЗ
а¶Ха¶њ පаІЛථаІЗа¶Х බගබග а¶Уа•§а•§
ටаІЛа¶∞а¶Ја¶Њ ථа¶∞аІНබаІА вАУ а¶Ца¶∞а¶ЄаІНа¶∞аІЛටඌ а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я ඙ඌයඌධඊаІА ථබаІА ටаІЛа¶∞а¶Ја¶Њ вАУ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙ඌබඁаІВа¶≤ а¶ІаІМට а¶Ха¶∞аІЗ ටа¶∞ටа¶∞ а¶ђаІЗа¶ЧаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶∞а¶њ ටаІАа¶∞аІЗ ටаІАа¶∞аІЗ а¶Чඌථ а¶ЧаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ а¶ЃаІЛа¶ЈаІЗа¶∞ ඙ගආаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЛටඌа¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЃаІЗа¶Ја¶Ъа¶Ња¶≤а¶Х а¶ЃаІИපඌа¶≤аІЗа¶∞ බа¶≤а•§ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶£аІНආаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ђаІЗа¶≤а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶£аІНආаІЗ а¶ђаІЗа¶Ба¶ІаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Ња•§ ටඌබаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁඌටаІГа¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња•§ ඁඌටаІГа¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶ХаІЗ а¶Еа¶ђа¶ња¶ХаІГට а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶Чඌථ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶®а¶Ња•§ ඁථаІЗ а¶ЬаІЗа¶ЧаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠а•§ а¶Па¶З а¶Чඌථ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єа¶ђа¶Ња¶∞ ටගථ а¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Є ඙а¶∞аІЗ а¶ЃаІНඃඌථаІЗа¶Ьа¶Ња¶∞а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶ЄаІНඐටа¶Г඙аІНа¶∞а¶ђаІГටаІНට а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶Жа¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ а¶Р а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Чඌථа¶З а¶¶а¶ња¶®а•§вАЭ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬබගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ а¶Па¶Х පа¶∞аІНටаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බаІЗපаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶ХаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶Еа¶ђа¶ња¶ХаІГටа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа•§вАЭ а¶§а¶ња¶®а¶њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ඐගබаІНа¶∞аІЛа¶є а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬබаІЗа¶ЦаІБථ, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බаІЗපаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶У а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІЗ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ а¶∞а¶В඙аІБа¶∞, බගථඌа¶Ь඙аІБа¶∞; а¶ђа¶ЧаІБа¶°а¶Ља¶Њ, а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБа¶°а¶Ља¶њ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶Єа¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ђа¶єаІБ а¶Ьа¶Ња¶ѓа¶Ља¶Ча¶Ња¶∞ а¶Ьථඪඌ඲ඌа¶∞а¶£а•§ ටඌ а¶Ыа¶Ња¶°а¶Ља¶Њ а¶ЄаІЗ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ, а¶Жа¶ЫаІЗ ඪඌයගටаІНа¶ѓ, а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶ђа¶ЬථаІАථ а¶Жа¶ђаІЗබථ, а¶Жа¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ а¶Па¶Ха¶Цඌථඌ බගඃඊаІЗа¶З බаІЗа¶Ца¶њ ථඌ!вАЭ а¶§а¶Ња¶∞඙а¶∞ а¶Ча¶Ња¶За¶≤а¶Ња¶Ѓ вАЬа¶Уа¶Ха¶њ а¶Ча¶Ња¶°а¶Ља¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤ а¶≠а¶Ња¶З а¶Хට а¶∞а¶ђ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඙ථаІНඕаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶∞аІЗа•§вАЭ а¶Ча¶Ња¶За¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬ඀ඌථаІНබаІЗ ඙ධඊගඃඊඌ а¶ђа¶Ча¶Њ а¶ХඌථаІНබаІЗа•§вАЭ а¶Па¶Єа¶ђ а¶ЧඌථаІЗ පаІБа¶ІаІБ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶Ва¶ЧаІЗ ථඃඊ, а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Ьа¶Ња¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ඐග඙аІБа¶≤ а¶Жа¶≤аІЛа¶°а¶Ља¶®а•§ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶Ва¶ЧаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶ѓа¶Љ а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Чඌථа¶З ථඃඊ а¶П-а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶ѓа¶Љ ඙ඌа¶Ба¶Ъа¶Цඌථඌ ථඌа¶Яа¶Ха¶У а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Ха¶∞а¶њ вАУ а¶Ѓа¶ІаІБа¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Њ, а¶Ѓа¶∞аІБа¶Ъඁටග а¶ХථаІНа¶ѓа¶Њ, а¶єа¶≤බаІА-පඌථඌа¶З а¶У а¶Ѓа¶єаІБа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ЄаІБථаІНබа¶∞аІАа•§ а¶Па¶∞ а¶Єа¶ђ а¶Ха¶ѓа¶Ља¶Яа¶ња¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЫаІЛа¶Я а¶≠а¶Ња¶З а¶ЖඐබаІБа¶≤ а¶Ха¶∞а¶ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а•§ ටඌа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶ђа¶єаІБ а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Чඌථа¶У а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§
а¶П а¶Чඌථ ඙аІНа¶∞ටග а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ а¶ђа¶Ња¶∞ යටаІЗ а¶Жа¶∞а¶ЃаІНа¶≠ а¶Ха¶∞а¶≤а•§ ටа¶Цථ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБඐඌථаІНа¶Іа¶ђ а¶Па¶ђа¶В а¶Ча¶Ња¶ѓа¶Ља¶ХබаІЗа¶∞ а¶ПථаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ බගඃඊаІЗ а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶ЉаІЈ а¶Чඌථ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Ха¶∞ඌටаІЗ а¶Жа¶∞а¶ЃаІНа¶≠ а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Ха¶Ѓа¶≤ බඌපа¶ЧаІБ඙аІНට а¶Па¶Хබගථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶Жа¶ђаІНа¶ђа¶Ња¶Є ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶Пට а¶ђаІЛа¶Ха¶Њ а¶ХаІЗථ? ටаІБа¶Ѓа¶њ ටаІЗ! а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ЧඌථаІЗ а¶Єа¶ЃаІНа¶∞а¶Ња¶Я, ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶њ а¶Йа¶Ъගට а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ බаІЗප ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶≤аІЛа¶Ха¶ХаІЗ ථගඃඊаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙ඕаІЗ ඙аІНа¶∞ටගබаІНඐථаІНබаІНа¶ђаІА බඌа¶Ба¶°а¶Љ а¶Ха¶∞ඌථаІЛ?вАЭ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶њ, вАЬඐගපඌа¶≤ а¶Па¶З а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ බаІЗපаІЗ а¶Ча¶Ња¶ѓа¶Ља¶Х-а¶Ча¶Ња¶ѓа¶Ља¶ња¶Ха¶Њ а¶Хට а¶Ыа¶°а¶Ља¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Еථඌа¶ШаІНа¶∞ඌට ඙аІБа¶ЄаІН඙аІЗа¶∞ ඁට а¶Ча¶Ња¶Ба¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ча¶Ња¶Ба¶ѓа¶ЉаІЗ ථඌඁයඌа¶∞а¶Њ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ ටඌа¶∞а¶Њ, а¶ЧаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жබа¶∞ ටаІЛ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶З а¶Ха¶∞а¶ђ а¶≠а¶Ња¶За•§ ථඌඁ, ඃප, а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටගа¶∞ ඙ඕаІЗ ටаІЛ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶З ටඌබаІЗа¶∞ ථගඃඊаІЗ а¶Жа¶Єа¶ђа•§ ටඌ а¶Ыа¶Ња¶°а¶Ља¶Њ, а¶≠аІАඁථඌа¶ЧаІЗа¶∞ ඪථаІНබаІЗපаІЗа¶∞ බаІЛа¶ХඌථаІЗа¶∞ ඙ඌපаІЗ а¶ЫаІБ’а¶Ъа¶Ња¶∞а¶ЯаІЗ බаІЛа¶Хඌථ ථඌ а¶єа¶≤аІЗ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ђаІБа¶Эа¶ђаІЗ а¶Ха¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ а¶≠аІАඁථඌа¶ЧаІЗа¶∞ ඪථаІНබаІЗපа¶З а¶Єа¶ђа¶Ъа¶Ња¶ЗටаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа•§вАЭ
а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶За¶Єа¶ђ а¶Ча¶Ња¶ѓа¶Ља¶ХබаІЗа¶∞ ටаІЗටа¶∞ ථඌඃඊаІЗа¶ђ а¶Жа¶≤аІА (а¶ЯаІЗ඙аІБ), а¶ХаІЗපඐ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶£, а¶ІаІАа¶∞аІЗථ а¶ЪථаІНබ а¶У а¶ЄаІБа¶∞аІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ а¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ђа¶ЄаІБථගඃඊඌа¶∞ а¶Чඌථ а¶Жа¶Ьа¶У а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђаІЗප а¶Ха¶Ња¶Яа¶§а¶ња•§
а¶Па¶З а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Чඌථ а¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗ а¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ බගථаІЗа¶∞ а¶Ша¶Яථඌ ඁථаІЗ ඙ධඊаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ පаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓа¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ХаІЛථ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶Єа¶≠а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Па¶Хබඌ ටබඌථаІАථаІНටථ ඁථаІНටаІНа¶∞аІА පаІНа¶∞аІА ථа¶≤ගථаІАа¶∞а¶ЮаІНа¶Ьථ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕගට а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЛ а¶Ча¶Ња¶За¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ථගඁථаІНටаІНа¶∞а¶£ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Єа¶≠ඌ඙ටග а¶Еа¶ЃаІГටඐඌа¶Ьа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙ඌබа¶Х පаІНа¶∞аІАටаІБа¶Ја¶Ња¶∞а¶Ха¶Ња¶ЄаІНටග а¶ШаІЛа¶Ја•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕගටගа¶Яа¶Њ ඐගපаІЗа¶Ј а¶Ха¶Ња¶ЃаІНа¶ѓ а¶ђа¶≤аІЗ ඁථаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Йආа¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬබаІЗа¶ЦаІБථ ඃබග а¶Ж඙ථඌа¶∞а¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඁථаІЗ ථඌ а¶Ха¶∞аІЗථ ටඌයа¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶ња•§ а¶Єа¶≠а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶ЄаІВа¶ЪаІАටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЙබаІНа¶ђаІЛ඲ථаІА-а¶Єа¶Ва¶ЧаІАට а¶Па¶ђа¶В ඐගබඌඃඊ-а¶Єа¶Ва¶ЧаІАට а¶Ча¶Ња¶За¶ђа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЕථаІНඃටаІНа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Жа¶ЫаІЗ, ටඐаІЗ බඃඊඌ а¶Ха¶∞аІЗ ඃබග а¶ЕථаІБඁටග а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ЙබаІНа¶ђаІЛ඲ථаІА а¶Єа¶Ва¶ЧаІАටаІЗа¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶З а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Цඌථඌ а¶Чඌථ а¶ЧаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђа•§вАЭ а¶Па¶Хඕඌඃඊ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶Єа¶Ња¶ѓа¶Љ බගа¶≤а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ а¶Ча¶Ња¶За¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶Ха¶Цඌථඌ а¶≠а¶Ња¶Яа¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤аІАа•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ ‘඀ඌථаІНබаІЗ ඙ධඊගඃඊඌ а¶ђа¶Ча¶Њ а¶ХඌථаІНබаІЗ а¶∞аІЗа•§вАЭ а¶Па¶З а¶Чඌථа¶Цඌථඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶ХаІЈ බගඃඊаІЗ а¶Чඌථа¶Яа¶Њ а¶Ча¶Ња¶За¶≤а¶Ња¶Ѓа•§
а¶Єа¶≠ඌ඙ටග ටаІБа¶Ја¶Ња¶∞а¶Ха¶Ња¶ЄаІНටග а¶ШаІЛа¶Ј ඁපඌඃඊ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Шථ а¶Шථ а¶∞аІВа¶Ѓа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶ЃаІБа¶Ыа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Чඌථ පаІЗа¶Ј а¶єа¶≤аІЗ ටගථග а¶ЙආаІЗ а¶∞аІЛа¶∞аІБබаІНඃඁඌථ а¶Ха¶£аІНආаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Йආа¶≤аІЗථ, вАЬа¶Ж඙ථඌа¶∞а¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ХаІНа¶Ја¶Ѓа¶Њ.а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶Ь а¶П а¶Єа¶≠а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ъа¶Ња¶≤ඌටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђ а¶®а¶Ња•§ а¶П а¶Чඌථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Жа¶Ь а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ЙථаІНඁථඌ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶ђаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶≠а¶Ња¶За¶ХаІЗ ථගඃඊаІЗ а¶Ъа¶≤а¶≤а¶Ња¶ЃвАЭ а¶Па¶З а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ ඪටඌа¶З ටගථග а¶Жඪථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЙආаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ යඌට а¶Іа¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ ථගඃඊаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶Ъа¶≤аІБථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Еа¶ЃаІГටඐඌа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Єа•§вАЭ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ ථගඃඊаІЗ а¶Па¶З а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶ЉаІЈ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶≠а¶Ња¶≤а¶ња¶Ха¶Њ а¶ѓа¶Њ ටа¶Цථ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ђаІЗа¶∞а¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗ а¶Єа¶ђ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗ ථගа¶≤аІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ха¶≤а¶Ха¶Ња¶∞а¶Цඌථඌ а¶Єа¶ђ බаІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗථ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ආගа¶Хඌථඌ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶Ча¶Ња¶°а¶ЉаІАටаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Ња¶ѓа¶Љ ඙аІМа¶ЫаІЗ බගඃඊаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶®а•§
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶П вАЬ඀ඌථаІНබаІЗ ඙ධඊගඃඊඌ а¶ђа¶Ча¶Њ а¶ХඌථаІНබаІЗ а¶∞аІЗвАЭ а¶ѓа¶Цථ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єа¶ѓа¶Љ, ටа¶Цථ а¶ЄаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Ља¶Ха¶Ња¶∞ а¶єа¶ња¶Ь а¶Ѓа¶Ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶≠а¶ѓа¶ЉаІЗа¶Є ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞ ඙аІБа¶ЄаІНටගа¶Ха¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єа¶ѓа¶Љ:
вАЬа¶ЙටаІНටа¶∞-а¶ђа¶Ва¶Ч а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶Ъඌයගබඌ බගථ බගථ а¶ђаІЗа¶°а¶ЉаІЗа¶З а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ඐගපаІНа¶≤аІЗа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ, а¶Па¶З පаІНа¶∞аІЗа¶£аІАа¶∞ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ ඐගපගඣаІНа¶Я а¶ЄаІБа¶∞ а¶Ыа¶Ња¶°а¶Ља¶Ња¶У а¶∞а¶Ъථඌа¶У а¶ЕථаІНඃටඁ а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£а•§ පගа¶ХаІНඣගට а¶Ха¶ђа¶ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓаІЗ а¶ѓа¶Цථ ඙ධඊග, а¶П-඙ඌа¶∞аІЗ а¶Ъа¶ХаІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶Х а¶У඙ඌа¶∞аІЗ а¶Ъа¶ХаІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶ХаІА, вАШа¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗටаІЗ а¶ђа¶єаІЗ а¶ђа¶ња¶∞යඐඌයගථаІА!вА٠ටа¶Цථ ඁථаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ђаІБබаІНа¶Іа¶њ බගඃඊаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶∞а¶Є а¶Й඙а¶≤а¶ђаІНа¶Іа¶њ а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Еපගа¶ХаІНඣගට а¶Ха¶ђа¶ња¶∞ а¶ЧඌථаІЗ а¶ѓа¶Цථ බаІЗа¶Ца¶њ вАУ вАЬ඀ඌථаІНබаІЗ ඙ධඊගඃඊඌ а¶ђа¶Ча¶Њ а¶ХඌථаІНබаІЗ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞යගථаІА а¶ђа¶ЧаІАа¶∞ а¶Ѓа¶∞аІНа¶Ѓа¶ђаІНඃඕඌඃඊ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Жа¶Хඌප а¶Ыа¶≤а¶Ыа¶≤! ටа¶Цථ а¶Жа¶∞ а¶ђаІБබаІНа¶Іа¶њ ඙аІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЛа¶Ьථ а¶єа¶ѓа¶Љ а¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶ња¶∞а¶єаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶Еටග а¶Єа¶єа¶Ь ඙аІНа¶∞а¶Хඌපа¶ЧаІНа¶≠а¶Ва¶ЧаІА ටаІАа¶∞аІЗа¶∞ ඁට а¶ЄаІЛа¶Ьа¶Њ а¶Па¶ЄаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶∞аІНа¶ЃаІЗ а¶ђаІЗа¶Ба¶ІаІЗа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඁථаІЗ а¶єа¶ѓа¶Љ, ථගа¶∞а¶≤а¶Ва¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶З а¶ђа¶ЄаІНටаІБටඌථаІНටаІНа¶∞а¶ња¶Х ඙аІНа¶∞а¶Хඌපа¶≠а¶Ва¶ЧаІАа¶З а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІНа¶ѓ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ ඐගපаІЗඣටа¶Г а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶Ъඌයගබඌа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£а•§вАЭ
вАЬ඙а¶≤аІНа¶≤аІА-а¶ЧаІАටග а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ බаІБа¶ѓа¶ЉаІЛа¶∞а¶Ња¶£аІА а¶Па¶З а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Ња¶Њ а¶Чඌථа¶ХаІЗ а¶Єа¶∞аІНඐ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Жа¶ђаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђа¶З а¶Жබа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ь-а¶Еа¶ЄаІНටа¶Г඙аІБа¶∞аІЗ а¶°аІЗа¶ХаІЗ а¶Жථа¶≤аІЗа¶®а•§ ටа¶Цථ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЃаІБа¶ЧаІНа¶І а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Й඙аІЗа¶ХаІНඣගට බаІБа¶ѓа¶ЉаІЛа¶∞а¶Ња¶£аІАа¶∞ а¶∞аІВ඙-පаІНа¶∞аІА а¶ЄаІБа¶ѓа¶ЉаІЛа¶∞а¶Ња¶£аІАа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ ට’ а¶Ха¶Ѓ а¶®а¶ѓа¶Ља•§ а¶Па¶ђа¶В ටඌа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЃаІБа¶ЧаІНа¶І а¶єа¶≤а¶Ња¶Ѓ ටඌа¶∞ ථගටඌථаІНට а¶Єа¶∞а¶≤ а¶єаІГබඃඊаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІБа¶∞аІАටаІЗ! а¶Па¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞ а¶∞а¶Єа¶ња¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠ගථථаІНබථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Њ ඙ඌа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Йа¶Ъගට ඙а¶≤аІНа¶≤аІА බаІБа¶≤а¶Ња¶≤ а¶Жа¶ђаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞а•§ а¶ђа¶єаІБ බаІБа¶≤а¶∞аІНа¶≠ а¶≠а¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Чඌථ ටගථග а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ж඙ථඌබаІЗа¶∞ а¶Й඙යඌа¶∞ බගඃඊаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§вАЭ
а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ьගබඌа¶∞ а¶За¶Єа¶≤а¶Ња¶ЃаІА а¶Чඌථ а¶ЧаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶єа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ж඙ඌඁа¶∞ а¶Ьථඪඌ඲ඌа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶єа¶≤а¶Ња¶Ѓ ඙а¶≤аІНа¶≤аІАа¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶Яа¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤аІА, а¶Ьа¶Ња¶∞а¶њ, а¶Єа¶Ња¶∞а¶њ а¶ЃаІБа¶∞аІНපගබඌ, බаІЗයටටаІНටаІНа¶ђ, а¶ђа¶ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗබ, а¶Ъа¶Яа¶Ха¶Њ а¶ХаІНа¶ЈаІАа¶∞аІЛа¶≤ а¶Чඌථ а¶ЧаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶ђа¶Ва¶ЧаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Яа¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤аІА, а¶ђа¶ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗබаІА, а¶ЃаІБපගබඌ а¶ЗටаІНඃඌබග а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶єа¶Х а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЕථаІБа¶Ь඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ѓ පаІНа¶∞аІАа¶Хඌථඌа¶За¶≤а¶Ња¶≤ පаІАа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ъа¶ња¶∞а¶ЛථаІАа•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ ඁඌආаІЗ-а¶Ша¶Ња¶ЯаІЗ а¶Па¶З ඙а¶≤аІНа¶≤аІАа¶ЧаІАටග а¶Ыа¶°а¶Ља¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶≤аІБа¶Ха¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ЕථඌබаІГට а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ ඙ධඊаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Хඌථඌа¶За¶∞ ඪයඌඃඊටඌඃඊ а¶ЄаІЗа¶З а¶єа¶Ња¶∞ඌථаІЛ ඁඌථගа¶Х а¶ЙබаІНа¶Іа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶Па¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Хඌථඌа¶За¶∞ ඁට බаІЛටа¶∞а¶Њ-ඐඌබа¶Х ඙ඌа¶Х-а¶≠а¶Ња¶∞ට а¶Й඙ඁයඌබаІЗපаІЗ а¶ђа¶ња¶∞а¶≤а•§ ටඌа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓ ථඌ ඙аІЗа¶≤аІЗ ඪටаІНа¶ѓа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха¶ЧаІАටග а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗа•§ а¶Жබග а¶У а¶Еа¶ХаІГටаІНа¶∞а¶ња¶Ѓ ඙а¶≤аІНа¶≤аІАа¶ЧаІАටගа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶∞а¶Ва¶Ъа¶В а¶≤а¶Ња¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ха¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ха¶Ьථ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х ඙а¶≤аІНа¶≤аІАа¶Ха¶ђа¶ња¶∞ а¶Чඌථа¶У а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶њ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ѓа¶Цථ ඪටаІНа¶ѓа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЯаІНа¶∞ඌධගපථඌа¶≤ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ ඪථаІН඲ඌථ ඙аІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶њ ටа¶Цථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶Чඌථ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶°аІЗ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ ඐථаІНа¶І а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§
а•• ඪගථаІЗа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЪаІМа¶Хඌආ ඕаІЗа¶ХаІЗ а••
а¶ѓаІМඐථаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЄаІБබа¶∞аІНපථ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶®а•§ ටඌа¶З ඐථаІНа¶ІаІБඐඌථаІНа¶Іа¶ђаІЗа¶∞ а¶ЕථаІБа¶∞аІЛа¶ІаІЗ а¶єа¶Ња¶Уа¶°а¶Ља¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Ьඃඊථඌа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Ља¶£ а¶ђа¶Ња¶ђаІБа¶ХаІЗ ඪඌඕаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶Хබගථ а¶ЬаІНа¶ѓаІЛටගඣ а¶ђа¶Ња¶Ба¶°а¶ЉаІБа¶ѓаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ටගථග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Чඌථ පаІБථаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Њ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶ЦаІБපаІА а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶£аІБа¶Ѓа¶Ња¶ѓа¶Ља¶ЊвАЭ а¶®а¶Ња¶ЃаІЗ а¶Па¶Ха¶Цඌථඌ а¶Єа¶ђа¶Ња¶Х а¶Ыа¶ђа¶њ පаІАа¶Ча¶ЧаІАа¶∞а¶З а¶Іа¶∞а¶ђа•§ а¶Ж඙ථඌа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶ђа¶ЗටаІЗ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞аІНа¶Я බаІЗа¶ђ, ආගа¶Х а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ьа¶Ња¶®а¶Ња¶ђа•§вАЭ а¶Єа¶§аІНа¶ѓа¶њ ඪටаІНа¶ѓа¶њ а¶Ѓа¶Ња¶Єа¶ЦඌථаІЗа¶Х ඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථඌඁаІЗ а¶Па¶Х а¶Ъගආග а¶Па¶≤ а¶Яа¶Ња¶≤а¶ња¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗ ටඌа¶∞ ඪඌඕаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Па¶Ха¶Ша¶∞ а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶≠ගටа¶∞ ටගථග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЧඌථаІЗ ඙ඌප а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓ; ටа¶Цථ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶ЬаІАඐථаІЗ ඕගඃඊаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ а¶Ха¶ЦථаІЛ? а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬටඌ ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶њ вАУ а¶¶аІЗа¶ђа¶≤а¶Њ බаІЗа¶ђаІА, පඌа¶Ьඌයඌථ, ඁගපа¶∞-а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞аІА, а¶∞а¶ња¶Ьа¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ, а¶Жа¶∞аІЛ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђа¶ЗටаІЗ!вАЭ вАЬа¶ЃаІЗа¶ђа¶Ња¶∞ ඙ටථвАЭ а¶ђа¶За¶Цඌථඌ а¶Па¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ බගඃඊаІЗ බаІБвАЩа¶Па¶Ха¶ЯаІЈ а¶Ьа¶Ња¶ѓа¶Ља¶Ча¶Њ ඙ධඊටаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§вА¶ ඙ඌප а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ බаІБ’а¶Цඌථඌ а¶Чඌථ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ ඙ඌа¶∞аІНа¶Я а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Па¶Ха¶Цඌථ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь බගඃඊаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶Па¶Х ඪ඙аІНටඌයаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЄаІБа¶∞ а¶ЯаІБа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗа¶®а•§вАЭ
඙ඌа¶∞аІНа¶Я а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Еа¶Ва¶ХаІБа¶∞аІЗа¶∞а•§ а¶Хඌථථඐඌа¶≤а¶Њ а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£аІЗа¶∞ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Ња¶ѓа¶Љ а•§ ඐගබаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£а¶ХаІЗ а¶Еа¶≠аІНа¶ѓа¶∞аІНඕථඌ а¶Ха¶∞аІЗ ථගඃඊаІЗ а¶ЖඪටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶Чඌථ а•§
а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛа¶Х ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ЫඐගටаІЗ а¶ЕඐටаІАа¶∞аІНа¶£ а¶єа¶≤а¶Ња¶Ѓ! ඁථаІЗ ඁථаІЗ а¶ЄаІНඐ඙аІНථаІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ња¶≤ а¶ђаІБථа¶Ыа¶ња•§ а¶ЬаІНа¶ѓаІЛටගඣ а¶ђа¶Ња¶ђаІБа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ вАУ вАЬа¶ЫඐගටаІЗ ථඌඁа¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙ඌа¶∞ගපаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶ХвА¶вАЭ а¶§а¶ња¶®а¶њ а¶ѓаІЗථ а¶Жа¶Хඌප ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙ධඊа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Йආа¶≤аІЗථ, ‘а¶ђа¶≤ а¶Ха¶њ а¶єаІЗ, а¶ЫඐගටаІЗ ථඌඁටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤аІЗ, а¶Па¶З ටаІЛ ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Я! а¶ѓа¶Ња¶Х а¶Па¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶∞ а¶ЫඐගටаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඙а¶∞аІЗа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶єа¶Ња¶Ба¶Яа¶Ња¶єа¶Ња¶Ба¶Яа¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බаІБ’а¶ЬаІЛа¶°а¶Ља¶Њ а¶ЬаІБටඌ а¶ХаІНа¶Ја¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ – а¶ЪඌථаІНа¶Є а¶Жа¶∞ ඙ඌа¶З а¶®а¶ња•§
а¶Па¶Хබගථ ථඌа¶ЯаІНа¶Яථගа¶ХаІЗටථаІЗ පගපගа¶∞ а¶≠ඌබаІБа¶°а¶ЉаІАа¶∞ ඪඌඕаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ѓа¶Љ а¶єа¶≤а•§ පගපගа¶∞ а¶≠ඌබаІБа¶°а¶ЉаІА ටа¶Цථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ බаІГපаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЧаІНа¶∞аІАථ а¶∞аІБа¶ЃаІЗ а¶ЯаІБа¶Ха¶ЫаІЗа¶®а•§ පගපගа¶∞а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Йආа¶≤аІЗථ, вАЬа¶єаІБа¶Б, а¶≠а¶Ња¶≤ а¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞? а¶Жа¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ а¶Па¶З а¶°аІНа¶∞඙ ඪගථа¶Яа¶Њ ඙ධඊа¶≤аІЗ ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗа¶З а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶ЬаІЗ ඥаІБа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Чඌථ а¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ?вАЭ а¶Ѓа¶єа¶Њ а¶ЂаІНඃඌඪඌබаІЗ ඙ධඊа¶≤а¶Ња¶Ѓ: а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁඌඕඌඃඊ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЧаІЗа¶∞аІБа¶ѓа¶Ља¶Њ ඙ඌа¶Ча¶°а¶ЉаІА а¶ђаІЗа¶Ба¶ІаІЗ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єа¶≤а•§ вАЬа¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ча¶єаІАථ а¶Ча¶Ња¶ЩаІЗа¶∞ ථඌа¶За¶ѓа¶Ља¶ЊвАЭ а¶Чඌථа¶Яа¶Њ а¶Еа¶∞аІНа¶Чඌථ-а¶ђа¶Ња¶Ьа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ආගа¶Х а¶Ха¶∞аІЗ ථගа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶ЧаІБа¶£ а¶ЧаІБа¶£ а¶Ха¶∞аІЗвА¶ ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶°аІНа¶∞඙ ටаІБа¶≤ටаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶ХаІЗ ඥаІБа¶ХටаІЗ а¶єа¶≤а•§ а¶Ча¶Ња¶За¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ПථаІНа¶ХаІЛа¶∞, а¶ПථаІНа¶ХаІЛа¶∞, а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ча¶Ња¶УвА¶ බаІБ’а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ча¶Ња¶За¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ යඌටටඌа¶≤а¶њ а¶Жа¶∞ ඕඌඁаІЗ а¶®а¶Ња•§ පගපගа¶∞а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶ѓаІЗа¶ѓа¶ЉаІЛ ථඌ ඙аІНа¶≤аІЗ පаІЗа¶Ј а¶єа¶≤аІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ХаІЛа¶∞аІЛа•§вАЭ
඙аІНа¶≤аІЗа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶ЧаІНа¶∞аІАථ а¶∞аІБа¶ЃаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶∞а¶В а¶Уආඌа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ЃаІБа¶Ц ඕаІЗа¶ХаІЗ вАУ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶°а¶Љ а¶Ша¶∞аІЗ а¶єа¶Ња¶∞а¶ЃаІЛථගඃඊඌඁ, ටඐа¶≤а¶Њ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єа¶≤ вАУ а¶ђаІБа¶Эа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Чඌථ а¶єа¶ђаІЗа•§ පගපගа¶∞а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ђа¶Єа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗ а¶°а¶Ња¶Ха¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶Ча¶Ња¶У බаІЗа¶Ца¶ња•§вАЭ а¶¶аІБ’ටගථ а¶Цඌථඌ а¶Ча¶Ња¶За¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Йආа¶≤, а¶Па¶∞ а¶Па¶Ха¶Цඌථඌ а¶Чඌථ පаІБථаІБථ вАЬа¶Уа¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶њ ටа¶∞аІА а¶єаІЗඕඌ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Іа¶ђаІЗ ථඌа¶ХаІЛ! а¶Жа¶Ьа¶ХаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ЭаІЗа•§вАЭ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ђа¶≤аІЗ а¶Йආа¶≤ вАУ а¶ђаІЗප а¶ђаІЗа¶ґа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬа¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња•§ ටගථа¶Яа¶Њ පа¶∞аІНට а¶Жа¶ЫаІЗа•§ ඙аІНа¶∞ඕඁ, а¶Па¶З а¶ЧඌථаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ටඐа¶≤а¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶ђаІЗ ථඌ; බаІНඐගටаІАа¶ѓа¶Љ, а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Хඕඌа¶У а¶ХаІЗа¶Й а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗථ ථඌ; ටаІГටаІАа¶ѓа¶Љ, а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЗ! ථගඐගඃඊаІЗ බගටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§вАЭ а¶§а¶•а¶Ња¶ЄаІНа¶§а•§ а¶Чඌථ а¶Жа¶∞а¶ЃаІНа¶≠ а¶єа¶≤а•§вА¶ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ බаІБа¶Яа¶Њ а¶Ха¶≤а¶њ а¶ЧаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶њ, а¶Пඁථ а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ ටඐа¶≤а¶Ъа¶њ ටඐа¶≤а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Ъа¶Ња¶Ба¶Яа¶њ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶≤а•§ а¶Чඌථ ඕඌඁගඃඊаІЗ බගඃඊаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬа¶Жа¶≤аІЛ а¶ЬаІНа¶ђа¶Ња¶≤аІБа¶®а•§вАЭ а¶ґа¶ња¶ґа¶ња¶∞а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶ХаІА, а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞ а¶Ха¶њ? а¶Чඌථ ඕඌඁඌа¶≤аІЗ а¶ХаІЗථ?вАЭ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬපа¶∞аІНට а¶≠а¶Ва¶ЧаІЗа¶∞ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІЗа•§вАЭ вАЬа¶У ටඐа¶≤а¶Њ а¶ђаІЗа¶ЬаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶З а¶ЬථаІНа¶ѓ?вАЭ вАЬආගа¶Х ටඌа¶За•§вАЭ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶Жа¶ЪаІНа¶Ыа•§ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶ђаІЗ ථඌ! а¶Ча¶Ња¶Уа•§вАЭ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬа¶Жа¶Ь а¶Жа¶∞ а¶П а¶Чඌථ а¶єа¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§вАЭ а¶§а¶ња¶®а¶њ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬටඌටаІЗ а¶Ха¶њ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Ча¶Ња¶У!вАЭ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ вАЬа¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ බගа¶≤аІЗа¶У а¶®а¶Ња•§ ටගථග а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ вАЬඃබග බප а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ බගа¶З?вАЭ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬа¶≤а¶Ња¶Ц а¶Яа¶Ња¶Х! බගа¶≤аІЗа¶У а¶Жа¶Ь а¶Жа¶∞ а¶П а¶Чඌථ а¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђ а¶®а¶Ња•§вАЭ
පගපගа¶∞а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђаІБа¶ХаІЗ а¶Ьа¶°а¶Ља¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙ගආ а¶Ъඌ඙ධඊඌටаІЗ а¶Ъඌ඙ධඊඌටаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Йආа¶≤аІЗථ, вАЬHere is true artist. පаІБථа¶≤аІЗ, පаІБථа¶≤аІЗ, а¶≤а¶Ња¶Ц а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ බගа¶≤аІЗа¶У а¶Чඌථ а¶Ча¶Ња¶За¶ђаІЗ ථඌ!вАЭ а¶ґа¶ња¶ґа¶ња¶∞а¶ђа¶Ња¶ђаІБ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЫаІЛа¶Я а¶≠а¶Ња¶За¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, බаІЗа¶Ц а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІАටඌ а¶ђа¶ЗටаІЗ а¶Па¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђаІИටඌа¶≤а¶ња¶ХаІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞аІНа¶Я බаІЗа¶ђ! а¶Жа¶ЪаІНа¶ЫаІЈ а¶Ха¶Ња¶≤ ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ, а¶ХаІЗඁථ?
඙а¶∞බගථ ඐගධථ а¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞аІАа¶ЯаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ЧаІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Ха¶ЩаІНа¶ХඌඐටаІАа¶ХаІЗ а¶°аІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶Жа¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ! а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶ња¶∞ а¶Чඌථ පаІЛථаІЛ ටаІЛа•§вАЭ а¶Жа¶∞аІЛ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶ЄаІАටඌ а¶ђа¶З බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ы?вАЭ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬබаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња•§вАЭ вАЬа¶Жа¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ, а¶ђаІИටඌа¶≤а¶ња¶ХаІЗа¶∞ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Ьඌථඌ а¶Жа¶ЫаІЗ?вАЭ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶ХаІЗ а¶Па¶ХаІЗ ‘а¶Ьа¶ѓа¶Ља¶ЄаІАටඌ඙ටග а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ ටඐаІБ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞а¶ЃаІНа¶≠ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Еа¶ђа¶ња¶Ха¶≤ а¶ХаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶ђа¶Ња¶ђаІБа¶∞ а¶Ча¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞ ථа¶Ха¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ча¶Ња¶За¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Еа¶ђа¶Ња¶Х а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ ටගථග а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶Ха¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶ђа¶Ња¶ђаІБа¶∞ а¶Ча¶≤а¶Ња¶∞ ඁට а¶ЄаІНа¶ђа¶∞ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ы?вАЭ
а¶ѓа¶Ња¶Х, ඙аІНа¶∞ටගබගථ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Жа¶∞а¶ЃаІНа¶≠ а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Ха¶ЩаІНа¶ХඌඐටаІАа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ ඙ඌа¶Ба¶Ъ а¶Ы’ а¶Цඌථඌ а¶Чඌථа¶У පගа¶Ца¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ බගа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶Хබගථ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬа¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶Ха¶ња¶В а¶ХаІЛථබගථ а¶єа¶ђаІЗ? ටගථග а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶ЪගථаІНටඌ а¶ХаІЛа¶∞аІЛථඌ, ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ආගа¶Х а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶ђа¶≤а¶ђа•§ ඙ඌа¶∞аІНа¶Яа¶Яа¶Ња¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞ а¶Хඕඌ ටаІЛ ථаІЗа¶З, පаІБа¶ІаІБ а¶Чඌථ а¶Х’а¶Цඌථඌ, а¶Жа¶∞ а¶ЄаІБа¶∞ ටаІЛ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶З а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶ЦඌථаІЗа¶Х ඙а¶∞аІЗ, а¶Па¶Хබගථ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶Ха¶ЩаІНа¶Ха¶Ња¶ХаІЗ а¶Чඌථ පаІЗа¶Ца¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња•§ පගපගа¶∞а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶Ша¶∞аІЗ ඥаІБа¶Ха¶≤аІЗථ а•§ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶ЫаІБа¶ЯаІЗ а¶Ьа¶ђа¶Њ а¶ЂаІБа¶≤аІЗа¶∞ ඁට а¶≤а¶Ња¶≤а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Ха¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗථвА¶ а¶Хටа¶ХаІНа¶Ја¶£ ඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ යඌටබаІБа¶ЯаІЛ а¶ЪаІЗ඙аІЗ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ ඁට а¶ХаІЗа¶БබаІЗ а¶Йආа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАЬа¶≠а¶Ња¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ХаІНа¶Ја¶Ѓа¶Њ а¶Ха¶∞а•§ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђаІЛа¶І а¶єа¶ѓа¶Љ ඙ඌа¶∞аІНа¶Яа¶Яа¶Њ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓ ථඌ! ඀ගථඌථаІНа¶Єа¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗ, а¶∞а¶Ња¶Ѓа¶Ња¶ѓа¶Ља¶£аІЗа¶∞ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗ а¶ХаІЛථаІНвАМ а¶Жа¶ђа¶ђа¶Ња¶Єа¶ЙබаІНබаІАථ а¶Ыа¶ња¶≤? а¶П а¶ђа¶ЗටаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБටаІЗа¶З а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථа¶ХаІЗ ථඌඐටаІЗ බаІЗа¶ђ ථඌ а•§ ටඌ а¶≠а¶Ња¶З, ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථඌඁа¶Яа¶Њ ඃබග ඙ඌа¶≤а¶ЯаІЗ බаІЗа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶ЉвА¶вАЭ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Хඕඌ පаІЗа¶Ј а¶Ха¶∞ටаІЗ බගа¶≤а¶Ња¶Ѓ ථඌ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, вАЬа¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ ථа¶Яа¶ЄаІВа¶∞аІНа¶ѓ а¶Ж඙ථග! а¶ѓаІЗ а¶ЄаІНථаІЗа¶є а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ බаІЗа¶Ца¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗථ а¶ЬаІАඐථ а¶≠а¶∞аІЗ ඁථаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶У а¶ЕථаІБа¶∞аІЛа¶І а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶∞а¶Ња¶Ѓа¶Ња¶ѓа¶Ља¶£аІЗа¶∞ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ ආගа¶Ха¶З, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ж඙ථඌа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ѓаІЛа¶Ьа¶Ха¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶ђаІЗථ а¶Еа¶≠ගථඃඊ ඁඌටаІНа¶∞а•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ а¶ђа¶Њ යගථаІНබаІБ а¶ѓаІЗ ථඌඁаІЗа¶З а¶Еа¶≠ගථඃඊ а¶Ха¶∞аІБа¶Х ථඌ а¶ХаІЗථ а¶≠а¶Ња¶≤ а¶Еа¶≠ගථඃඊ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶З а¶ђа¶З а¶ЙаІОа¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ, ථඌඁаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඪගථаІЗа¶Ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථඌඁ ඙ඌа¶≤а¶ЯаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Х а¶Еа¶≠ගථඃඊ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђ а¶®а¶Ња•§
а¶Па¶З а¶Ша¶Яථඌа¶∞ ඙а¶∞ а¶Жа¶∞ а¶ЪගටаІНа¶∞а¶Ьа¶ЧටаІЗ а¶ЖටаІНඁ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ ඐඌඪථඌ а¶ђа¶єаІБබගථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЃаІГට а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶∞а¶За¶≤а•§
а¶ђа¶єаІБබගථ ඙а¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч а¶Па¶≤ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞а•§ ටаІБа¶≤а¶ЄаІА а¶≤а¶Ња¶єа¶ња¶°а¶ЉаІАа¶∞ вАЬආගа¶Хඌබඌа¶∞вАЭ а¶ЫඐගටаІЗа•§ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗ а¶Ыа¶ђа¶њ ථаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗ а¶°аІБа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗ а¶ЄаІЗа¶Цඌථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶∞аІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Єа¶Ва¶Чටග а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ පаІИа¶≤аІЗථ а¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ, вАЬටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЫඐගටаІЗ ථඌඁටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§вАЭ а¶Єа¶Ва¶ЧаІАට а¶∞а¶Ъඃඊගටඌ පаІИа¶≤аІЗථ а¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ ථගа¶ЬаІЗ, а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶З ටඌа¶∞ а¶Хඕඌ ඪගථаІЗа¶Ѓа¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤ඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІЗа¶Й а¶Й඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶ЪаІБа¶ХаІНටගටаІЗ а¶Єа¶З а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ඪබа¶≤а¶ђа¶≤аІЗ а¶ђаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶ЧаІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ ඙ථаІЗа¶∞-а¶ХаІБа¶°а¶Ља¶њ බගථ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Жа¶≤ග඙аІБа¶∞බаІБа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶З බඁ඙аІБа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗ а¶Ыа¶ђа¶њ ථаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ යටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤а•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗ а¶єа¶≤ вАУ
඙аІМа¶ЈаІЗа¶∞ ඙ඌයඌධඊаІА а¶ђа¶Ња¶ѓа¶Љ
а¶Ха¶Ња¶Ба¶Яа¶Њ а¶ѓаІЗ а¶ђа¶ња¶Ба¶Іа¶ња¶≤ а¶Ча¶Ња¶ѓа¶Љ
ථа¶Ха¶∞аІА а¶Жа¶∞ а¶Ха¶∞а¶ђ а¶Ха¶њ а¶Ѓа¶∞а¶ђ а¶Ха¶њ а¶Ѓа¶∞а¶ђ а¶®а¶Ња•§а•§вАЭ
вАУ а¶Єа¶ња¶®аІЗа¶Ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶Њ ඁඌටаІНа¶∞ а¶ЫඐගටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЖටаІНඁ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗ вАЬа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶£аІБа¶Ѓа¶Ња¶ѓа¶Ља¶ЊвАЭ вАЬඁයඌථගපаІАвАЭ вАЬа¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ХඕඌвАЭ а¶Жа¶∞ вАЬආගа¶Хඌබඌа¶∞вАЭ а•§
а¶ђа¶Ња¶Ыа¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞
Latest posts by а¶ђа¶Ња¶Ыа¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞ (see all)
- (а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ-а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶Єа¶ња¶Х) ඐගපаІНඐථඐаІА вАУ а¶ЧаІЛа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ЃаІЛа¶ЄаІНට඀ඌ [පа¶∞аІНа¶Я а¶≠а¶Ња¶∞аІНа¶Єа¶®а•§] ඙ඌа¶∞аІНа¶Я аІЂ - а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Ъ 17, 2024
- а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶єа¶ђаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ха¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶Зථа¶Хඁ඙ගа¶ЯаІЗථа¶Яа¶≤а¶њ (incompetently) а¶ХගථаІНටаІБ ඙ඌа¶∞а¶Єа¶ња¶Єа¶ЯаІЗථа¶Яа¶≤а¶њ (persistently) а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶Еа¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞а¶ђаІЗථ (аІІаІѓаІЃаІЂ) – а¶ЖඐබаІБа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶Ьа¶Ња¶Х - а¶ЂаІЗа¶ђаІНа¶∞аІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ 26, 2024
- а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶ЧаІЛа¶БаІЬа¶Ња¶Ѓа¶њ а¶ђа¶Њ а¶ЫаІБаІОа¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶ЄаІНඕඌථ ථаІЗа¶З – а¶ЃаІБа¶єа¶ЃаІНඁබ පයаІАබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶єаІН - а¶ЂаІЗа¶ђаІНа¶∞аІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ 21, 2024